শাহজালাল ইয়ামেনি (রহ.)-এর সঙ্গে ৩৬০ আউলিয়া সিলেট অঞ্চলে আগমন করেন। তাঁদের একজন সৈয়দ আহমদ গেসুদারাজ কেল্লা শহীদ (রহ.)। যুদ্ধে শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীরা জয়লাভ করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সৈয়দ আহমদ গেসুদারাজ শাহাদতবরণ করেন।
মুসলিম প্রত্ননিদর্শন
আখাউড়ার কেল্লা শহীদের মাজার
আহমাদ ইজাজ

মাজারসংলগ্ন জমিতে নির্মাণ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন মসজিদ, মুসাফিরখানা, চুলাঘর, এতিমখানা, বিশ্রামাগার, কবরস্থান, মার্কেট কাম কমপ্লেক্স, মাদরাসা, বিদ্যালয় ও বিশাল পুকুর। প্রচলিত আছে, একদিন চৈতন দাস ও তাঁর সঙ্গীরা তিতাস নদীতে মাছ ধরার সময় একটি কাটা মাথা তাদের জালে আটকা পড়ে। এমন ঘটনায় সবাই যখন হতবিহ্বল, তখনই মাথাটি বলে ওঠে, ‘একজন আস্তিকের সঙ্গে একজন নাস্তিকের কখনো মিল হতে পারে না।
ওই দিনই কালেমা পড়ে মুসলমান হন জেলে চৈতন দাস ও তাঁর সঙ্গীরা। আর কাটা মাথার নির্দেশে সেটিকে খড়মপুরে তিতাস নদীর পারের কবরস্থানে দাফন করা হয়। সেই থেকে কবরটি সৈয়দ আহম্মদ গেসুদারাজ ওরফে কেল্লা শহীদ (রা.)-এর মাজার নামে পরিচিতি পায়। ২৬০ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত দরগা শরিফের জায়গা তৎকালীন আগরতলা রাজ্যের মহারাজা দান করেন।
সম্পর্কিত খবর
কোরআন থেকে শিক্ষা
- পর্ব, ৭৫৮

আয়াতের অর্থ : “তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনিই ‘রহমান’, তাঁর সম্পর্কে যে অবগত আছে, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। যখন তাদের বলা হয়, সিজদাবনত হও রহমানের প্রতি... তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামীরূপে তার জন্য, যে উপদেশ গ্রহণ করতে ও কৃতজ্ঞ হতে চায়।
আয়াতগুলোতে তারকারাজি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
শিক্ষা ও বিধান
১. আসমান-জমিন এবং এই দুয়ের মধ্যকার সব বিষয় সম্পর্কে মহান আল্লাহই পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। তাই সৃষ্টিজগত্ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে তাঁরই দ্বারস্থ হতে হবে।
২. বরকত হলো কোনো কিছুতে আল্লাহ প্রদত্ত কল্যাণ লাভ করা।
৩. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, বুরুজ হলো বড় বড় নক্ষত্র বা ১২টি প্রসিদ্ধ রাশিচক্র।
৪. আয়াত থেকে বোঝা যায়, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজির মধ্যে আল্লাহ মানুষের জন্য কল্যাণ রেখেছেন। এটা মানবজাতির প্রতি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ।
৫. ওমর (রা.) বলেন, দিনে বা রাতে যেসব ইবাদত নিয়মিত আদায় করা হয় তা ছুটে গেলে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আদায় করে নেবে (যদি নিষিদ্ধ সময় না হয়)।
(বুরহানুল কুরআন : ২/৬২৩)
মুসলিম বাঙালি নারীর আত্মপরিচয়
আহমাদ আরিফুল ইসলাম
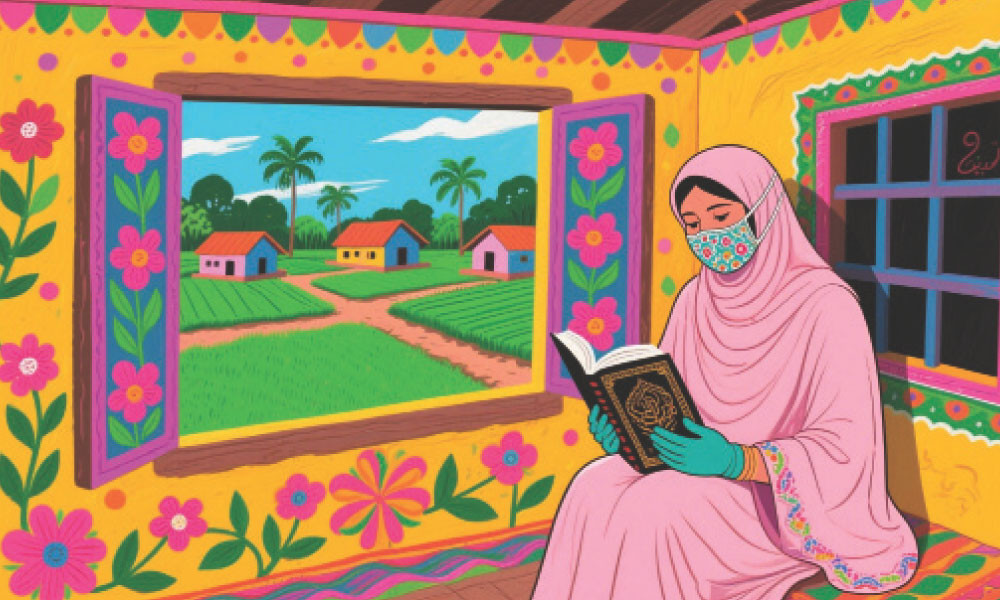
বাংলার মাটি ও বাঙালির সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে যে অনবদ্য শক্তির প্রতিচ্ছবি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জ্বলজ্বল করে এসেছে, তা হলো বাঙালি মুসলিম নারী। সে শুধু একটি লিঙ্গ পরিচয়ের বাহক নয়, সে এই জাতির বিশ্বাস, মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন, শালীনতা ও আত্মমর্যাদার এক জাগ্রত প্রতীক। বাংলার প্রতিটি পরতে পরতে তার অবদান ইতিহাসে লেখা, পরিবারে প্রোথিত এবং সমাজে প্রমাণিত।
ঐতিহাসিক নির্মাণে বাঙালি মুসলিম নারী
ইসলামী ইতিহাসে নারীদের মর্যাদার যে উদাহরণ নবীজির (সা.) যুগ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে, বাঙালি মুসলিম নারী সেই আদর্শ থেকেই নির্মিত হয়েছে।
শিক্ষার ক্ষেত্রে মা আয়েশা (রা.), ত্যাগের ক্ষেত্রে খাদিজা (রা.), সাহসিকতার ক্ষেত্রে নুসাইবা বিনতে কাব (রা.)-এর জীবনী আমাদের পূর্বসূরি মুসলিম নারীদের অনুপ্রেরণা দিয়েছে।
এই আদর্শ নিয়েই বাংলা সমাজে মুসলিম নারী গড়ে তুলেছে পরিবার, সাহসিকতা আর শালীনতার সম্মিলনে একটি অনন্য জীবনধারা।
বাঙালি মুসলিম নারী ‘সংসারপটু’, ‘লাজুক’, ‘পর্দাশীল’ ও ‘ধর্মবিশ্বাসী’—এই চারটি শব্দের ছায়ায় নিজের পরিচয় নির্মাণ করেছে।
মধ্যযুগে মুসলিম পরিবারে নারী ছিল শিক্ষিত, ধর্মচর্চায় প্রবল এবং গৃহস্থালির সংগঠক।
হাজার বছরের ঐতিহ্যে তারা কখনো বিদ্রোহিনী, কখনো আলোকবর্তিকা; কখনো গৃহকোণে সংযত সাহসিনী, আবার কখনো রাজপথে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। তাদের ভূমিকা পরিবারে, সমাজে, রাজনীতিতে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে যতটা বিস্তৃত, ততটাই শিকড়গাঁথা ধর্মীয় মূল্যবোধে।
ইতিহাস সাক্ষী দেয়, বাংলার নারী কখনো সস্তা পরিচয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয়নি, বরং তারা ছিল পর্দার আড়ালে থেকেও সবচেয়ে দৃঢ় কণ্ঠস্বর, ছিল সংসারের শান্তি, সমাজের স্থিতি, আর নৈতিকতার প্রহরী।
আধুনিকতার অভিঘাতে নতুন চ্যালেঞ্জ
তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বায়ন, বাজার-অর্থনীতি ও তথাকথিত উন্নয়ন চিন্তার অভিঘাতে বাঙালি মুসলিম নারীর আত্মপরিচয় এক নতুন সংকটের মুখে পড়েছে। নারীবাদ ও মানবাধিকারের নামে এমন কিছু ধারণা ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যা তার প্রকৃত মর্যাদা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
নারীর ‘স্বাধীনতা’ কথাটিকে অনেক সময় এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেন ধর্ম, পরিবার বা শালীনতা—সব কিছুই নারীর জন্য এক ধরনের শৃঙ্খল। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, বাঙালি মুসলিম নারীর স্বাধীনতা মানে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জীবনের নিশ্চয়তা, যেখানে সে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, সন্তানদের গড়তে পারে, সমাজকে আলোকিত করতে পারে।
এই প্রেক্ষাপটে যখন পতিতাবৃত্তিকে ‘শ্রম’ হিসেবে স্বীকৃতির প্রস্তাব আসে, তখন সেটি নিছক একটি শ্রমনীতির বিষয় থাকে না, বরং হয়ে দাঁড়ায় এক গভীর সাংস্কৃতিক সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু।
এই সমাজে একজন পতিতা কখনোই নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে না, বরং তারা পুনর্বাসনের দাবি রাখে, সম্মানিত জীবনের সুযোগ পাওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু সেই পেশাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিলে তা হবে আত্মমর্যাদার ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দেওয়া।
বাঙালি মুসলিম নারীর ভবিষ্যত্ কোন পথে?
আজ আমাদের সমাজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। একদিকে রয়েছে ইসলামী মূল্যবোধ, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও সামাজিক শালীনতার ঐতিহ্য। অন্যদিকে রয়েছে ভোগবাদ, পণ্যায়ন ও আত্মপরিচয়ের বিভ্রান্তি। এই দ্বন্দ্বে বাঙালি মুসলিম নারী কী করবে?
উত্তর একটাই—তাকে তার শিকড়ে ফিরতে হবে। তাকে জানতে হবে তার ইসলাম কী বলে, সমাজ কী প্রত্যাশা করে এবং আত্মমর্যাদা কিসে রক্ষা পায়। ইসলাম নারীর স্বাধীনতাকে তার সম্ভ্রমহানির ছায়া নয়, বরং সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা হিসেবে দেখেছে। তাই কোনো আইন, সংস্কার কিংবা উন্নয়নের অজুহাতে যদি নারীকে তার ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা হয়, তা সমাজে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি ডেকে আনবে।
নারী স্বাধীনতা মানেই তার শালীনতাকে সম্মান করা, পরিবারকে গুরুত্ব দেওয়া এবং সমাজে কার্যকর ভূমিকা রাখা। একমাত্র এই পথেই বাঙালি মুসলিম নারী হতে পারে তার ইতিহাসের যোগ্য উত্তরসূরি।
জুমার নামাজের গুরুত্ব
মাইমুনা আক্তার

ইসলামের দৃষ্টিতে জুমার দিনকে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা নবীজি (সা.) বলেছেন, সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমার দিন সর্বোত্তম। এদিন আদম (সা.)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং সেখান থেকে দুনিয়ায় অবতরণ করানো হয়েছে। জুমার দিনই কিয়ামত সংঘটিত হবে।
ইসলামের জুমার দিনের গুরুত্ব অপরিসীম। জুমার দিনের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে নবীজি এই দিনকে ঈদের দিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন বলে একটি সূত্রে পাওয়া যায়।
জুমার দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো জুমার নামাজ। জুমার অর্থ হলো একত্র হওয়া, সংঘবদ্ধ হওয়া।
পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হে মুমিনগণ, জুমার দিনে যখন নামাজের আজান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে দ্রুত মসজিদের দিকে ধাবিত হও। আর বেচাকেনা বন্ধ করো। এটা তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারো।
জুমার দিনের অধিক গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে নবীজি (সা.) এই দিনকে ঈদের দিনের সঙ্গে তুলা করেছেন। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ এই দিনকে মুসলিমদের ঈদের দিনরূপে নির্ধারণ করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি জুমার সালাত আদায় করতে আসবে সে যেন গোসল করে এবং সুগন্ধি থাকলে তা শরীরে লাগায়। আর মিসওয়াক করাও তোমাদের কর্তব্য। (ইবনে মাজাহ, আয়াত : ১০৯৮)
হাদিসবিশারদের মতে, এখানে ঈদ বলে খুশি ও আনন্দের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
ইবনে আব্বাস (রা.) এই দিনের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে এই দিনকে ‘গরিবের হজ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন। (তাবরানি)
উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যাতে এই দিনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং এই দিনের পবিত্রতা রক্ষা করে ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারে। কোনো অবস্থায়ই যেন এই দিনের ফজিলত থেকে বঞ্চিত না হয়। হাদিস শরিফে জুমার দিনের বহু ফজিলত ও আমলের কথা উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো, এক জুমা থেকে আরেক জুমার মধ্যবর্তী সময়ের (সগিরা গুনাহের) জন্য কাফফারা হয়ে যায় যদি মুমিন কবিরাহ গুনাহ থেকে বিরত থাকে। (মুসলিম, হাদিস : ৪৪০)
জুমার নামাজ আদায়ের জন্য ইসলামের দেওয়া বিধান ও আদবগুলো পালন করে বের হলে, প্রতি কদমে কদমে গুনাহ মাফ হতে থাকে। আওস ইবনে আওস আস-সাক্বাফি (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করবে এবং (স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগবে এবং জাগাবে, জুমার জন্য বাহনে চড়ে নয়, বরং পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাবে এবং কোনোরূপ অনর্থক কথা না বলে ইমামের নিকটে বসে খুতবা শুনবে, তার (মসজিদে যাওয়ার) প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত্ সিয়াম (রোজা) পালন ও রাতভর সালাত (নামাজ) আদায়ের (সমান) সওয়াব পাবে। (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৪৫)
এর বিপরীতে যারা কোনো শরিয়ত সমর্থিত যৌক্তিক কারণ ছাড়া জুমার নামাজ পড়া থেকে বিরত থাকবে, তারা তো অফুরন্ত সওয়াব থেকে বঞ্চিত হবেই, পাশাপাশি তাদের নাম গাফিলদের তালিকায় পড়ে যাবে। আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তারা উভয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে তাঁর মিম্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন, যারা জুমার নামাজ ত্যাগ করে তাদেরকে এ অভ্যাস বর্জন করতে হবে, নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে সিল মেরে দেবেন, অতঃপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুসলিম, হাদিস : ১৮৮৭)
নাউজুবিল্লাহ, একজন মুমিনের জন্য এর চেয়ে বড় দুঃসংবাদ আর কী হতে পারে! উসামা ইবনে জায়েদ (রা.) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বিনা ওজরে (শরিয়ত সমর্থিত কোনো অজুহাত ছাড়া) পর পর তিন জুমা পড়া থেকে বিরত থাকে, তার নাম মুনাফিকদের খাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।’ (তাবরানি)
হাদিসটি সনদগতভাবে দুর্বল হলেও বিনা ওজরে জুমার নামাজ ছাড়া যে জঘন্য অপরাধ, তা জুমার দিনের ফজিলত সংবলিত হাদিসগুলো দেখলে অনুভব করা যায়।
অতএব, আমাদের সবার উচিত জুমার দিনের আদব রক্ষা করে জুমার নামাজ আদায়ের ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া।
আরবির প্রধান পাঁচ উপভাষা
আববার আবদুল্লাহ

পৃথিবীর কমপক্ষে ৩৫ কোটি মানুষ আরবি ভাষায় কথা বলে। ভাষাভাষীর বিচারে আরবি পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম ভাষা। ইসলামপূর্ব আরব উপদ্বীপই আরবি ভাষার জন্মস্থল। জাহেলি যুগ (যে যুগে ইসলামের আগমন ঘটে) এবং ইসলামী যুগেই আরবি ভাষার চূড়ান্ত বিকাশ সাধিত হয়।
তবে আরবি ভাষার একটি প্রমিত রূপ শিক্ষিত আরবদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।
আরবি ভাষার প্রধান পাঁচ উপভাষা
আরবি ভাষার প্রচলিত উপভাষাগুলোর মধ্যে প্রধান পাঁচ উপভাষার পরিচয় তুলে ধরা হলো—
১. মিসরীয় উপভাষা : আরবি ভাষাভাষীদের ভেতরে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষ মিসরীয় উপভাষায় কথা বলে। এটা প্রায় ১০ কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ভাষা। মিসরের বাইরেও লাখ লাখ মানুষ এই উপভাষায় কথা বলে। মিসরীয় চলচ্চিত্র ও গণমাধ্যম মিসরীয় উপভাষা জনপ্রিয় করে তুলেছে। এই উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হলো ‘জিম’ বর্ণকে ‘গাইন’-এর মতো উচ্চারণ করা।
২. মেসোপটেমিয়ান উপভাষা : মেসোপটেমিয়ান উপভাষায় কথা বলে ইরাক, কুয়েত, সিরিয়ার একাংশ, ইরানের আরবি ভাষীরা ও দক্ষিণ তুরস্কের আরবি ভাষীরা। এই উপভাষার ওপর প্রাচীন ও আধুনিক মেসোপটেমিয়ান ভাষাগুলোর প্রভাব আছে। যেমন—সুমেরি, আক্কাদি, ফারসি, কুর্দি ও গ্রিট। মেসোপটেমিয়ান উপভাষার প্রধান দুটি ধারা হলো জেলেট ও কেল্টু। এই উপভাষায় ‘দোয়াদ’ বর্ণকে কিছু ‘সা’ বর্ণের মতো উচ্চারণ করা হয়। একইভাবে ‘ক্বফ’ বর্ণকে ‘গাইন’ বর্ণের মতো উচ্চারণ করা হয়।
৩. শামি উপভাষা : ইংরেজিতে শামি উপভাষাকে লেভানটাইন বলা হয়। শামি উপভাষায় তিন কোটি ৮০ লাখ মানুষ কথা বলে। যাদের বেশির ভাগ সিরিয়া, লেবানন, জর্দান, ফিলিস্তিন ও তুর্কি সাইপ্রাসে বসবাস করে। শামি উপভাষা প্রমিত আরবির (এমএসএ) খুবই নিকটবর্তী। এই উপভাষায় ‘সা’ বর্ণকে ‘সিন’ বর্ণের মতো, ‘ক্বফ’ বর্ণকে ‘গাইন’ বর্ণের মতো এবং ‘কাফ’ বর্ণকে ‘সোয়াদ’ বর্ণের মতো উচ্চারণ করা হয়। শামি উপভাষার ওপর তুর্কি ভাষার বিশেষ প্রভাব রয়েছে। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষারও সামান্য প্রভাব আছে।
৪. মাগরিবি : উত্তর আফ্রিকা তথা মরক্কো, আলজেরিয়া, তিউনিশিয়া, লিবিয়া, পশ্চিম সাহারা ও মৌরিতানিয়া এবং পশ্চিম মিসরের লোকেরা এই উপভাষায় কথা বলে। স্থানীয়রা মাগরিবি আরবিকে দারিজা বলে। যার অর্থ নিত্যদিনের ভাষা। অভিযোগ আছে, মাগরিবি উপভাষা বোঝা তুলনামূলক কঠিন। এই উপভাষার ওপর ফরাসি, স্প্যানিশ, তুর্কি ও ইতালিয়ান ভাষার প্রভাব আছে। মাগরিবি উপভাষার বৈশিষ্ট্য হলো স্বরবর্ণ বিলোপ করা। যেমন—প্রমিত আরবি বাক্য ‘মিন আইনা আনতা’-এর মাগরিবি উচ্চারণ হলো ‘মানিনতা’। মিন আইনা আনতা অর্থ আপনি কোথা থেকে এসেছেন।
৫. খালিজি উপভাষা : আরবি খালিজি শব্দের অর্থ উপসাগরীয়। এই উপভাষায় কমপক্ষে ৭০ লাখ মানুষ কথা বলে। সৌদি আরব, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, দক্ষিণ ইরাক ও উত্তর ওমানের অধিবাসীরা খালিজি উপভাষায় কথা বলে। তবে প্রত্যেক দেশের খালিজি উপভাষার ব্যবহার ও উচ্চারণে সামান্য ব্যবধান আছে। এই উপভাষার বৈশিষ্ট্য হলো ‘ক্বফ’ বর্ণকে ‘গাইন’ বর্ণের মতো উচ্চারণ করা এবং ‘কাফ’ বর্ণকে ‘সোয়াদ’ বর্ণের মতো উচ্চারণ করা। খালিজি উপভাষার ওপর ফারসি ও তুর্কি ভাষার দৃশ্যমান প্রভাব আছে।
মিডল ইস্ট আই অবলম্বনে