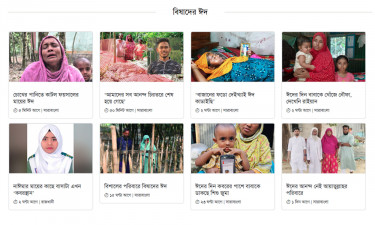বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা ঈদুল ফিতর অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে উদযাপন করে। যদিও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে ঈদ ব্যাপকভাবে উদযাপিত হয়, তবে অমুসলিম দেশগুলোতেও এটি যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা হয়। এসব দেশে বসবাসরত মুসলমানরা স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঈদ উদযাপন করে। এই প্রবন্ধে আমরা অমুসলিম দেশগুলোতে ঈদুল ফিতর উদযাপনের বৈচিত্র্যময়তা ও বিশেষ দিকগুলো তুলে ধরব।
অমুসলিম দেশগুলোতে যেভাবে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়
অনলাইন ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানরা ঈদুল ফিতরকে অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন করে। ঈদের দিন ভোরে মসজিদে বা খোলা স্থানে ঈদের নামাজ আদায় করা হয়। এরপর পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান হয়। বড় শহরগুলোর মুসলিম কমিউনিটি সেন্টারে ঈদের আয়োজন করা হয় যেখানে খাবারের স্টল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং শিশুদের জন্য বিশেষ বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে।
মিশিগানের হ্যামট্রামিক শহরের স্কুল মাঠে বৃহৎ জামাত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশ নেন। নামাজ শেষে মুসল্লিরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং বাসায় গিয়ে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে আনন্দ উদযাপন করেন।
রাশিয়া
রাশিয়া ইউরোপ ও এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত একটি বিশাল দেশ, যেখানে প্রায় ২ কোটি মুসলমান বসবাস করে, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৫%।
রাশিয়ার মস্কো ক্যাথেড্রাল মসজিদ, সেন্ট পিটার্সবার্গ মসজিদ, কাজান মসজিদ সহ বিভিন্ন মসজিদে ঈদের বিশেষ নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী মস্কোতে ঈদের দিন লাখো মুসল্লি জড়ো হয়। ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করতে রাশিয়ার মুসলিমরা ফজরের পর থেকেই মসজিদের দিকে যেতে থাকে।
ঈদের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ঐতিহ্যবাহী রুশ-মুসলিম খাবার। "চাক-চাক" (মিষ্টি ময়দার খাবার), "বেলিশ" (মাংস ও আলুর রুটি), "শুরপা" (মাংসের স্যুপ) ইত্যাদি রাশিয়ার মুসলিমদের ঈদের বিশেষ খাবার। দাগেস্তান ও চেচনিয়ায় জনপ্রিয় খাবার হলো "খিঙ্কাল" (গরু বা ভেড়ার মাংস দিয়ে তৈরি একটি রুটি)। চায়ের সঙ্গে "বাকলাভা" ও "সামসা" পরিবেশন করা হয়।
চেচনিয়া ও দাগেস্তানে ঈদের দিনে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। রাশিয়ায় ঈদুল ফিতরকে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এটি জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে পালিত না হলেও মুসলিমপ্রধান অঞ্চলগুলোতে সরকারি ছুটি দেওয়া হয়।
চীন
মুসলমানদের জন্য ঈদুল ফিতর একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় উৎসব, এবং চীনের মুসলিমরা এ দিনটি ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপন করে। তবে, চীনের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সরকারি নীতির কারণে মুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কিছুটা সীমিত। চীনের মুসলিম সম্প্রদায় প্রায় ২ কোটির বেশি, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ১.৫%। চীনের মুসলিমরা ঐতিহ্যগতভাবে ঈদুল ফিতর উদযাপন করে আসছে। তবে তাদের উদযাপনের ধরণ অঞ্চলভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে।
চীনের বিভিন্ন মসজিদে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, বিশেষ করে মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে যেমন শিনজিয়াং, নিংশিয়া, গানসু ও ইউন্নান। বেইজিং, শানজি ও হেনানেও মুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট মসজিদে ঈদের জামাত হয়। নামাজ শেষে মুসলিমরা একে অপরের সঙ্গে কোলাকুলি করে এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করে।
চীনা মুসলমানরা ঈদের দিন বিশেষ খাবার প্রস্তুত করে। "ল্যাম্ব কাবাব", "পোলাও", "নুডলস", "সুইট রাইস" ও বিভিন্ন ধরনের "হালুয়া" এদিনের জনপ্রিয় খাবার। "স্যানঝি" (তেলে ভাজা মিষ্টি খাবার) ও "ইয়োগুর্ট" হুই মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়। শিনজিয়াং অঞ্চলে "লাগমেন" (এক ধরনের নুডলস) ও "নাং" (রুটি) ব্যাপকভাবে খাওয়া হয়।
বড় শহরগুলোতে ঈদের দিন মুসলিম পরিবারগুলো একে অপরের বাড়িতে বেড়াতে যায়। বিভিন্ন বাজার ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে মুসলমানরা নতুন পোশাক, খাবার ও উপহার কেনাকাটা করে। সাংস্কৃতিকভাবে ঈদের দিনে হুই মুসলিমরা ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে এবং শিনজিয়াংয়ে উইঘুর মুসলিমরা ঐতিহ্যবাহী নাচ ও গান পরিবেশন করে।
কানাডা
কানাডায় মুসলিম সম্প্রদায় ঈদের দিন নামাজ আদায় করে এবং বিশেষ পার্টি ও খাবারের আয়োজন করে। এখানে বিভিন্ন ইসলামিক সোসাইটি ও মসজিদ ঈদের আয়োজন করে। বৃহৎ শহরগুলোতে যেমন টরন্টো, মন্ট্রিয়াল ও ভ্যাঙ্কুভারে ঈদের বড় জমায়েত হয়। মুসলমানরা সাধারণত ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে একে অপরকে শুভেচ্ছা জানায়। এছাড়া ক্যালগেরিতে আকরাম জুম্মা মসজিদে প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে স্থানীয় মুসলিমরা অংশ নেন। বাংলাদেশ কমিউনিটির মসজিদ বিএমআইসিসিতেও একাধিক জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের দিনটি কর্মদিবস হওয়ায় অনেকেই নামাজ আদায় করে কর্মস্থলে যোগ দেন।
যুক্তরাজ্য
যুক্তরাজ্যে মুসলমানরা ঈদ অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে উদযাপন করে। লন্ডন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টারসহ বড় শহরগুলোতে ঈদের নামাজের জন্য বড় মাঠ বা পার্ক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক সেন্ট্রাল মসজিদে বৃহৎ জামাত অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সকাল ৭টা থেকে এক ঘণ্টা পর পর ছয়টি জামাত হয়। বাংলাদেশি অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটসের ইস্ট লন্ডন মসজিদ ও ব্রিকলেন মসজিদেও চারটি করে জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধীদলীয় নেতা পৃথক বার্তা প্রদান করেন। ঈদের দিন রাস্তায় বিশেষ খাবারের দোকান বসে এবং পারিবারিক মিলনমেলা হয়। ব্রিটিশ মুসলমানরা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাবার যেমন বিরিয়ানি, কাবাব, শির খুরমা ইত্যাদি উপভোগ করেন।
ফ্রান্স
ফ্রান্সে প্রায় ৫৫ লাখেরও বেশি মুসলমান বসবাস করেন, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮.৮ শতাংশ। এখানে মুসলিম সম্প্রদায় ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ঈদুল ফিতর উদযাপন করে। প্যারিসের বিভিন্ন মসজিদে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশগ্রহণ করেন। সাধারণত সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে মিল রেখে ফ্রান্সে ঈদুল ফিতর উদযাপিত হয়। এখানকার মুসলমানরা ঈদের দিন নামাজ আদায়ের পর পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে একত্রিত হয় এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।
অস্ট্রেলিয়া
অস্ট্রেলিয়ায় ঈদুল ফিতর বেশ বড় পরিসরে উদযাপিত হয়। ঈদের দিন সকালে মুসলমানরা স্থানীয় মসজিদ বা খোলা স্থানে সমবেত হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন। নামাজের পর পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও সম্প্রদায়ের সদস্যরা একত্রিত হয়ে খাবার ভাগাভাগি করেন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।
অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি মুসলিমরা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিল রেখে ঈদ উদযাপন করেন। তারা স্থানীয় মসজিদে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন, যেখানে ঐতিহ্যবাহী খাবার পরিবেশন করা হয় এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
নিউজিল্যান্ড
নিউজিল্যান্ডের মুসলিম জনসংখ্যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সম্প্রদায়টি বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত, যা তাদের উদযাপনে বৈচিত্র্য নিয়ে আসে।
ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নিউজিল্যান্ডের বিভিন্ন মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারগুলো বিশেষ নামাজের আয়োজন করে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রাইস্টচার্চের মসজিদ আল-নূর এবং অকল্যান্ডের পনসনবি মসজিদে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মুসলিম সম্প্রদায়ের সদস্যরা একত্রিত হয়ে প্রার্থনা করেন এবং আনন্দ ভাগাভাগি করেন। ঈদের সময় মুসলিম পরিবারগুলো ঐতিহ্যবাহী খাবার প্রস্তুত করে এবং বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের সঙ্গে তা উপভোগ করে। এছাড়াও, বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠন ও কমিউনিটি সেন্টারগুলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যা মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি করে।
জার্মানি
জার্মানিতে মুসলিম সম্প্রদায় সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে মিল রেখে ঈদুল ফিতর উদযাপন করে। রাজধানী বার্লিনসহ বিভিন্ন শহরে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা অংশগ্রহণ করেন। জার্মানিতে বসবাসরত মুসলমানরা ঈদের দিন ছুটি না পেলেও তারা সকালে নামাজ আদায় করে এবং রাতে পার্টির আয়োজন করে। অনেক জায়গায় স্থানীয় কমিউনিটি সেন্টারে ঈদ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়।
জাপান
জাপানে মুসলিম সম্প্রদায় খুবই ছোট, তবে তারা মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে একত্রিত হয়ে ঈদ উদযাপন করে। টোকিও, ওসাকা ও নাগোয়ার মসজিদগুলোতে ঈদের নামাজ আদায় করা হয় এবং পরে খাবার ভাগ করে নেওয়া হয়।
দক্ষিণ কোরিয়া
দক্ষিণ কোরিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা কম, তবে সিউলে কেন্দ্রীয় মসজিদে ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে কমিউনিটি ফেস্টিভাল ও খাবার বিতরণের আয়োজন করা হয়।
ব্রাজিল
ব্রাজিলে মুসলমানরা ঈদের নামাজের পর একে অপরকে শুভেচ্ছা জানায় এবং বিশেষ খাবার রান্না করে। সাও পাওলো ও রিও ডি জেনেইরোর মুসলিম কমিউনিটিগুলোতে ঈদ উদযাপন চোখে পড়ার মতো।
অমুসলিম দেশগুলোতে ঈদুল ফিতরের উদযাপন সাধারণত স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে করা হয়। যদিও এসব দেশে সরকারি ছুটি থাকে না, তবে মুসলিম সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়। ঈদুল ফিতর শুধু একটি ধর্মীয় উৎসবই নয়, এটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের প্রতীক।
সম্পর্কিত খবর
মায়ানমার জান্তাও সাময়িক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল
অনলাইন ডেস্ক

মায়ানমারের সামরিক বাহিনী ভূমিকম্প-পরবর্তী ত্রাণ সরবরাহ ও পুনর্গঠনের গতি বাড়াতে সাময়িক যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছে। এক বিবৃতিতে ক্ষমতাসীন জান্তার রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক পরিষদ জানিয়েছে, এই চুক্তি ২ এপ্রিল থেকে ২২ এপ্রিল পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
এর আগে চলতি সপ্তাহে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইরত বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলো একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছিল, যাতে ত্রাণ কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালিত হতে পারে। তবে সামরিক বাহিনী বুধবারের ঘোষণার আগ পর্যন্ত একই পদক্ষেপ নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছিল।
গত শুক্রবার ৭.৭ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার পর এখন পর্যন্ত কমপক্ষে দুই হাজার ৮৮৬ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। এখনো শত শত মানুষ নিখোঁজ রয়েছে। ভূমিকম্পের কম্পন কয়েক শ মাইল দূর পর্যন্ত অনুভূত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিবেশী থাইল্যান্ডও। সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা বর্তমানে ২১ জনে দাঁড়িয়েছে।
২০২১ সালের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর থেকে মায়ানমার গৃহযুদ্ধের কারণে ব্যাপক সহিংসতার কবলে রয়েছে। সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন জাতিগত মিলিশিয়া ও প্রতিরোধ বাহিনীগুলো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।
ত্রাণবাহী চীনা রেড ক্রসের গাড়িবহরে গুলি
এদিকে মায়ানমারের সামরিক বাহিনী স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাতে ত্রাণবাহী চীনা রেড ক্রসের গাড়িবহরের দিকে গুলি ছুড়েছে। সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী তা’আং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (টিএনএলএ) জানিয়েছে, পূর্ব শান রাজ্যে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ৯টি যানবাহনের ওই বহরের দিকে মেশিনগান দিয়ে গুলি চালায়।
এই বহরটি ভূমিকম্পে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শহর মান্দালয়ের দিকে যাচ্ছিল। তবে এই ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। জান্তা সরকার এই ঘটনার তদন্তের ঘোষণা দিয়েছে। তবে তারা সরাসরি গাড়িগুলোর দিকে গুলি ছোড়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, বহরটি থামতে সংকেত দেওয়া হলেও না থামায় সেনারা ফাঁকা গুলি ছোড়ে।
অন্যদিকে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার জানায়, তাদের উদ্ধারকারী দল ও ত্রাণসামগ্রী নিরাপদ রয়েছে। তারা আশা করে, ‘মায়ানমারের সব পক্ষ ও গোষ্ঠী ভূমিকম্প-পরবর্তী ত্রাণ কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে।’
মায়ানমারে মানবিক সংকট আরো তীব্র হয়েছে
গত সপ্তাহের ভূমিকম্পের পর মায়ানমারে মানবিক সংকট মারাত্মকভাবে বেড়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে জান্তার দেওয়া মৃতের সংখ্যা যা বলা হচ্ছে, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়েও অনেক বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বহু আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা ও বিভিন্ন বিদেশি সরকার ভূমিকম্প আক্রান্ত অঞ্চলে উদ্ধারকর্মী ও ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছে।
এক সামরিক মুখপাত্র বুধবার জানান, মঙ্গলবার রাতে সেনারা নাউংচো টাউনশিপ থেকে আসা ওই ত্রাণ বহরটি দেখে। বহরের গাড়িগুলোতে চীনা স্টিকার ও মায়ানমারের নম্বর প্লেট ছিল, তবে সেনারা আগেভাগে এই বহরের গতিবিধি সম্পর্কে কোনো তথ্য পায়নি।
তিনি বলেন, ‘আমরা বহরটি দেখে থামানোর নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা থামেনি। তখন আমরা ২০০ মিটার দূর থেকে গুলি চালাই, তবু তারা থামেনি। যখন তারা প্রায় ১০০ মিটারের মধ্যে চলে আসে, তখন আমরা তিনটি ফাঁকা গুলি ছুড়ি। এরপর গাড়িগুলো ঘুরে নাউংচোর দিকে ফিরে যায়।’
মুখপাত্র আরো জানান, মান্দালয়ে উদ্ধার সহায়তা দিচ্ছে চীনের ব্লু স্কাই রেসকিউ টিম এবং তারা এই রুট দিয়ে যাওয়ার সময় নিরাপত্তা সুরক্ষা পেয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ত্রাণ সহায়তা দিতে চাইলে তাদের অবশ্যই মায়ানমার সরকারকে আগেভাগে জানাতে হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
এদিকে রেড ক্রসের বহরকে পাহারা দেওয়া টিএনএলএ জানিয়েছে, তারা মান্দালয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সামরিক পরিষদকে আগেই অবহিত করেছিল। বহরটি নাউংচোতে ফিরে গেলেও তাদের যাত্রা আবার শুরু হবে বলে টিএনএলএ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
সূত্র : বিবিসি
ইতালি নাগরিকত্বের পথ কঠোর করছে কেন
- আগের আইনে কী ছিল
নতুন নিয়ম কী
পরিবর্তনের প্রভাব কতটা বিস্তৃত
কেন এই পরিবর্তন
অন্য দেশগুলো কী করছে
আলজাজিরা
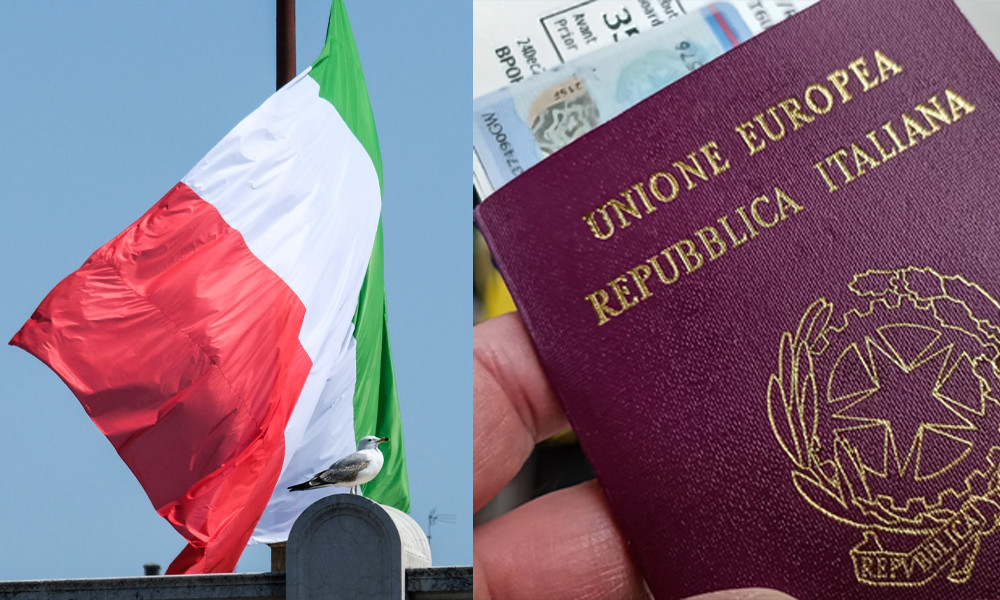
ইতালির সরকার দেশের নাগরিকত্ব আইন আরো কঠোর করেছে। সমালোচকরা বলছেন, অনেকেই শুধু বিশ্বজুড়ে ভ্রমণের সুবিধার্থে পারিবারিক বংশধারা অনুসন্ধান করে ইতালীয় পাসপোর্ট পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, যাদের প্রকৃতপক্ষে দেশটির সঙ্গে তেমন কোনো বাস্তব সংযোগ নেই।
এখন থেকে ইতালীয় বংশোদ্ভূত কমসংখ্যক ব্যক্তি নাগরিকত্ব পাবেন। কারণ নতুন নিয়মে শুধু যাদের মা-বাবা বা দাদা-দাদি ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, তারাই নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।
সরকার জানিয়েছে, অভিবাসীদের বংশধারা অনুসন্ধান করে বিপুল পরিমাণ নাগরিকত্ব আবেদন জমা পড়ায় এই পরিবর্তন আনা হয়েছে।
ইতালির আগের নাগরিকত্ব আইন কী ছিল?
আগের নিয়ম অনুযায়ী, কেউ যদি প্রমাণ করতে পারতেন, তার কোনো ইতালীয় পূর্বপুরুষ ১৮৬১ সালের ১৭ মার্চের পর জীবিত ছিলেন (যেদিন ইতালির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়), তাহলে তিনি নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারতেন।
তবে ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি বলেছেন, এই নিয়ম পুরনো এবং আইন পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো ‘অপব্যবহারকারী’দের দমন করা, যারা শুধু ভ্রমণসংক্রান্ত বিধি-নিষেধ এড়াতে ইতালির নাগরিকত্ব গ্রহণ করছিলেন।
হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্স অনুযায়ী, ইতালির পাসপোর্ট বিশ্বের তৃতীয় শক্তিশালী পাসপোর্ট, যা ভিসামুক্ত বা অন-অ্যারাইভাল ভ্রমণের বিশাল সুবিধা দেয়।
রোমে এক সংবাদ সম্মেলনে তাজানি বলেন, ‘ইতালির নাগরিক হওয়া গর্বের বিষয়। এটি কোনো খেলা নয়, যেখানে শুধু পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য কেউ ইতালীয় হতে পারে এবং তারপর মায়ামিতে কেনাকাটা করতে যায়।’
নতুন নিয়ম কী?
শুক্রবার ঘোষিত নতুন ডিক্রি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে।
এ ছাড়া দ্বৈত নাগরিকত্বধারীরা যদি ইতালির প্রতি ‘নিষ্ঠার প্রমাণ’ না দেখান, যেমন কর প্রদান, ভোটদান বা পাসপোর্ট নবায়ন না করেন, তাহলে তাদের ইতালীয় নাগরিকত্ব হারানোর ঝুঁকি থাকবে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হলো, ইতালির বিদেশি কনস্যুলেটগুলো আর নাগরিকত্ব আবেদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করবে না।
এই পরিবর্তনের প্রভাব কতটা বিস্তৃত?
ইতালির পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা মন্ত্রণালয়ের মতে, আগের নিয়ম অনুযায়ী বিশ্বজুড়ে ছয় থেকে আট কোটি মানুষ ইতালির নাগরিকত্বের জন্য যোগ্য ছিলেন, যা ইতালির মোট ৫.৯ কোটি জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকায় ইতালীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য ব্যাপকভাবে আবেদন করছিলেন। কারণ ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইতালির অনেক মানুষ দরিদ্রতা থেকে বাঁচতে এই অঞ্চলে অভিবাসী হয়েছিলেন।
২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ইতালির নাগরিকত্বধারী অভিবাসীদের সংখ্যা ৪০ শতাংশ বেড়েছে, যা ৪৬ লাখ থেকে ৬৪ লাখে পৌঁছেছে। এর একটি বড় অংশ নবনাগরিকত্ব পাওয়া ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করে। শুধু আর্জেন্টিনায় ২০২৩ সালে যেখানে ২০ হাজার জন নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন, ২০২৪ সালে সেটি বেড়ে ৩০ হাজার হয়েছে। একই সময়ে ব্রাজিলে ১৪ হাজার থেকে বেড়ে ২০ হাজার জন নাগরিকত্ব পেয়েছেন।
ইতালি কেন এই পরিবর্তন আনল?
বংশপরম্পরায় নাগরিকত্ব পাওয়ার নিয়মের সমালোচকরা বলছেন, এতে এমন লোকজন নাগরিকত্ব পাচ্ছিলেন যাদের ইতালির সঙ্গে বাস্তবিক কোনো সম্পর্ক নেই।
তাজানি বলেছেন, ‘যাদের পূর্বপুরুষ শতাব্দী আগে ইতালি ছেড়েছেন এবং যাদের ইতালির সংস্কৃতি বা ভাষার সঙ্গে কোনো সংযোগ নেই, তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে নাগরিকত্ব পাওয়া উচিত নয়।’
তিনি আরো জানান, কিছু প্রতিষ্ঠান বিপুল অর্থের বিনিময়ে মানুষের পূর্বপুরুষের ইতালীয় পরিচয় খুঁজে দিচ্ছিল, যাতে তারা নাগরিকত্ব পেতে পারেন। একই সঙ্গে বলেন, ‘আমরা কঠোরভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছি, যেন কেউ ইতালীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগকে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম বানাতে না পারে।’
লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসের অধ্যাপক ভ্যালেন্টিনো লারসিনিস বলেন, পুরনো ব্যবস্থা ইউরোপীয় শ্রমবাজারে প্রবেশ সহজ করত এবং এর অপব্যবহার হতো। তার মতে, পাসপোর্টের ক্ষেত্রে কিছু সীমা নির্ধারণের ধারণাটি যুক্তিসংগত।
এ ছাড়া নাগরিকত্ব আবেদনের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ইতালির কনস্যুলেট ও পৌরসভাগুলো অতিরিক্ত চাপের মুখে পড়েছিল। এটি সামলাতেই কেবল কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদনপ্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হয়েছে।
আরেকটি বড় সমালোচনা হলো, বংশপরম্পরায় নাগরিকত্ব পাওয়া সহজ হলেও ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী অভিবাসী শিশুদের জন্য নাগরিকত্ব পাওয়া কঠিন। বর্তমানে ইতালিতে বসবাসরত আইনসিদ্ধ অভিবাসীদের সন্তানরা ১৮ বছর বয়স হওয়ার পর এবং শৈশব থেকে ইতালিতে থাকার প্রমাণ দিলে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারেন।
লারসিনিস বলেন, ‘ইতালির অভিবাসী শিশুদের নাগরিকত্ব পাওয়ার জটিলতা বহিরাগতদের পাসপোর্ট পাওয়া নিয়ে বিতর্কের চেয়েও বড় সমস্যা।’
তিনি আরো উল্লেখ করেন, ইতালিতে নাগরিকত্ব সহজ করার জন্য আসন্ন ৮-৯ জুন ভোট হবে। এই প্রস্তাবের আওতায় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য ইতালিতে বসবাসের আবশ্যক সময়সীমা ১০ বছর থেকে কমিয়ে পাঁচ বছর করার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হবে। আর একবার ইতালির নাগরিকত্ব পাওয়া গেলে, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সন্তানদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।
অন্য দেশগুলো কী করছে?
ইতালি ও ইউরোপের বেশির ভাগ দেশ বংশপরম্পরায় নাগরিকত্ব প্রদান করে থাকে। তবে প্রতিটি দেশে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্ত থাকে। হাঙ্গেরিতে বংশোদ্ভূতরা নাগরিকত্ব পেতে পারেন, তবে তাদের ভাষাগত দক্ষতা প্রমাণ করতে হয়। পোল্যান্ডে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য প্রার্থীদের পূর্বপুরুষের ধারাবাহিকতা প্রমাণ করতে হয়। পর্তুগালের ক্ষেত্রে সেফার্দি ইহুদিরা তাদের ঐতিহাসিক পূর্বপুরুষের সংযোগ প্রমাণ করলে পাসপোর্ট পেতে পারেন।
এদিকে অভিবাসনসংক্রান্ত নীতিগুলো পুনর্বিবেচনা করছে বিভিন্ন দেশ। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি এক নির্বাহী আদেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব বন্ধের ঘোষণা দেন। যদিও এটি ১৯ ফেব্রুয়ারি কার্যকর হওয়ার কথা ছিল, তবে এক ফেডারেল বিচারক এটি অসাংবিধানিক বলে আটকে দিয়েছেন।
বিশ্ব জনসংখ্যা পর্যালোচনাবিষয়ক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের হিসাবে অন্তত ৩৩টি দেশে জন্মসূত্রে নাগরিকত্বের নিয়ম রয়েছে, যার বেশির ভাগই মেক্সিকোসহ উত্তর ও লাতিন আমেরিকায়।
২০০০ বছরের পুরনো কঙ্কালের ডিএনএ থেকে মিলল যত চমকপ্রদ তথ্য
বিবিসি

২০১৭ সালের কথা। যুক্তরাজ্যের ক্যামব্রিজ ও হান্টিংডনের মধ্যকার সড়কের উন্নয়ন কাজের জন্য খোঁড়াখুঁড়ির সময় একটি প্রাচীন দেহাবশেষ পাওয়া যায়। শুরুতে প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভেবেছিলেন, এটি হয়তো স্থানীয় কোনো সাধারণ মানুষের মরদেহ, যা সময়ের আবর্তনে ফসিলে রূপান্তরিত হয়েছে। ওই দেহাবশেষের বয়স আন্দাজ করা যায়নি তখনো।
কিন্তু গবেষণায় দেখা গেল, ক্যামব্রিজশায়ারে পাওয়া কঙ্কালটি দুই হাজার বছরের পুরনো এবং এটি সারমাশিয়ান নামে এক যাযাবর জাতিগোষ্ঠীর পুরুষের কঙ্কাল। এ তথ্য তখন রীতিমতো দ্বিধায় ফেলে দেয় গবেষকদের। কারণ সারমাশিয়ানরা ছিল পারস্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী, যাদের বসবাস ছিল রোমান সাম্রাজ্যের আরেক প্রান্ত বর্তমান রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে। অশ্বারোহী ও যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি ছিল তাদের।
আজ থেকে দুই হাজার বছর আগে এখনকার রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে জন্ম নেওয়া এক যুবক কিভাবে দুই হাজার কিলোমিটারেরও বেশি দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এখনকার ইংল্যান্ডে পৌঁছেছিলেন, তা এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল গবেষকদের সামনে। আর সে প্রশ্নের উত্তর তারা খুঁজেছেন দক্ষ গোয়েন্দাদের মতো।
সম্প্রতি কারেন্ট বায়োলজি জার্নালে তাদের প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ নিয়ে চমকপ্রদ সব তথ্য। প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাদের আবিষ্কৃত কঙ্কালটির নাম দিয়েছেন অফোর্ড ক্লুনি ২০৩৬৪৫, যা মূলত ক্যামব্রিজশায়ারের ওই গ্রাম আর নমুনা সংখ্যার মিশেল।
কঙ্কালের জাতিগত পরিচয় জানা গেল যেভাবে
ক্যামব্রিজশায়ারে একটা নালার মতো জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল দেহাবশেষটি। সঙ্গে এমন কিছু ছিল না, যা দিয়ে তার পরিচয় বা আবাস সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায়। পুরো কঙ্কালের মধ্যে সবচে সুরক্ষিত অবস্থায় ছিলো তার কানের ভেতরের দিকের হাড়। ওই হাড়েরই একটি ছোট টুকরা থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করেছিলেন লন্ডনের ফ্র্যান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউটের অ্যানসিয়েন্ট জেনোমিক ল্যাবরেটরির ড. মারিনা সিলভা।
ড. সিলভার ল্যাব থেকে পাওয়া বিশ্লেষণই প্রথম জানান দেয়, কঙ্কালের মানুষটি আসলে রোমান সাম্রাজ্যের দূরতম এক প্রান্ত থেকে এসেছিলেন।
তিনি আরো বলেন, ‘প্রথমই যেটা চোখে পড়ল, অন্য রোমানো-ব্রিটিশদের চেয়ে জিনগতভাবে অনেক আলাদা এই মানুষটি।’
আগে ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে ধারণা পেতে দালিলিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণপত্রের ওপর নির্ভর করতে হতো, আর সেসবে মোটা দাগে আর্থিক ও সামাজিকভাবে প্রভাবশালীদের কথাই থাকে। তবে হাল আমলে গবেষণার পদ্ধতিগত উৎকর্ষের কারণে ডিএনএ বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এখন সেসব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। বড় বড় ঐতিহাসিক ঘটনার নেপথ্যে থাকা সাধারণ মানুষের অজানা গল্পও বের করে আনা সম্ভব হয় এখন। যেমন হাড়ের ফসিলে লুকিয়ে থাকা হাজার বছরের পুরনো জেনেটিক কোড বলে দিতে পারে যে কারো নৃতাত্ত্বিক পরিচয়।
অফোর্ড ক্লুনিকে নিয়ে করা গবেষণাটিতে তো রীতিমতো গোয়েন্দা গল্পের আঁচ পাওয়া যায়, যেন এটি একটি ফরেনসিক তদন্তপ্রক্রিয়া। একজন সাধারণ মানুষ, যিনি ১২৬ থেকে ২২৮ সালের মধ্যকার কোনো সময়ে তার ২৫ বছরের জীবন কাটিয়েছেন। রোমানদের অধিকৃত ব্রিটেনের ক্যামব্রিজশায়ারে নালার মত কোনো এক জলাধারে যার কবর হয়েছিল। তার জীবন সম্পর্কে দুই হাজার বছর পরে এসে জানা যাচ্ছে এই গবেষণার বদৌলতে।
পিতৃভূমি থেকে এতটা দূরে যে এসেছিলেন, তা কিভাবে নিশ্চিত হওয়া গেল
এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থীরা আরেকটি গবেষণা কৌশল ব্যবহার করেন। তারা ফসিল হয়ে যাওয়া মানুষটির দাঁত পরীক্ষা করেন, যাতে ওই ব্যক্তির গ্রহণ করা খাদ্যবস্তুর রাসায়নিক ছাপ পাওয়া যায়।
বিশ্লেষণে উঠে আসে, পাঁচ বছর বয়স থেকে পরবর্তী সময়ে তার খাদ্যাভ্যাস কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। গাছের কাণ্ডের চক্রাকার দাগ থেকে যেমন সেটি কী ধরনের পরিবেশ, আবহাওয়া আর সময়ের মধ্য দিয়ে এসেছে তা জানা যায়। একইভাবে মানুষের দাঁতের প্রতিটি স্তরেও সেটি কী ধরনের উপাদানের সংস্পর্শে এসেছে তার প্রভাব থেকে যায়। তার ফলে জানা যায় ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাসের ধরন।
ছয় বছর বয়স পর্যন্ত জোয়ার ও বাজরার মতো শস্যই ছিল অফোর্ডের প্রধান খাদ্য। তখনকার দিনে সারমাশিয়ান অধ্যুষিত অঞ্চলে এই ধরনের শস্য প্রচুর পরিমাণে জন্মাত। গবেষণা দলের অন্যতম সদস্য অধ্যাপক জ্যানেট মন্টগোমারি বলেন, ‘কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার খাদ্য তালিকায় এসবের বদলে গমের আধিক্য দেখা দিয়েছিল, যা মূলত পশ্চিম ইউরোপের ফসল।’
অধ্যাপক জ্যানেট আরো বলেন, ‘এ থেকে আমরা জানতে পারি, তার গোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো তিনিই প্রথম ব্রিটেনে এসেছিলেন। পরিণত বয়সে পশ্চিমের অভিবাসী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার খাদ্য তালিকা থেকে আগের শস্যগুলো বাদ পড়ে গিয়েছিল।’
আর ঐতিহাসিক নানা তথ্য-প্রমাণে জানা যায়, ওই সময়ে রোমান সেনাবাহিনীতে কর্মরত সারমাশিয়ানদের একটি দলকে ব্রিটেনে মোতায়েন করা হয়েছিল। এমন ঐতিহাসিক তথ্য থেকে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, অফোর্ড কোনো অশ্বারোহীর ছলে হতে পারেন। কিংবা দাসও হয়ে থাকতে পারেন।
খননকাজে নেতৃত্ব দেয়া মিউজিয়াম অব লন্ডনের আর্কিওলজি বিভাগের ড. অ্যালেক্স স্মিথের মতে, ডিএনএর সূত্রে এমন একটা ঘটনাপ্রবাহের ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। তিনি বিবিসিকে বলেন, ‘এটাই প্রথম বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স।’
ড. স্মিথ বলছিলেন, ‘ডিএনএ প্রাপ্তি ও রাসায়নিক বিশ্লেষণের কৌশলের সুবাদে আমরা এখন অন্য বিষয়গুলোর দিকে নজর দিতে পারছি। জানতে পারছি রোমান শাসনামলে সমাজের গঠন, বিন্যাস ও বিবর্তনের ব্যাপারে। বোঝা যাচ্ছে, শুধু শহরগুলোতেই নয়, সে সময়ের গ্রামাঞ্চলেও ব্যাপক যাতায়াত ও স্থানান্তর ঘটত মানুষের।’
ক্রিক ইনস্টিটিউটের অ্যানসিয়েন্ট জেনোমিক ল্যাবরেটরির প্রধান ড. পন্টাস স্কগল্যান্ড বিবিসি নিউজকে বলেন, ‘নতুন প্রযুক্তি ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়ায় রূপান্তর ঘটিয়ে চলেছে।’
ড. স্কগলান্ডের ভাষ্য, ‘প্রাচীন ডিএনএর হালনাগাদ বিশ্লেষণ প্রস্তর আর ব্রোঞ্জ যুগ সম্পর্কে আমাদের জানাশোনা বাড়িয়েছে। আর এখন, উন্নত কলাকৌশলের কারণে রোমান ও পরবর্তী সময়টাও ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ধরা দিচ্ছে আমাদের কাছে।’
গাজার বিস্তীর্ণ এলাকা দখলে নিতে চায় ইসরায়েল
অনলাইন ডেস্ক

ইসরায়েলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ গাজায় সামরিক অভিযানের একটি বড় সম্প্রসারণের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আজ বুধবার উপত্যকায় সামরিক অভিযান জোরদার করার ঘোষণা দিয়ে আরো বলেছেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের ‘বিস্তীর্ণ এলাকা’ দখল করবে।
এক বিবৃতিতে কাটজ বলেছেন, যুদ্ধরত এলাকাগুলো থেকে ফিলিস্তিনি জনসংখ্যা স্থানান্তরিত করা হবে। যুদ্ধ শেষ করার একমাত্র উপায় হামাসকে নির্মূল।
এদিকে গাজার উদ্ধারকারীরা জানিয়েছেন, দুটি বাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় সকাল থেকে ১৫ জন নিহত হয়েছে। গাজার নাগরিক প্রতিরক্ষা সংস্থা জানিয়েছে, আজ বুধবার যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের দুটি বাড়িতে ইসরায়েলি বিমান হামলায় শিশুসহ কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়েছে।
বেসামরিক প্রতিরক্ষা মুখপাত্র মাহমুদ বাসাল এএফপিকে বলেছেন, ‘দক্ষিণ গাজার মধ্য খান ইউনিসে বাস্তুচ্যুতদের আশ্রয়দানকারী একটি বাড়িতে দখলদার বাহিনী (ইসরায়েলি সেনাবাহিনী) বোমা হামলা চালালে ভোরে শিশুসহ ১৩ জন শহীদ হয়। মধ্য গাজার নুসাইরাত ক্যাম্পের একটি বাড়িতে ইসরায়েলি হামলায় আরো দুজন নিহত হয়েছে।’
ইসরায়েল ইতিমধ্যেই গাজার অভ্যন্তরে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাফার জোন তৈরি করেছে। যুদ্ধের আগে ছিটমহলের প্রান্তের চারপাশে বিদ্যমান একটি এলাকা সম্প্রসারণ করেছে এবং গাজার মাঝখানে তথাকথিত নেটজারিম করিডরে একটি বৃহৎ নিরাপত্তা এলাকা যুক্ত করেছে।
একই সময়ে ইসরায়েলি নেতারা বলেছেন, তারা ছিটমহল থেকে ফিলিস্তিনিদের স্বেচ্ছায় প্রস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও একই প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, সামরিক চাপ প্রয়োগই বাকি ৫৯ জিম্মিকে ফিরিয়ে আনার সর্বোত্তম উপায়।
সূত্র : এএফপি