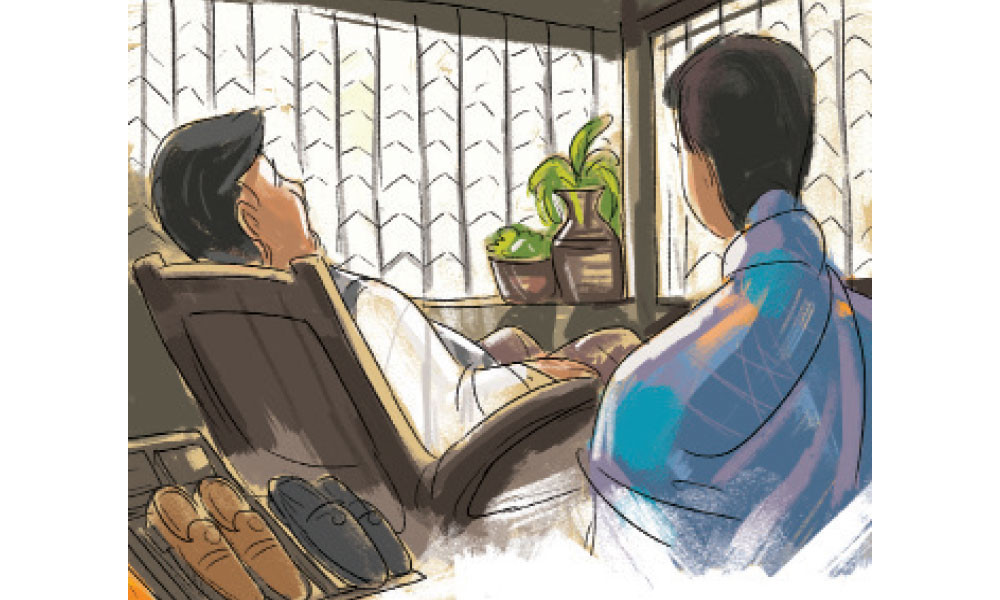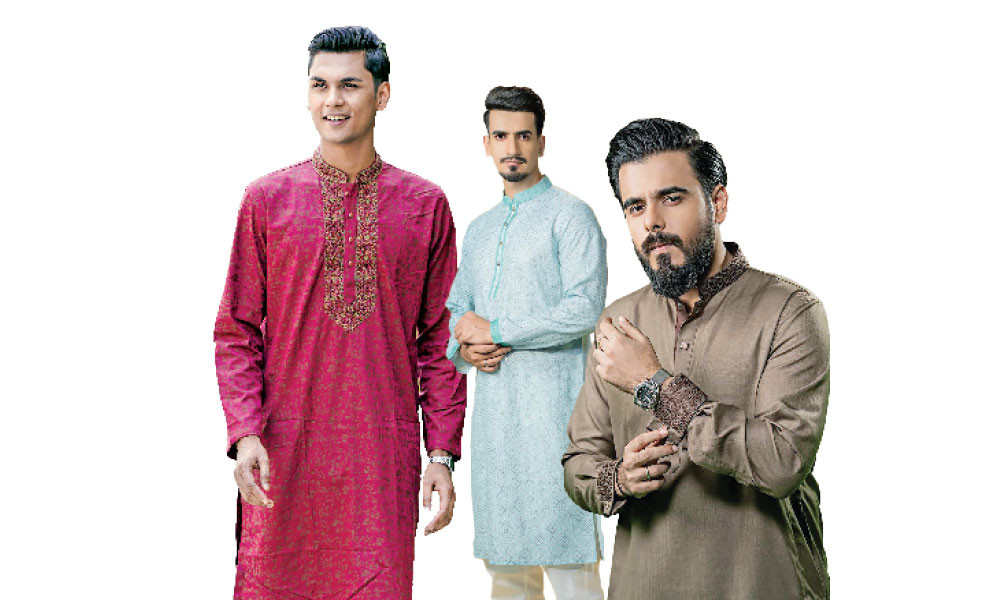দুজনই মোবাইল নিয়ে রাতভর পড়ে থাকে। ফেসবুক, টিকটক—আরো কত কী দেখে! ফাঁক পেলেই এসব নিয়ে কথা বলে দুজন। ফেসবুক অবশ্য মাশুকও দেখে। রাতে ঘুম না এলে ফেসবুকের ভিডিওগুলো দেখে।

‘ভাই, এই জোড়া নামান। নিয়া আসেন, দেখি।’
নরম কুশনের টুলে গিয়ে বসল ক্রেতা। ছোকরা দুটো আসছে না কেন? মাশুকের মাঝেমধ্যে এমন রাগ হয়, দুজনের নামে মালিকের কাছে নালিশ দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু দমে যায়। ওরা দুজনই ছেলের বয়সী। মায়া লাগে।
মাশুক বাধ্য হয়ে লেগে গেল খুবই অপ্রিয় একটা কাজে। লোকটা ধুলোমলিন পুরনো জুতা থেকে পা দুটি বের করতেই ছুটে পালাতে ইচ্ছা করল তার। মোজায় এমন গন্ধ, কেনার পর চিজ দুখানায় কখনো পানি পড়েছে কি না সন্দেহ!
লোকটা নতুন জুতা পায়ে গলিয়ে মচমচ করে কয়েক কদম হেঁটে দেখল। তারপর মুখ বাঁকা করে বলল, ‘নাহ, জুত নাই। রাইখ্যা দেন।’
লোকটার ধুলোমলিন পুরনো জুতা ডাকঘরের সিলমোহরের মতো একটা ছাপ রেখে যায় মাশুকের মনে। পরিবার থেকে দলছুট এই দেহটা এখনো বয়ে বেড়ানো যাচ্ছে। যখন আরো বয়স হবে, কর্মক্ষম থাকবে না, ঠিক ওই ধুলোমলিন জুতা বনে যাবে সে। হায় জীবন!
তাড়াহুড়া করে আসায় সকালের নাশতাটাও সারা হয়নি আজ। পেটে সারিন্দা বাজাচ্ছে ক্ষুধা। কিছু মুখে দেওয়া দরকার। কিন্তু ওরা না এলে বাইরে যাবে কী করে?
পরিষ্কার থাকার একটু বাতিক আছে মাশুকের। লোকটার নোংরা মোজা হাতড়ে গা ঘিনঘিন করছে। হাত না ধুলেই নয়। এ সময় সুরেলা আওয়াজ তোলে মোবাইলের রিংটোন। কল দিয়েছে নাবিলা। হাত ধোয়ার কথা ভুলে কল রিসিভ করে মাশুক।
‘কী করছ, বাবা?’
‘এইতো—দোকানে বসছি।’
‘আজ দুপুরে আসতে পারবা?’
‘কেন?’
‘তোমার এই একটা বিশ্রী স্বভাব, একটা প্রশ্ন করলে জবাব না দিয়া পাল্টা প্রশ্ন করো। আসতে পারবা কি না?’
‘খুব দরকার?’
‘উহু রে, আবার প্রশ্ন! আইসো।’
‘দেখি।’
‘দেখি আবার কী? দেখার কী আছে? আসবা, ব্যস।’
লাইন কেটে দেয় নাবিলা। মাশুকের হৃদয়গভীরে একটা কুলুকুলু স্রোত বয়ে যায়। ওদের কাছে যাওয়ার সুযোগ হলে এমন অনুভূতি হয়। আজব এক পরিস্থিতি। পরিবার নিজের, কিন্তু বাসা ওদের।
মাস কয়েক আগে মিরপুরের রুফটপ ওই ফ্ল্যাটে উঠেছে ওরা। নাজু, নাবিলা আর নাহিদ। বড় একটা রুম দুই ভাগ করে দুটি বানানো হয়েছে। একটায় রান্নাবান্না চলে। সেখানেই এক কোণে খাট পেতে থাকে নাজু আর নাবিলা। বাথরুম একটাই। সেটা ছাদের আরেক প্রান্তে। আরেকটা রুম নাহিদের। সেখানে জায়গা হয়নি মাশুকের। মা-মেয়ে যত স্বচ্ছন্দে একসঙ্গে থাকা যায়, বাপ-ছেলের এক রুমে থাকাটা সহজ নয়। বিশেষ করে ছেলে যদি তরুণ হয় আর মুখের ওপর বলে, ‘কী করলা জীবনে? মায়ের জীবন তো তামা করছই, আমাদের জন্যও তো কিছু করতে পারলা না!’
বাধ্য হয়ে মেসে উঠেছে মাশুক।
এর মধ্যে দোকানের ছেলে দুটি এসেছে। সমিতির মার্কেটের দোকানগুলোতে ক্রেতার ভিড় জমছে। এখানে বেশির ভাগই নিম্নমধ্যবিত্ত। তারা দেখে বেশি, কেনে কম। কিনলেও দোনামনা থাকে—ঠকলাম কি না। এর পরও জুতার দোকানে বিক্রি মন্দ না। দিনে সাত-আট জোড়া বিক্রি করতে পারলে ভালো লাভ থাকে।
দুপুরের দিকে ফোনে মালিকের কাছ থেকে ঘণ্টা তিনেকের জন্য ছুটি নেয় মাশুক। বলে, বাসায় জরুরি কাজ। ছেলে দুটির ওপর দোকানের ভার বুঝিয়ে দিয়ে মিরপুরের বাস ধরে সে। মাথায় এলোমেলো চিন্তা। হঠাৎ এই জরুরি তলব কেন? টাকার দরকার, না অন্য কোনো সমস্যা? নাজু আজকাল নিজে ফোন করে না, মেয়েকে দিয়ে করায়। এখন মাসের তৃতীয় সপ্তাহ চলছে। এই মুহূর্তে টাকা দেওয়া সম্ভব না, যা দেওয়ার তা তো দিয়েছেই।
মিরপুর-১০ গোলচত্বরে বাস থেকে নেমে যায় মাশুক। এখান থেকে বাসায় যেতে রিকশায় ৫০ টাকার মতো লাগে। মাশুক হেঁটেই যায়। গলির মাথায় সবজির ভ্যান। বাসায় কিছু সবজি নেওয়া যায়। খুশি হবে ওরা। কিন্তু দাম শুনে দমে যায় মাশুক। নতুন আলু ৭০ টাকা, করলা ৮০ টাকা, বেগুন ১০০ টাকা। সবজির দামের কাছে জীবনের দাম পানি। সস্তার সবজি অবশ্য আছে। মুলা। বিশ টাকা কেজি। মাশুক নেয় কেজিখানেক।
এ বাসায় লিফট নেই। সিঁড়ি ভেঙে ছয়তলায় ওঠা কষ্ট। প্রবল ইচ্ছাশক্তি মাশুককে টেনে তোলে। টুকটুক করে মৃদু টোকা দেয়। নাজু দরজা খোলে।
‘তুমি!’
যেন তিরিশ বছরের জীবনসঙ্গীকে চিনতে অনেক কষ্ট। মাশুক গা করে না। সয়ে গেছে। তবে নাজুর জন্য মাশুকের এখনো অনেক মায়া।
মাশুক বিরস মুখে বলে, ‘নাবু ফোন দিয়া আসতে বলল। ভাবলাম জরুরি।’
‘আসো।’
দরজা থেকে সরে জায়গা করে দেয় নাজু। পেছনে নাবিলা এসে দাঁড়িয়েছে। মাকে তীক্ষ কণ্ঠে বলে, ‘বাবাকে দেইখা চমকানোর কী আছে, মা? নয় দিন পর আসল বেচারা!’
নাজু বলে, ‘আমাকে তো বললি না?’
‘তোমাকে বইলা কী হইব? তিতা কথা ছাড়া কিছু জানো?’
‘তিতা কথা তো এমনিই বাইর হয় না। তোর বাপের চুল পাইকা সাদা হইয়া যাইতেছে, তবু আক্কেল-বুদ্ধি পাকল না! দেখ, মুলা নিয়া আসছে! এইসব বলে কোনো বাসায় নেওয়ার জিনিস!’
‘মাসের কয় তারিখ আইজ? তুমি আমার পকেটের অবস্থা দেখবা না?’
‘টাকা না থাকলে আনবা না। তাই বইলা গ্যাসের ফ্যাক্টরি নিয়া আসবা?’
নাবিলা ফিক করে হেসে ফেলে। নাজুও যোগ দেয়।
মাশুক বিরক্ত হয়ে বলে, ‘এই জন্যই তোদের কাছে আসতে ইচ্ছা করে না। ভালো কিছু করলেও মরণ! মুলা দিয়া পাতা শুঁটকির চচ্চড়ি তুমি পছন্দ করো না? এই জন্যই তো...। এখন বলো কী হইছে?’
নাবিলা বলে, ‘কিছু হয় নাই, বাবা। বাসায় আজ ভালো কিছু রান্না হইছে। আমরা পোলাও-মাংস খাব, আর তুমি বাদ থাকবা, সেইটা কি হয়?’
মাশুক এতক্ষণে খেয়াল করে, রান্নাঘর প্লাস থাকার ঘরটায় দারুণ সুবাস! কয়েক দিনের না-খাওয়া অভাগার মতো হাসি ফোটে তার। বলে ফেলে, ‘পোলাওয়ের সঙ্গে কী করছ তোমরা? গরু, না মুরগি?’
নাবিলাও হাসে, ‘দুইটাই।’
‘কী উপলক্ষে এত কিছু?’
নাজু বলে, ‘আরে, নাহিদ ওর এক বন্ধুরে খাওয়াইব। সেও রাইড শেয়ার করে।’
এখন দুপুর দুইটা। এত বেলা পর্যন্ত না-খাওয়া মাশুকের আর তর সয় না। বলে, ‘কী দিবা দাও। খুব ক্ষুধা লাগছে।’
নাজু ভেতরে ভেতরে টেনশনে অস্থির। আজকের দাওয়াতের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। নাহিদ যে বন্ধুকে নিয়ে আসবে, সেও পড়াশোনা ছেড়ে রাইড শেয়ার করে। নাহিদ বলেছে, ওর জানা মতে ছেলেটির বাজে কোনো নেশা নেই। কোনো মেয়ের সঙ্গেও নেই, তবে খুঁজছে। পছন্দমতো পেলে বিয়ে করবে। নাবিলাকে দেখে সে রকম আগ্রহ দেখালে বিয়ের কথা পাড়বে নাহিদ।
নাবিলা দেখতে-শুনতে মন্দ না। মেধাবীও। এসএসসিতে সায়েন্স থেকে জিপিএ ফাইভ পেয়েছে। মেডিক্যালে পড়ার ইচ্ছা। না হলে পাবলিক ভার্সিটি। কিন্তু নাহিদ বলে, বাবার যে অবস্থা, কলেজে থাকতে থাকতে নাবিলাকে পার করতে হবে। আইবুড়ো হলে তখন ছেলে পাওয়া মুশকিল।
নাজু একটু আপত্তি তুলেছিল, অমনি রেগে গেল ছেলেটা। বলল, ‘আমি এত বিয়ার করতে পারব না, মা। বোঝা হালকা করতে হইব। আমারও তো ভবিষ্যৎ আছে। বি প্র্যাকটিক্যাল!’
নাজু আর কিছু বলেনি। টাকা-পয়সা না থাকলে এ বয়সে অনেক অধিকার বেদখল হয়ে যায়। নাহিদ পইপই করে বলেছে, ‘বাবা যেন কিছুতেই জানতে না পারে। পরে জানাইলেই হইব।’
এ জন্যই নাজু কিছু জানায়নি মাশুককে। নাবিলাও জানে না এই দাওয়াতের আসল কারণ। মেয়েটা হুট করে বাবাকে নিয়ে আসায় এখন ভারি বিপদ হয়েছে। কখন যে ওরা এসে পড়ে! বাবাকে দেখলে নাহিদ এখন হয়তো কিছু বলবে না, পরে ঠিকই ঝাল ওঠাবে।
নাজু বলে, ‘তাড়াতাড়ি খাইয়া চইলা যাও। দেরি করলে দোকানের মালিক আবার কী বলে!’
হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় বসে পড়ে মাশুক। নাবিলা ঘরে রাখা মোটা কাগজের একটা শপিং ব্যাগ ছিঁড়ে বিছিয়ে দেয় বাবার সামনে। বলে, ‘সকালে কী দিয়ে নাশতা করছ, বাবা?’
মাশুক এড়িয়ে যায়, ‘সকালের কথা এখন জানার দরকার আছে?’
‘রোজ সকালে নাশতা করার সময় তোমার কথা মনে পড়ে, বাবা। মা দুধ-চা দিত, তুমি তেল ছাড়া পরোটা ভিজাইয়া খাইতা। মা বলে আর কাঁদে।’
‘তুইও এখন কাঁদবি নাকি?’
নাবিলা ওদিক ফিরে মুখ আড়াল করে। মাশুকের বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। করোনার আগে ভালোই ছিল ওরা। তখন এত লোয়ার লেভেলে না, বেশ ভালো একটা আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানে হিসাব বিভাগে ছিল। দুই কামরার একটা ছিমছাম বাসায় ছিল। আলাদা কিচেন, দুটি বাথরুম। নাহিদ তখন ঢাকা কলেজে অনার্সে পড়ে। নাবিলা স্কুলে। হুট করে করোনা এলো, ভোজবাজির মতো উধাও হলো চাকরিটা। তারপর কয়েকটা মাস একদম বেহদ্দ বেকার। করোনা গেলে ব্যাংকে যা ছিল, তা দিয়ে শেষরক্ষা হিসেবে একটা ফাস্ট ফুডের দোকান দিয়েছিল। জমল না। পুরো ১০ লাখ টাকা গচ্চা। নাহিদের পড়াশোনা ওখানেই শেষ। তবু ভাগ্যিস, ধারদেনা করে ওকে একটা মোটরবাইক কিনে দিতে পেরেছে। চারটা বছর ছোট-বড় নানা ঢেউ সামলে শেষে এই জুতার দোকানে ঢুকেছে মাশুক। বেতন যা পায়, তা দিয়ে কোনোমতে টেকা যায়, কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না।
বাবাকে পোলাও-মাংস বেড়ে দেয় নাবিলা। অনেক দিন এমন ভালো খাবার খায় না মাশুক। রাজ্যের ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
সব শেষে দই খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে মাশুক। নাবিলা বলে, ‘তোমার বেতন কি আর বাড়বে না, বাবা?’
‘বাড়বে কিভাবে? বাড়ানোর কথা বলারই তো সাহস হয় না।’
‘তোমার সাহস নাই দেইখাই তো আমাদের এই অবস্থা। ভাইয়া ঠিকই বলে। মালিককে বলবা যে জিনিসপত্রের দাম বেশি, চলা যায় না।’
মাশুক কিছু বলে না। হালকা নিঃশ্বাস ছাড়ে। নাজুর ফোনে রিংটোন। কল দিচ্ছে নাহিদ। বুকটা ধড়াস করে ওঠে। এসে গেছে নিশ্চয়ই! ভয়ে ভয়ে ফোন ধরে। কিন্তু না, জরুরি কি একটা কাজ পড়েছে। এখন না, রাতে আসবে ওরা। হাঁপ ছাড়ে নাজু। যাক, এ যাত্রা বাঁচা গেছে!
নাজু এবার বলে, ‘খেয়ে একটু আরাম করেই যাও। একদিন একটু লেট হইলে কী আর বলবে?’
মাশুকেরও ভরপেট খেয়ে নড়তে ইচ্ছা করে না। ওই বিছানায়ই চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। নাবিলা মাথার কাছে বসে। বাবার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে, ‘আর কয়েকটা মাস কষ্ট করো, বাবা। আমি এইচএসসি দিয়া টিউশনি করব। তোমাকে আর মেসে থাকবে হইব না। তখন আরেকটা ভালো বাসায় উঠব।’
নাবিলা বলেই চলে, ‘আর যদি ভার্সিটিতে ভর্তি হই, হলে উঠতে পারি...’
নাবিলার সব কথা কানে যায় না মাশুকের। আবেশে চোখ বুজে আসে। ঘোরলাগা চোখে স্বপ্ন দেখে সে। সবাই একসঙ্গে নতুন একটা বাসায় উঠেছে। বারান্দায় আসা নরম রোদে গা পেতে বসে আছে সে। ভেতরে চায়ের কাপে টুং টাং। এখনই আসবে ভাপ ওঠা চা। কিন্তু শীত বিকেলটা বড্ড ক্ষণস্থায়ী। কখন যে মিষ্টি বিকেল অস্তাচলে বিলীন হয়, টের পায় না মাশুক।


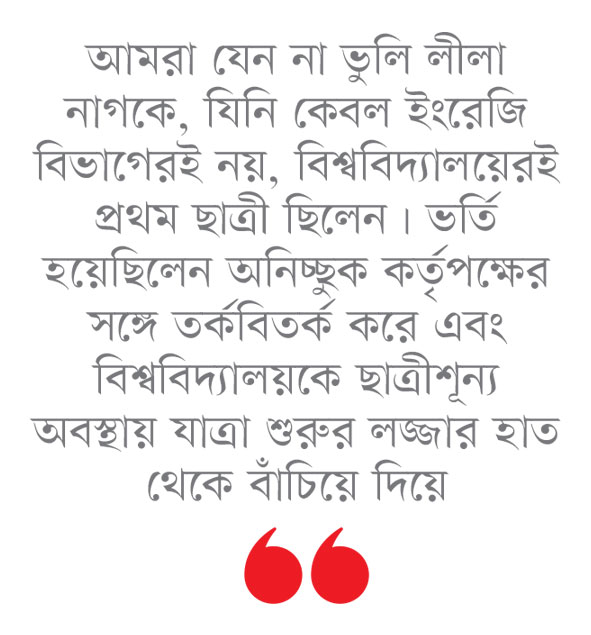 প্রেমিক ছিল আরো একজন; তবে অন্য বিভাগের এক মেয়ের। খালেদা ফ্যান্সি খানম পড়ত দর্শন বিভাগে, ওই সময়েই খ্যাতি পেয়েছিল রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে; আর তার গান শুনেই প্রেমে পতিত হয়ে গেল আমাদের এই সহপাঠী। সে সময় বেতার ভবনটি ছিল নাজিমউদ্দিন রোডে, কলা ভবনের কাছেই; খালেদার গান গাওয়া থাকলে আমাদের ওই বন্ধুটি গিয়ে বেতার ভবনের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত; একঝলক দেখবে বলে। এই কাতরতায় তার পড়াশোনাটাই মাটি হলো। ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে বিভাগ ছেড়ে চলে গেল সে রাজশাহীতে; সেখানে গিয়ে পড়েছে ইসলামের ইতিহাস। অধ্যাপকও হয়েছিল। অনেক বছর হলো বন্ধুটি চলে গেছে। আবিদ হোসেন ছিল ভীষণ চটপটে। সে থাকল না; লন্ডনে পাড়ি দিল। দ্বিতীয় বর্ষ পার করে সাবসিডিয়ারি শেষ করে এবং বিএ ডিগ্রি নিয়ে। ঠিক করেছে ব্যারিস্টার হবে। হয়েছিলও। তারপর দেশে ফিরে এসেছে, অনেক বছর পরে; ভেবেছিল থাকবে, কিন্তু পারল না। একাত্তরের ২৫শে মার্চের পরে দ্রুত চলে গেল লন্ডনে। যুদ্ধে যোগ দেবে। সেটা আর সম্ভব হয়নি। হার্ট ফেইলিউরে মারা গেছে অল্প কিছুদিন পরেই। মৃত্যু দমিয়েছে, নইলে আবিদকে দমানো ছিল খুবই কঠিন। ওর বাবা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ‘বুদ্ধির মুক্তি’ খ্যাত আবুল হোসেন; আবিদ তার বাবার সান্নিধ্য বেশিদিন পায়নি; অকালেই তাঁর মৃত্যু ঘটে; কিন্তু আবিদ পিতার উত্তরাধিকার ঠিকই পেয়েছিল। বাবা ঢাকা শহরের গোঁড়া হর্তাকর্তাদের জ্বালাতনে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়, যোগ দিয়েছিলেন আইন পেশায়; আবিদও চেয়েছিল দক্ষ ব্যারিস্টার হবে, গেছিল তাই লন্ডনে। আমাদের শিক্ষক ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ক্লাসে একদিন আবিদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; ‘আর ইউ সৈয়দ আবুল হুসেনস সান?’ চটপটে আবিদের জবাবটা ছিল, ‘ইয়েস স্যার, আই অ্যাম, বাট আই ডু নট কল মাইসেলফ সৈয়দ, বিকজ মাই ফাদার ডিডন্ট।’ ছেলেটির সাহস ছিল দুর্দান্ত। মুজিবুল হক সাহেব আমাদের ক্লাস নিয়েছেন কিছুদিন, সিএসপি হয়ে চলে যাওয়ার আগে। ব্লেকের কবিতা পড়াতেন তিনি। বলেছিলেন, ‘দিজ পোয়েমস আর সিম্পল লাইক জসীমউদ্দীনস, বাট ইনডিড ভেরি কমপ্লেক্স।’ পেছন বেঞ্চ থেকে আবিদ মন্তব্য করেছিল, ‘না বোঝাতেও কিন্তু আনন্দ আছে, স্যার।’ আবিদের টিউটরিয়াল ছিল প্রফেসর আই এইচ জুবেরীর সঙ্গে। তিনি তখন ডিন ও বিভাগীয় প্রধান; চলে যাবেন রাজশাহীতে, ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে; সেই প্রস্তুতিতে মানসিকভাবে ব্যস্ত। আবিদকে বলেছিলেন টিউটরিয়াল লিখে নিয়ে আসতে। আবিদ সে কাজ করেছিল। প্রফেসর জুবেরী তার খাতায় নানা জায়গায় লাল কালিতে দাগ দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নম্বর দিয়েছিলেন ভালোই, এ মাইনাস; তবে নিচে একটা মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলেন : ‘ইজ দিস ইওর ওউন?’ মধুর দোকানে ফেরত এসে আবিদ শিক্ষকের মন্তব্যের পিঠে লিখেছিল, ‘নাথিং ইজ মাই ওউন, স্যার, একসেপ্ট দ্য মিসটেকস।’ আমাদের ওই সময়টায় দাপট ছিল বামপন্থার; আবিদ একটি মার্ক্সবাদী আজান উদ্ভাবন করেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে দুই কানে হাত লাগিয়ে উঁচু গলায় শুরু করত তিনবার মার্ক্স মহান বলে; শেষও করত তিনবার ওই ধ্বনি দিয়ে। মাঝখানে বলত, আগামীকাল মিটিং হবে, মিটিং হবে, বিকেল পাঁচটায়, পুঁথিপত্রে।
প্রেমিক ছিল আরো একজন; তবে অন্য বিভাগের এক মেয়ের। খালেদা ফ্যান্সি খানম পড়ত দর্শন বিভাগে, ওই সময়েই খ্যাতি পেয়েছিল রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে; আর তার গান শুনেই প্রেমে পতিত হয়ে গেল আমাদের এই সহপাঠী। সে সময় বেতার ভবনটি ছিল নাজিমউদ্দিন রোডে, কলা ভবনের কাছেই; খালেদার গান গাওয়া থাকলে আমাদের ওই বন্ধুটি গিয়ে বেতার ভবনের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে থাকত; একঝলক দেখবে বলে। এই কাতরতায় তার পড়াশোনাটাই মাটি হলো। ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে বিভাগ ছেড়ে চলে গেল সে রাজশাহীতে; সেখানে গিয়ে পড়েছে ইসলামের ইতিহাস। অধ্যাপকও হয়েছিল। অনেক বছর হলো বন্ধুটি চলে গেছে। আবিদ হোসেন ছিল ভীষণ চটপটে। সে থাকল না; লন্ডনে পাড়ি দিল। দ্বিতীয় বর্ষ পার করে সাবসিডিয়ারি শেষ করে এবং বিএ ডিগ্রি নিয়ে। ঠিক করেছে ব্যারিস্টার হবে। হয়েছিলও। তারপর দেশে ফিরে এসেছে, অনেক বছর পরে; ভেবেছিল থাকবে, কিন্তু পারল না। একাত্তরের ২৫শে মার্চের পরে দ্রুত চলে গেল লন্ডনে। যুদ্ধে যোগ দেবে। সেটা আর সম্ভব হয়নি। হার্ট ফেইলিউরে মারা গেছে অল্প কিছুদিন পরেই। মৃত্যু দমিয়েছে, নইলে আবিদকে দমানো ছিল খুবই কঠিন। ওর বাবা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ‘বুদ্ধির মুক্তি’ খ্যাত আবুল হোসেন; আবিদ তার বাবার সান্নিধ্য বেশিদিন পায়নি; অকালেই তাঁর মৃত্যু ঘটে; কিন্তু আবিদ পিতার উত্তরাধিকার ঠিকই পেয়েছিল। বাবা ঢাকা শহরের গোঁড়া হর্তাকর্তাদের জ্বালাতনে ত্যক্তবিরক্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়, যোগ দিয়েছিলেন আইন পেশায়; আবিদও চেয়েছিল দক্ষ ব্যারিস্টার হবে, গেছিল তাই লন্ডনে। আমাদের শিক্ষক ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ক্লাসে একদিন আবিদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; ‘আর ইউ সৈয়দ আবুল হুসেনস সান?’ চটপটে আবিদের জবাবটা ছিল, ‘ইয়েস স্যার, আই অ্যাম, বাট আই ডু নট কল মাইসেলফ সৈয়দ, বিকজ মাই ফাদার ডিডন্ট।’ ছেলেটির সাহস ছিল দুর্দান্ত। মুজিবুল হক সাহেব আমাদের ক্লাস নিয়েছেন কিছুদিন, সিএসপি হয়ে চলে যাওয়ার আগে। ব্লেকের কবিতা পড়াতেন তিনি। বলেছিলেন, ‘দিজ পোয়েমস আর সিম্পল লাইক জসীমউদ্দীনস, বাট ইনডিড ভেরি কমপ্লেক্স।’ পেছন বেঞ্চ থেকে আবিদ মন্তব্য করেছিল, ‘না বোঝাতেও কিন্তু আনন্দ আছে, স্যার।’ আবিদের টিউটরিয়াল ছিল প্রফেসর আই এইচ জুবেরীর সঙ্গে। তিনি তখন ডিন ও বিভাগীয় প্রধান; চলে যাবেন রাজশাহীতে, ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে; সেই প্রস্তুতিতে মানসিকভাবে ব্যস্ত। আবিদকে বলেছিলেন টিউটরিয়াল লিখে নিয়ে আসতে। আবিদ সে কাজ করেছিল। প্রফেসর জুবেরী তার খাতায় নানা জায়গায় লাল কালিতে দাগ দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু নম্বর দিয়েছিলেন ভালোই, এ মাইনাস; তবে নিচে একটা মন্তব্য জুড়ে দিয়েছিলেন : ‘ইজ দিস ইওর ওউন?’ মধুর দোকানে ফেরত এসে আবিদ শিক্ষকের মন্তব্যের পিঠে লিখেছিল, ‘নাথিং ইজ মাই ওউন, স্যার, একসেপ্ট দ্য মিসটেকস।’ আমাদের ওই সময়টায় দাপট ছিল বামপন্থার; আবিদ একটি মার্ক্সবাদী আজান উদ্ভাবন করেছিল। উঠে দাঁড়িয়ে দুই কানে হাত লাগিয়ে উঁচু গলায় শুরু করত তিনবার মার্ক্স মহান বলে; শেষও করত তিনবার ওই ধ্বনি দিয়ে। মাঝখানে বলত, আগামীকাল মিটিং হবে, মিটিং হবে, বিকেল পাঁচটায়, পুঁথিপত্রে।

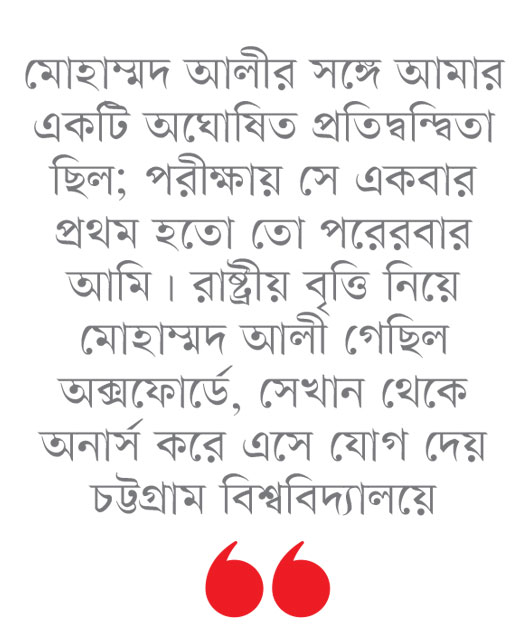 ব্যারিস্টার হয়েছিল আরো একজন, রশীদুজ্জামান। পার্টিশনের আগে কলকাতায় আমরা একই স্কুলে পড়েছি, পরে দেখি ঢাকায় আমরা আইএ পড়ছি একই কলেজে। ওর বাবা ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের জজ। রশীদ বিলেত গেছে অনার্স পরীক্ষা দিয়েই। সেও মারা গেছে অনেক দিন হলো। লতিফুর রহমান চলে গেছে ক’বছর হলো। আবিদের মতোই সেও যশোরের; তার বাবাও আইনজীবী ছিলেন। যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন দুবার। পার্টিশনের সময় সদস্য ছিলেন আইন পরিষদের। লতিফুরের ডাকনাম ছিল শান্তি; খুবই জনপ্রিয় ছিল সে বন্ধুমহলে। নিয়মিত টেনিস খেলত হলের টেনিস কোর্টে। শান্তিও গেছিল আইন পেশায়ই, হাইকোর্টের জজ হয়েছে, আরো পরে চিফ জাস্টিস, এবং অবসর-পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তো ছিলই, পরবর্তী সময়ে আমরা পরস্পরের আত্মীয়ও হয়ে গিয়েছিলাম, বৈবাহিক সূত্রে।
ব্যারিস্টার হয়েছিল আরো একজন, রশীদুজ্জামান। পার্টিশনের আগে কলকাতায় আমরা একই স্কুলে পড়েছি, পরে দেখি ঢাকায় আমরা আইএ পড়ছি একই কলেজে। ওর বাবা ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের জজ। রশীদ বিলেত গেছে অনার্স পরীক্ষা দিয়েই। সেও মারা গেছে অনেক দিন হলো। লতিফুর রহমান চলে গেছে ক’বছর হলো। আবিদের মতোই সেও যশোরের; তার বাবাও আইনজীবী ছিলেন। যশোর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন দুবার। পার্টিশনের সময় সদস্য ছিলেন আইন পরিষদের। লতিফুরের ডাকনাম ছিল শান্তি; খুবই জনপ্রিয় ছিল সে বন্ধুমহলে। নিয়মিত টেনিস খেলত হলের টেনিস কোর্টে। শান্তিও গেছিল আইন পেশায়ই, হাইকোর্টের জজ হয়েছে, আরো পরে চিফ জাস্টিস, এবং অবসর-পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান। তাঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তো ছিলই, পরবর্তী সময়ে আমরা পরস্পরের আত্মীয়ও হয়ে গিয়েছিলাম, বৈবাহিক সূত্রে।
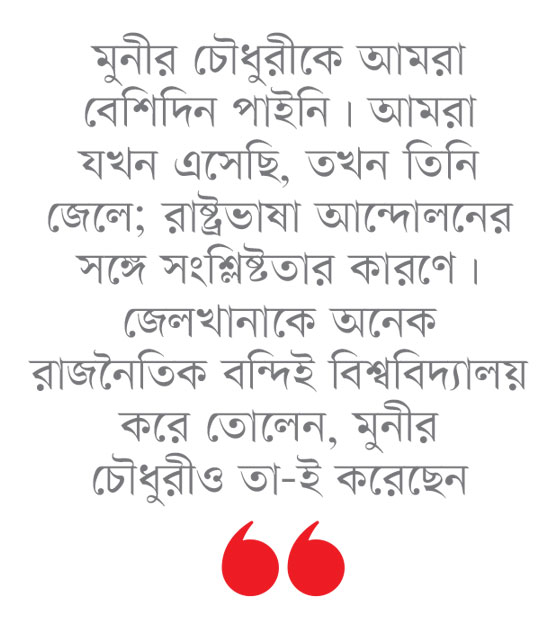 আহসানুল হক ও আমি বিভাগের শিক্ষক ছিলাম দীর্ঘদিন। আহসানুল হক গিয়েছিল ব্রিস্টলে। সেখানে তার গবেষণার বিষয় ছিল মিডল ইংলিশ লিটারেচার ড্রিম পোয়েট্রি। সেটি বই হিসেবে বের হয়েছে। পরে গবেষণা করেছে এলিয়টর বক্তব্যের আলোকে এলিয়টের নিজের কবিতা নিয়ে। আহসানুল হক অত্যন্ত সচেতন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে। সত্তর-একাত্তরে সে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক; হানাদার পাকিস্তানি সেনারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রেখেছিল বেশ কয়েক মাস। সেও তো চলে গেল। মোহাম্মদ আলী এসেছিল চট্টগ্রাম থেকে। মেধাবী ও মনোযোগী ছাত্র; সবাই বলত জেনুইন স্কলার। মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে আমার একটি অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল; পরীক্ষায় সে একবার প্রথম হতো তো পরেরবার আমি। রাষ্ট্রীয় বৃত্তি নিয়ে মোহাম্মদ আলী গেছিল অক্সফোর্ডে, সেখান থেকে অনার্স করে এসে যোগ দেয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সে। পরে উপাচার্যও হয়েছিল। আরো পরে ইউজিসির সদস্য। মোহাম্মদ আলীও তো চলে গেল ক’বছর হলো। মোহাম্মদ মোশতাকের পেশা দাঁড়িয়েছিল সাংবাদিকতা। প্রথমে পত্রিকায়, পরে রেডিওতে। অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিল সে। চলে গেছে বেশ আগেই। চোখে ভারী চশমাওয়ালা আনওয়ার হোসেন ছিল খুবই শান্ত স্বভাবের। পড়াশোনা শেষে কাজ নিয়েছিল ব্যাংকে। সেও আর নেই। আনওয়ারকে আমার মনে আছে বিশেষ এক কারণে। ওর এক ভাই থাকতেন লন্ডনে। তখন নামকরা পত্রিকা ছিল ত্রৈমাসিক ‘এনকাউন্টার’; সম্পাদক কবি স্টিফেন স্পেন্ডার। ছোট ভাইয়ের কাজে লাগবে জেনে আনওয়ারের ভাই পত্রিকার ছয়টি সংখ্যার একটি করে কপি পাঠিয়েছিলেন ডাকযোগে। আনওয়ার সেগুলো দেখেটেখে আমাকে দিয়ে একগাল হেসে বলেছিল, ‘তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশি।’ তা, আমার কাজে লেগেছিল বৈকি। আমি অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে সব কটি সংখ্যা পড়েছি। বিশেষভাবে মনে পড়ে নীরদ সি চৌধুরীর একটি লেখা, যাতে তিনি ই এম ফরস্টারের ‘এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া’ পাঠে রুষ্ট এক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। মোতাহার হোসেন এসেছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে। ভালো ছাত্র, কিন্তু একেবারেই নতুন ও অপরিচিত পরিবেশে তাকে ভারি নিঃসঙ্গ ঠেকত। পড়াশোনা শেষ করে অধ্যাপনা করেছে কলেজে। কয়েক বছর আগে তার মৃত্যুসংবাদ পড়েছি খবরের কাগজে। মাহবুবুর রহমানও কলেজে গিয়েছিল, অধ্যাপক হিসেবে; তার পরে আর খবর পাইনি।
আহসানুল হক ও আমি বিভাগের শিক্ষক ছিলাম দীর্ঘদিন। আহসানুল হক গিয়েছিল ব্রিস্টলে। সেখানে তার গবেষণার বিষয় ছিল মিডল ইংলিশ লিটারেচার ড্রিম পোয়েট্রি। সেটি বই হিসেবে বের হয়েছে। পরে গবেষণা করেছে এলিয়টর বক্তব্যের আলোকে এলিয়টের নিজের কবিতা নিয়ে। আহসানুল হক অত্যন্ত সচেতন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে। সত্তর-একাত্তরে সে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক; হানাদার পাকিস্তানি সেনারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রেখেছিল বেশ কয়েক মাস। সেও তো চলে গেল। মোহাম্মদ আলী এসেছিল চট্টগ্রাম থেকে। মেধাবী ও মনোযোগী ছাত্র; সবাই বলত জেনুইন স্কলার। মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে আমার একটি অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল; পরীক্ষায় সে একবার প্রথম হতো তো পরেরবার আমি। রাষ্ট্রীয় বৃত্তি নিয়ে মোহাম্মদ আলী গেছিল অক্সফোর্ডে, সেখান থেকে অনার্স করে এসে যোগ দেয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সে। পরে উপাচার্যও হয়েছিল। আরো পরে ইউজিসির সদস্য। মোহাম্মদ আলীও তো চলে গেল ক’বছর হলো। মোহাম্মদ মোশতাকের পেশা দাঁড়িয়েছিল সাংবাদিকতা। প্রথমে পত্রিকায়, পরে রেডিওতে। অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিল সে। চলে গেছে বেশ আগেই। চোখে ভারী চশমাওয়ালা আনওয়ার হোসেন ছিল খুবই শান্ত স্বভাবের। পড়াশোনা শেষে কাজ নিয়েছিল ব্যাংকে। সেও আর নেই। আনওয়ারকে আমার মনে আছে বিশেষ এক কারণে। ওর এক ভাই থাকতেন লন্ডনে। তখন নামকরা পত্রিকা ছিল ত্রৈমাসিক ‘এনকাউন্টার’; সম্পাদক কবি স্টিফেন স্পেন্ডার। ছোট ভাইয়ের কাজে লাগবে জেনে আনওয়ারের ভাই পত্রিকার ছয়টি সংখ্যার একটি করে কপি পাঠিয়েছিলেন ডাকযোগে। আনওয়ার সেগুলো দেখেটেখে আমাকে দিয়ে একগাল হেসে বলেছিল, ‘তোমার প্রয়োজন আমার চেয়ে বেশি।’ তা, আমার কাজে লেগেছিল বৈকি। আমি অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে সব কটি সংখ্যা পড়েছি। বিশেষভাবে মনে পড়ে নীরদ সি চৌধুরীর একটি লেখা, যাতে তিনি ই এম ফরস্টারের ‘এ প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া’ পাঠে রুষ্ট এক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। মোতাহার হোসেন এসেছিল চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে। ভালো ছাত্র, কিন্তু একেবারেই নতুন ও অপরিচিত পরিবেশে তাকে ভারি নিঃসঙ্গ ঠেকত। পড়াশোনা শেষ করে অধ্যাপনা করেছে কলেজে। কয়েক বছর আগে তার মৃত্যুসংবাদ পড়েছি খবরের কাগজে। মাহবুবুর রহমানও কলেজে গিয়েছিল, অধ্যাপক হিসেবে; তার পরে আর খবর পাইনি।
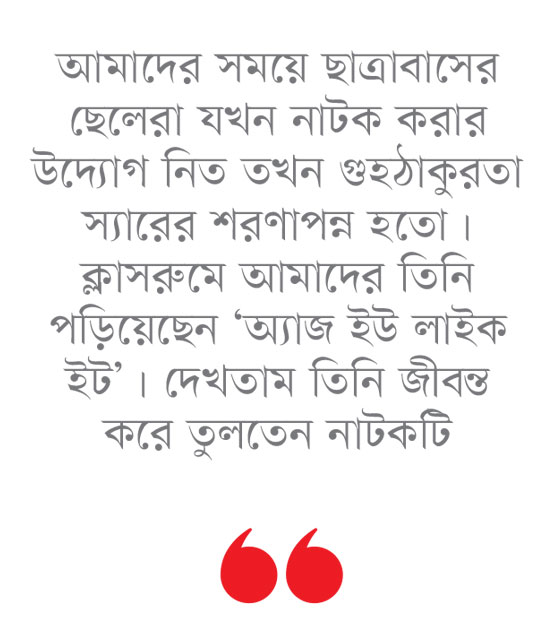 থেকে সম্মিলিত পরিচয়পত্র ছাপিয়ে আনার। একবার তো আমার সারা রাতই কেটেছে প্রেসে। খুব সকালে ছাপানো বুকলেট প্যাকেটে করে নিয়ে হলে গেছি; তাতে অন্যরা কতটা উত্ফুল্ল হয়েছে জানা হয়নি, কিন্তু আমি যে গৌরব অনুভব করেছি তাতে সন্দেহ নেই। নির্বাচনের দিন মাইক্রোফোনে প্রবল প্রচারণা চলত, তাতেও আমার সক্রিয় অংশগ্রহণে কোনো ত্রুটি ছিল না।
থেকে সম্মিলিত পরিচয়পত্র ছাপিয়ে আনার। একবার তো আমার সারা রাতই কেটেছে প্রেসে। খুব সকালে ছাপানো বুকলেট প্যাকেটে করে নিয়ে হলে গেছি; তাতে অন্যরা কতটা উত্ফুল্ল হয়েছে জানা হয়নি, কিন্তু আমি যে গৌরব অনুভব করেছি তাতে সন্দেহ নেই। নির্বাচনের দিন মাইক্রোফোনে প্রবল প্রচারণা চলত, তাতেও আমার সক্রিয় অংশগ্রহণে কোনো ত্রুটি ছিল না।
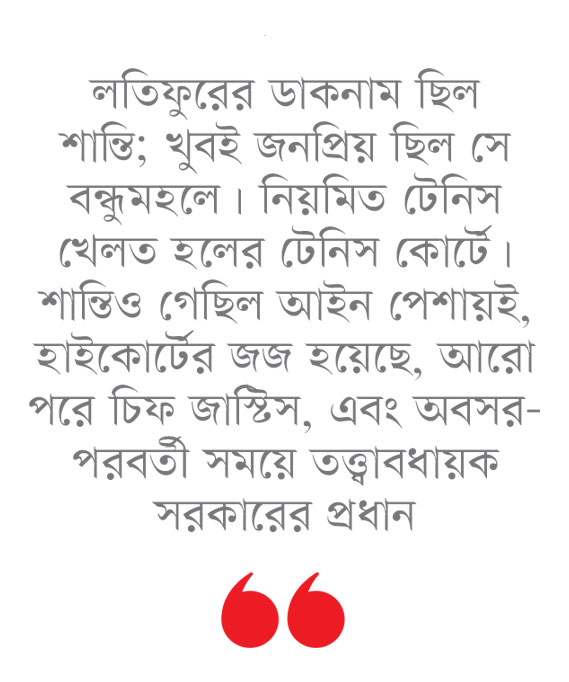 একটা অভ্যস্ত ছিলেন না। ব্যতিক্রম ছিলেন দুজন—জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও মুনীর চৌধুরী। এটা হয়তো নিতান্ত কাকতালীয় নয় যে তাঁরা দুজনেই আলবদর বাহিনীর দ্বারা শহীদ হয়েছেন একাত্তরে। আমাদের সময়ে ছাত্রাবাসের ছেলেরা যখন নাটক করার উদ্যোগ নিত তখন গুহঠাকুরতা স্যারের শরণাপন্ন হতো। ক্লাসরুমে আমাদের তিনি পড়িয়েছেন ‘অ্যাজ ইউ লাইক ইট’। দেখতাম তিনি জীবন্ত করে তুলতেন নাটকটি। একবার তিনি সুইনবর্নের ‘অ্যাটালান্টা ইন ক্যালিডন’ নাট্যকাব্য পড়াতে গিয়ে ইংরেজ কবির অ্যাফ্রোডাইটির উপস্থাপনার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বশী’র। দুটি টেক্সটই পাঠ করে শুনিয়েছেন। তিনি বলে দেননি, কিন্তু আমাদের পক্ষে বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি যে রবীন্দ্রনাথ কতটা উঁচু মানের কবি ছিলেন অন্যদের তুলনায়।
একটা অভ্যস্ত ছিলেন না। ব্যতিক্রম ছিলেন দুজন—জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা ও মুনীর চৌধুরী। এটা হয়তো নিতান্ত কাকতালীয় নয় যে তাঁরা দুজনেই আলবদর বাহিনীর দ্বারা শহীদ হয়েছেন একাত্তরে। আমাদের সময়ে ছাত্রাবাসের ছেলেরা যখন নাটক করার উদ্যোগ নিত তখন গুহঠাকুরতা স্যারের শরণাপন্ন হতো। ক্লাসরুমে আমাদের তিনি পড়িয়েছেন ‘অ্যাজ ইউ লাইক ইট’। দেখতাম তিনি জীবন্ত করে তুলতেন নাটকটি। একবার তিনি সুইনবর্নের ‘অ্যাটালান্টা ইন ক্যালিডন’ নাট্যকাব্য পড়াতে গিয়ে ইংরেজ কবির অ্যাফ্রোডাইটির উপস্থাপনার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ‘উর্বশী’র। দুটি টেক্সটই পাঠ করে শুনিয়েছেন। তিনি বলে দেননি, কিন্তু আমাদের পক্ষে বুঝতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি যে রবীন্দ্রনাথ কতটা উঁচু মানের কবি ছিলেন অন্যদের তুলনায়।