মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের পাল্টাপাল্টি শুল্ক আরোপের মধ্য দিয়ে কি বিশ্বে নতুন করে বাণিজ্যযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল? বিশ্ব কি আবার একটা মহামন্দার দিকে এগিয়ে যাবে? এসব প্রশ্নে বিশ্বজুড়ে এখন তোলপাড়। এই উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কী হবে? আমরা কি বাণিজ্যযুদ্ধের বলি হতে যাচ্ছি? আমাদের অর্থনীতির জন্য এটিই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। চীনের ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প গত বুধবার তাঁর প্রধান অর্থনৈতিক শত্রুর ওপর ১২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপের পাল্টা হিসেবে শুরুতে চীন মার্কিন পণ্যের ওপর ৮৪ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেও গতকাল শুক্রবার তা ১২৫ শতাংশে উন্নীত করেছে।
বিশেষ লেখা
বাণিজ্যযুদ্ধে বেসরকারি খাতকে পাশে নিতে হবে
- অদিতি করিম
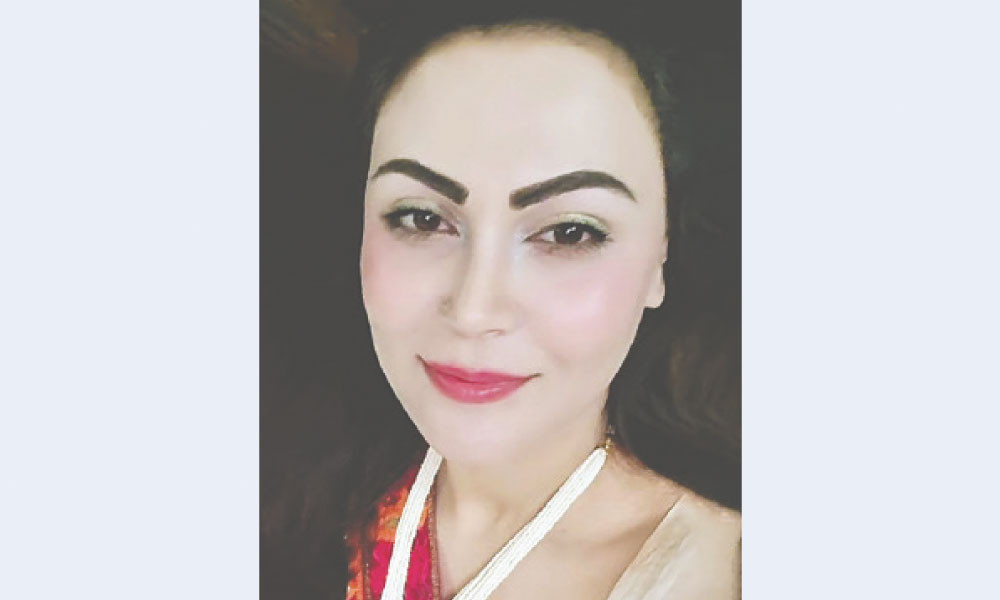
চীন যদি অর্থনৈতিক চাপে পড়ে তাহলে অনিবার্যভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। তা ছাড়া বিশ্ব অর্থনীতির টালমাটাল পরিস্থিতি চাপে ফেলবে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে।
গত বছর ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের অর্থনীতির চিত্রপট ভালো নয়। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একমাত্র ভরসা এখন প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। প্রবাসীরা নিজেদের উজাড় করে দেশে রেমিট্যান্স পাঠাচ্ছেন। কিন্তু এই রেমিট্যান্স-প্রবাহ সারা বছর একই রকম থাকবে—এটি ভাবা ঠিক নয়।
অর্থনীতিতে বিগত সরকারের আমলে বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ এবং অর্থপাচারের কারণে একটা সংকট আগে থেকেই ছিল। সেই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য অর্থনৈতিক সংস্কারের যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হচ্ছে, সেই উদ্যোগগুলো অবশ্যই ভালো। কিন্তু ব্যাংকিং খাতের সংস্কার বা খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনা, পাচার করা অর্থ ফেরত আনা, এই কাজগুলো দীর্ঘমেয়াদি। চটজলদি এর সুফল পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে আইএমএফের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল ঢাকায় এসেছে। এই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের বৈঠক হচ্ছে। তারা বাংলাদেশে ঋণের পরবর্তী কিস্তির ছাড় দেবে কি না, সে নিয়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। এ পর্যন্ত যেটুকু খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে, এই ঋণছাড়ের আগে তারা বাংলাদেশে কিছু দৃশ্যমান সংস্কার দেখতে চায়। এসব সংস্কারের মধ্যে কর ব্যবস্থাপনা সংস্কার, করের পরিধি বাড়ানো এবং খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এটি করতে গিয়ে সরকারকে হয়তো জনগণের ওপর বাড়তি করের বোঝা চাপাতে হবে। অন্যদিকে নতুন কর্মসংস্থান প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। অর্থনীতির যখন এমন চিত্র, তখন বিশ্ববাণিজ্যে অস্থিরতা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের অনড় বাণিজ্য যুদ্ধাবস্থা বাংলাদেশের জন্য কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করবে। এ সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে হবে দক্ষতার সঙ্গে, সম্মিলিতভাবে। তা না হলে শুধু অর্থনীতি বিপর্যস্ত হবে না, রাজনৈতিক সংস্কারসহ অন্য সংস্কারগুলোও মুখ থুবড়ে পড়বে, হবে প্রশ্নবিদ্ধ।
আমরা লক্ষ করেছি, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন, তার পরপরই প্রধান উপদেষ্টা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকের মাধ্যমে দ্রুত করণীয় বিষয়ে চটজলদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধান উপদেষ্টা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা দুজনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বকে চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠিতে তিন মাসের জন্য আরোপিত শুল্ক স্থগিত রাখার আহ্বান জানান। গত বুধবার বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশে বাড়তি শুল্ক আরোপের আদেশ ৯০ দিনের জন্য স্থগিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান। এটি খুবই ইতিবাচক। বাংলাদেশ কিছু বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও ভাবছে। কিন্তু শুধু বাংলাদেশ ব্যাংক, আমলা কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সঙ্গে নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব নয়।
আমাদের মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রায় ৯০ শতাংশ অবদান রাখে বেসরকারি খাত। বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র, মাঝারি শিল্প এবং ছোট ছোট শিল্প কারখানাগুলো এ দেশের অর্থনীতির প্রধান শক্তি। বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের ৯০ শতাংশের বেশি বেসরকারি খাত থেকে আসে। এই যে বিনিয়োগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো, এই বিনিয়োগ সম্মেলনে যেসব বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, তাঁরা বিনিয়োগ করবেন বেসরকারি খাতেই। কিন্তু বেসরকারি খাত যদি আতঙ্কিত থাকে, উদ্বিগ্ন থাকে এবং সরকার যদি তাঁদের আস্থায় না নেন, তাহলে এ ধরনের বেসরকারি বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়িত হবে না। এ কারণেই সরকারকে এখন বেসরকারি খাতকে আস্থায় নিতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ৩৭ শতাংশ শুল্ক আরোপ করলেন, তখন বাণিজ্য উপদেষ্টার উচিত ছিল পোশাক খাতের ব্যবসায়ী এবং মালিকদের সঙ্গে দ্রুত বৈঠক করা। এই বৈঠকের মাধ্যমে তাদের আস্থায় নেওয়া, তাদের পরামর্শ নেওয়া। কারণ ৩৭ শতাংশ শুল্কের পর পরিস্থিতি কী হবে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাংলাদেশকে কিভাবে মোকাবেলা করতে হবে, সেটা সবচেয়ে ভালো জানেন পোশাক খাতের মালিকরাই। পোশাক খাতের মালিকরা সরাসরি ক্রেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন, কথা বলছেন এবং করণীয় নিয়ে তাঁরা চিন্তা-ভাবনা করছেন। তাঁদের চিন্তা-ভাবনাগুলোকে সামষ্টিক রূপ দিয়ে সরকারের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।
বর্তমানে অর্থনীতিতে যে সংকটগুলো চলছে, সেই সংকটগুলোর সমাধানের পথও খুঁজে পেতে হবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে। আমরা জানি, বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তারা তাঁদের কারখানা এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে সচল রাখতে চান। শুধু নিজেদের প্রয়োজনে নয়, দেশের স্বার্থে তাদের রয়েছে অসাধারণ উদ্ভাবনী প্রাণশক্তি, কর্মমুখরতা। এই কর্মমুখরতা ও উদ্দীপনাকে অন্তর্বর্তী সরকার কাজে লাগাতে পারে। বাংলাদেশের বেসরকারি খাত আমাদের অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। তারাই আমাদের অর্থনীতিকে আজকের জায়গায় নিয়ে এসেছে। ছোট উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে বড় বড় শিল্প গ্রুপগুলোই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের দূরে ঠেলে দিয়ে বা তাদের মধ্যে বিভেদ-বিভক্তি সৃষ্টি করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা যাবে না।
আমরা একটা কঠিন বিশ্ব বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে একদিকে যেমন বৈদেশিক নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে, অন্যদিকে একটি অনিশ্চিত রাজনৈতিক ভবিষ্যতের কারণে বিনিয়োগকারী শিল্পপতিরা বিনিয়োগের নতুন উদ্যোগ গ্রহণে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। তা ছাড়া ৫ আগস্টের পর থেকে আমরা লক্ষ করেছি, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনো কোনো মহল আক্রমণাত্মক আচরণ করছেন। ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা সবাই জানি, গত ১৫ বছর বাংলাদেশের কী অবস্থা ছিল। ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করার জন্য সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক করতেই হবে—এর কোনো বিকল্প ছিল না। এটি বাংলাদেশের বাস্তবতা। যেখানে একটি গ্যাসের লাইন পাতার জন্য মন্ত্রী বা নীতিনির্ধারকদের কাছে ধরনা দিতে হয়। ব্যাংক ঋণের জন্য সরকারের সুনজরে থাকতে হয়। এই বাস্তবতাকে যদি কেউ অস্বীকার করে কোনো ব্যবসায়ীকে ফ্যাসিবাদের দোসর বা সাবেক সরকারের সুবিধাভোগীর তকমা দেয়, সেটা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কারণ ব্যবসায়ীরা কোনো দলের নন, ব্যবসায়ীরা কোন ব্যক্তিকে সমর্থন করেন না। তাঁদের দায়বদ্ধতা শুধু দেশের প্রতি।
গত ৮ এপ্রিল বিনিয়োগ সম্মেলনে বিডার নির্বাহী পরিচালক একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ফলে যেন বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।’ এটি হলো সব শিল্পোদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ীর মনের কথা। সরকার যাবে, সরকার আসবে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখবেন। তাঁদের যদি হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়, তাঁদের কাজে যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়, তাহলে কোনোভাবেই সেটি ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনবে না। এটি অর্থনীতিকে আরো সংকটের গভীরে নিয়ে যাবে।
বর্তমানে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে। এরই মধ্যে মার্কিন-চীনের বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে খুব সাবধানে এগোতে হবে। আমাদের পথ পরিক্রমা কী হবে, সে বিষয়ে শুধু আমলাদের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। একেবারে মাঠে যারা যুদ্ধ করছেন, সেসব অর্থনৈতিক যোদ্ধা হলেন আমাদের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও দেশি বিনিয়োগকারীরা। তাঁদের আস্থায় নিতে হবে। তাদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে। সরকার যদি রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য রাজনীতিবিদদের সঙ্গে বারবার বৈঠক করেন, তাহলে অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তা বা শিল্পপতিদের সঙ্গে বারবার বৈঠক করতে অসুবিধা কোথায়? তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে অনেকে মনে করেন।
আমাদের প্রধান উপদেষ্টা একজন বিচক্ষণ মানুষ। তিনি উদার মনের অধিকারী। যেকোনো প্রয়োজনে তিনি সবাইকে ডেকে আলাপ-আলোচনার একটি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি চালু করেছেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আমলান্ত্রিক বাধাও তিনি দূর করেছেন। এখন তাঁর দ্রুত উচিত বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অবিলম্বে বৈঠক করা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি আমাদের মোকাবেলা করতে হবে সম্মিলিতভাবে।
লেখক : নাট্যকার ও কলাম লেখক
ই-মেইল: auditekarim@gmail.com
সম্পর্কিত খবর
শুল্কঝড়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আঞ্চলিক-দ্বিপক্ষীয় চুক্তিতে জোর
- ছায়া সংসদে ফাহমিদা খাতুন
নিজস্ব প্রতিবেদক

সারা বিশ্বে এখন শুল্কঝড় বইছে। মার্কিন প্রশাসন শুল্কহার বৃদ্ধিতে কোনো নিয়ম-কানুনের ধার ধারেনি। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে শুল্ক আরোপ নিয়ে পরস্পরবিরোধী অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছে। বাংলাদেশও এই চ্যালেঞ্জের বাইরে নয়।
গতকাল শনিবার রাজধানীর এফডিসিতে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্কহারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা নিয়ে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি আয়োজিত ছায়া সংসদে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ সভাপতিত্ব করেন।
ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, ‘বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ কর আরোপের প্রক্রিয়া ত্রুটিপূর্ণ। তবে ট্রাম্পের উচ্চ শুল্কনীতি আমাদের জন্য ওয়েক-আপ কল। ব্যক্তি সমালোচনা না করে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বাড়াতে হবে। দেশের করকাঠামো শক্তিশালী করতে আয়কর আদায়ে জোর দিতে হবে।
তিনি বলেন, ‘শুল্ক ও অশুল্ক বাধা কাটিয়ে বাণিজ্যের সম্প্রসারণে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) গঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রভাবশালী দেশগুলো ডব্লিউটিওর নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা করেনি। তাই সংস্থাটি এ ক্ষেত্রে সেভাবে প্রভাব রাখতে পারেনি। এর পর থেকেই নিজেদের মধ্যে সমমনা ১৫ থেকে ২০টি দেশ মিলে একাধিক জোট করে সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতের মধ্য দিয়ে বাণিজ্য করছে।
ড. ফাহমিদা খাতুন আরো বলেন, ‘বাণিজ্য সক্ষমতা বাড়াতে আমরা অনেক দিন ধরেই বেশ কিছু দেশের সঙ্গে এফটিএ করার কথা বলে আসছি। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, প্রতিযোগী দেশ ভিয়েতনামে যেখানে ৫০ দেশের সঙ্গে এফটি রয়েছে সেখানে আমাদের রয়েছে শুধু ভুটানের সঙ্গে। যত দ্রুত সম্ভব আরো কিছু দেশের সঙ্গে এফটি করতে হবে। একই সঙ্গে নতুন বাজার, পণ্য বহুমুখীকরণ ও উৎপাদনশীলতার ওপর জোর দিতে হবে।’
হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে ঘোষিত নতুন শুল্ক আরোপ তিন মাসের জন্য স্থগিত করায় বাংলাদেশের রপ্তানি খাতে সাময়িক স্বস্তি মিললেও অনিশ্চয়তা কাটেনি। এই ৯০ দিনের মধ্যে নতুন করে এলসি খোলা হলে তার জাহাজীকরণ যদি ৯০ দিনের পরে হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে ওই রপ্তানির বিপরীতে স্থগিত কর সুবিধা প্রযোজ্য হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। যদি এই স্থগিতাদেশের ৯০ দিন পর মার্কিন শুল্ক বিভাগ পণ্য খালাসীকরণের লক্ষ্যে শুল্ক অ্যাসেসমেন্ট করে তাহলে কত শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে, তা নিশ্চিত করা না গেলে ব্যবসায়ীদের মধ্যে শঙ্কা থেকেই যাবে।
চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ১০ সুপারিশ
বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্কহারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি ১০ দফা সুপারিশ করে। এগুলো হচ্ছে এক. শুধু পোশাক খাতকেন্দ্রিক রপ্তানিনির্ভরতা না রেখে রপ্তানি পণ্যের বহুমুখিতা ও বৈচিত্র্য বাড়ানো এবং বিকল্প বাজার খুঁজে বের করা, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য কূটনীতি জোরদার করে সে দেশের বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি অব্যাহত রাখা, ৯০ দিনের স্থগিতাদেশের মেয়াদ শেষে রপ্তানি পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছালে বা জাহাজীকরণ হলে রপ্তানির বিপরীতে স্থগিতকৃত শুল্ক সুবিধা প্রযোজ্য হবে কি না তা স্পষ্ট করা অন্যতম।
ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে ‘যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্কহারের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সক্ষম হবে’ শীর্ষক ছায়া সংসদে মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বিতার্কিকদের পরাজিত করে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির বিতার্কিকরা বিজয়ী হন। প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ রইস, সুলতান আহমেদ ভূঁইয়া এফসিএ, সাংবাদিক দৌলত আক্তার মালা, ড. এস এম মোর্শেদ এবং টিভি অনুষ্ঠান নির্মাতা কে এম মাহমুদ হাসান।
ঢাবি সাদা দল
ফ্যাসিবাদের মুখোশে আগুন পরিকল্পিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) চারুকলা অনুষদে ফ্যাসিবাদের মুখাকৃতি ও শান্তির পায়রা মোটিফে আগুন দেওয়ার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন সাদা দল।
একই সঙ্গে অবিলম্বে অগ্নিকাণ্ডে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানায় সংগঠনটি।
গতকাল শনিবার ঢাবি সাদা দলের আহবায়ক অধ্যাপক মো. মোর্শেদ হাসান খান, যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক আব্দুস সালাম ও অধ্যাপক মো. আবুল কালাম সরকার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এই দাবি জানানো হয়।
বিবৃতিতে নেতারা বলেন, বাঙালি জাতির ঐতিহ্যের স্মরক পহেলা বৈশাখ।
নেতারা অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ঢাবি ক্যাম্পাসের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, পহেলা বৈশাখের আনন্দ শোভাযাত্রা পালনের লক্ষ্যে তৈরি প্রতিকৃতিসহ অন্যান্য জিনিসের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তাব্যবস্থা ছিল না। ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচার সরকারের পতনের পর চারুকলার শোভাযাত্রা নিয়ে আগে থেকেই সতর্ক থাকা অত্যাবশ্যক ছিল। অতএব পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা দরকার বলে মনে করি।
ঢাবি সাদা দলের নেতারা অবিলম্বে চারুকলায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
আদানির বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি ইউনিট ১৭ ঘণ্টা পর চালু
নিজস্ব প্রতিবেদক

ভারতের আদানি গ্রুপের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় গত শুক্রবার রাতে। এর ১৭ ঘণ্টা পর গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ১৫ মিনিটে পুনরায় একটি ইউনিট থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৪৬ মেগাওয়াট। ক্রমান্বয়ে এক ইউনিট থেকে বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়বে।
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, কেন্দ্রটির দুটি ইউনিট থেকে গড়ে এক হাজার ৪০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ পাওয়া যেত। কারিগরি ত্রুটির কারণে প্রথম ইউনিট থেকে উৎপাদন বন্ধ হয়েছে গত মঙ্গলবার। আর দ্বিতীয় ইউনিট বন্ধ হয় গত শুক্রবার রাত ১টার দিকে।
জানতে চাইলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের সদস্য (উৎপাদন) মো. জহুরুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, ত্রুটি দেখা দেওয়ায় আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুটি ইউনিট থেকেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। ঘাটতি পূরণে গ্যাস ও তেলভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন বাড়ানো হয়।
আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত কয়লার দাম নিয়ে বিরোধ আছে। এটি নিয়ে আদানি ও বিপিডিবির মধ্যে আলোচনা চলছে। বকেয়া শোধ নিয়েও বিভিন্ন সময় তাগাদা দিয়েছে আদানি।
পিজিসিবি ও বিপিডিবি সূত্র বলছে, গতকাল শনিবার ছুটির দিন থাকায় বিদ্যুতের চাহিদা অন্য দিনের চেয়ে কিছুটা কম। গতকাল বিকেল ৩টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ চাহিদা উঠেছে ১৩ হাজার ৫৫২ মেগাওয়াট। এ সময় ৪২৮ মেগাওয়াট লোডশেডিং করা হয়েছে। আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সরবরাহ শুরু না হলে আজ রবিবার লোডশেডিং আরো বৃদ্ধি পেত। ঘাটতি মেটাতে পেট্রোবাংলার কাছে বাড়তি গ্যাস সরবরাহও চেয়েছিল বিপিডিবি।
আদানির কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি এক হাজার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার। ৮০০ মেগাওয়াট সক্ষমতার দুটি ইউনিট আছে এই কেন্দ্রে। এতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২৫ বছর ধরে কিনবে বাংলাদেশ। প্রথম ইউনিট থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় ২০২৩ সালের এপ্রিলে। দ্বিতীয় ইউনিট থেকে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয় একই বছরের জুনে। ২০১৭ সালে আদানির সঙ্গে বিদ্যুৎ কেনার চুক্তি করে বিপিডিবি। আদানির সঙ্গে বিপিডিবির চুক্তি পর্যালোচনায় অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত একটি কমিটি কাজ করছে।
ইসরায়েল গাজায় এবার পানি-অস্ত্র প্রয়োগ করছে
কালের কণ্ঠ ডেস্ক

ধরার বুকে ‘নির্মিত জাহান্নাম’ হিসেবে পরিচিত গাজার মানবিক পরিস্থিতির অবনতি বিশ্বসম্প্রদায়কে ভাবতে বাধ্য করছে। দখলদার ইসরায়েলের বেপরোয়া বিমান হামলা ও ভয়াবহ স্থল হামলায় অবরুদ্ধ গাজাবাসী এখন শুধু খাবারের অভাবে ধুঁকে ধুঁকে মরছে না; অনাহারি গাজাবাসী এক ঢোক সুপেয় জলও এখন পাচ্ছে না।
গাজায় বিশুদ্ধ পানির সবচেয়ে বড় উৎসটি ছিল ইসরায়েলি একটি কম্পানির। গত শুক্রবার কম্পানিটি পানির পাইপলাইন বন্ধ করে দিয়েছে।
ইসরায়েল গত সপ্তাহেই গাজার শিজাইয়া এলাকার সব অধিবাসীকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।
মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মকর্তা বলেন, ‘গাজার পরিস্থিতি অত্যন্ত কঠিন এবং দিন দিন তা অবনতির দিকেই যাচ্ছে। পানি তো দৈনন্দিন নানা কাজে লাগে। কিন্তু পানি কোথাও মিলছে না। গাজা এখন বিশ্বের এক তৃষ্ণার্ত নগরী। আগামী দিনগুলোতে কী ঘটতে যাচ্ছে, তা আমরা কেউ জানি না।’
গাজার লোকসংখ্যা ২৩ লাখ। কিন্তু যুদ্ধের কারণে বেশির ভাগ অধিবাসী এখন বাস্তুচ্যুত। প্রত্যন্ত এলাকায় এখনো দু-একটি কূপে পানি রয়েছে। কিন্তু সেই কূপে পানির বিশুদ্ধতার কোনোই গ্যারান্টি নেই।
গত শুক্রবার রেড ক্রসের প্রেসিডেন্ট মিরজানা স্পোলজারিক বলেন, গাজার মানবিক পরিস্থিতি ‘পৃথিবীর দোজখে’ পরিণত হয়েছে। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে অস্থায়ী হাসপাতালগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হবে। কারণ এরপর গাজাবাসীর রসদ ফুরিয়ে যাবে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক সাহায্যকারী সংস্থা রেড ক্রস।
তিনি বলেন, ‘আমরা গাজায় এখন নিজেদের এমন পরিস্থিতিতে দেখছি। যেটিকে আমাকে বলতে হবে পৃথিবীর দোজখ। মানুষ বিভিন্ন জায়গায় বিদ্যুৎ, পানি, খাবার পায় না।’
গত ২ মার্চ গাজায় পূর্ণ অবরোধ আরোপ করে দখলদার ইসরায়েল। ওই সময় দখলদারদের সঙ্গে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যুদ্ধবিরতি ভেস্তে যাওয়ার শঙ্কায় পড়ে। ওই দিন থেকে গাজায় যুদ্ধবিরতির দ্বিতীয় ধাপ শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইসরাইল চুক্তি ভঙ্গ করে। এর কয়েক দিন পর ১৮ মার্চ রাতে গাজায় হঠাৎ তীব্র বিমান হামলা চালায় তারা। এতে এক রাতে চার শরও বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়।
জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এ ছাড়া অবরুদ্ধ এই ভূখণ্ডের ৬০ শতাংশ অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ভোরে গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলায় ইসরায়েলে অন্তত এক হাজার ১৩৯ জন নিহত হয় এবং দুই শর বেশি মানুষকে বন্দি করে গাজায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে গাজায় ভয়াবহ হামলা শুরু করে ইসরাইলি বাহিনী। সূত্র : এএফপি, রয়টার্স



