পৃথিবীতে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ষাটের দশকের দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম নেওয়া শুরু হয়। পাঁচ দশক পর বিভিন্ন দেশ উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পাঁচ দশক পর উন্নয়নের একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোট্ট ভূখণ্ডে বিপুল জনগোষ্ঠী নিয়ে প্রথমেই বিশাল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের জন্য একটি ‘উদাহরণ’ হয়ে উঠেছে।
আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই শতকে জনপ্রশাসন
- ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ
অন্যান্য

বাংলাদেশ এখন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক সন্ধিক্ষণে।
প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে গণমুখী জনপ্রশাসনের বৈশিষ্ট্য কী? এটা হবে প্রথমত. জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রশাসন; দ্বিতীয়ত, এটা হবে দক্ষ প্রশাসন; তৃতীয়ত, সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলাবোধ থাকতে হবে; চতুর্থতে প্রশাসককে পরার্থপরতার অনুসারী ও জনগণের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে। এই চারটি বৈশিষ্ট্য থাকতে হলে জনপ্রশাসন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হতে হবে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কর্মসম্পাদনে দক্ষ। কিন্তু শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা, যেটা আমরা বলি শুধু ‘হার্ড স্কিল’ আহরণ করা যায়; বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো আহরণ করতে হবে যেটা আমরা বলি ‘সফট স্কিল’-এর মাধ্যমে। এই সফট স্কিল ও বৈশিষ্ট্যগুলো সাধারণত মানুষ আহরণ করে আলোচনা, একের সঙ্গে আরেকজনের যোগাযোগ, দলভিত্তিক কাজ, বিভিন্ন উদাহরণ ও কেস স্টাডি ইত্যাদির মাধ্যমে; যেটা চলমান এবং সাধারণত অনেকটা অনানুষ্ঠানিক। অনেক সময় জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তার উপদেশ, অভিজ্ঞতা জানা এবং তাঁদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমেও এটা আহরণ করা যায়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখে থাকি, জনপ্রশাসন, বিশেষ করে সরকারি কর্মক্ষেত্রে ‘সফট স্কিল’-এর বিষয়ে গুরুত্ব ও আগ্রহ অপেক্ষাকৃত কম। অন্যদিকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, যা অনেকাংশে প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতিতে দেওয়া হয়; সেটারই প্রাধান্য বেশি থাকে।
উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবেই মানুষ ও সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। এর জন্য প্রয়োজন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় : ক. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো (সিস্টেম); খ. সবার অংশগ্রহণের জন্য সঠিক প্রক্রিয়া (প্রসেস); গ. সক্রিয় ব্যক্তিবর্গ অর্থাৎ প্রশাসনের ব্যক্তি, সুধীসমাজের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যক্তি খাতের ব্যক্তি। এই তিনটি বিষয় ও ওপরে উল্লিখিত চারটি বৈশিষ্ট্য মিলেই হবে ‘গণমুখী জনপ্রশাসন’।
ভূমিকা ও ওপরে আলোচিত জনপ্রশাসনের বিভিন্ন দিকের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এই শতকের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—কোনো রাষ্ট্রই একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো চলতে পারবে না। বিশ্ব অর্থনীতি, বাণিজ্য ও প্রযুক্তির প্রভাব সব রাষ্ট্রের ওপর পড়েছে। তদুপরি যোগ হয়েছে সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের তাগিদ, কাঠামোগত সংস্কার ও বাজার অর্থনীতির প্রয়োজনীয় নিয়ামকসমূহ এবং অবাধ তথ্য ও নতুন প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা। বর্তমান কভিড-১৯ মহামারির আঘাতের ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক মিলিয়ে রাষ্ট্রের সব খাতেই স্থবিরতা চলে এসেছে। জীবন ও জীবিকার সমন্বয় করে মহামারি প্রতিহত করার চেষ্টায় সবাই ব্যস্ত ও উৎকণ্ঠিত। মোটা দাগে আরো তিনটি বিষয় দক্ষ ও গণমুখী প্রশাসনে অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়েছে। সেগুলো হলো—ক. নিম্নমধ্যম আয় থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হওয়া; খ. উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য হওয়া এবং পরবর্তী পর্যায়ে উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত হওয়া; গ. টেকসই উন্নয়ন অর্থাৎ জাতিসংঘের ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস-২০৩০-এর মধ্যে অর্জন করা।
ওপরের আলোচনার মাধ্যমে এটা সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশকে বর্তমান অবস্থা থেকে আরো উন্নত পর্যায়ে নেওয়া এবং সব অনিশ্চয়তা ও দুর্বলতা কাটিয়ে ভবিষ্যতে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হলে রাষ্ট্রীয় জনপ্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই অংশে আমি অন্যান্য খাতের প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা না করে শুধু রাষ্ট্রীয় জনপ্রশাসনকে গণমুখী জনপ্রশাসন করার জন্য সাতটি পদক্ষেপ উল্লেখ করব। সেগুলো হলো—ক. প্রশাসনকে বিকেন্দ্রীকরণ : কেন্দ্র থেকে devolution, deconcentration ও delegation-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ভৌগোলিক স্তরে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন; খ. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালীকরণ। সংবিধানের বিভিন্ন ধারা অনুযায়ী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশাসন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমাজ উন্নয়ন, নাগরিক সুরক্ষাসহ মানুষের জীবনের বিভিন্ন চাহিদা পূরণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ; গ. জনপ্রশাসনকে জবাবদিহিমূলককরণ। তিনটি বিশেষ দিক প্রয়োজন—স্বচ্ছতা (transparency); বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের শুনানি (public hearing of issues and policies); ঘ. প্রশাসককে সমাজচেতনায় উদ্বুদ্ধ বিশেষ নাগরিকের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন; সর্বোপরি নীতিনির্ধারণ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত জনগণের রাজনৈতিক প্রতিনিধির সার্বিক পরামর্শে গুরুত্ব দেওয়া। তবে উল্লেখ্য, জনপ্রশাসনের সব ব্যক্তিকেই রাজনৈতিক দলের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে; ঙ. জনপ্রশাসনের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি; দক্ষ প্রশাসকের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি করলে জনসাধারণ সহজেই বিভিন্ন সেবা পাবে; চ. জনপ্রশাসনের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবাধ তথ্য প্রদান। প্রশাসন সম্পর্কে গোপনীয়তা কমিয়ে এনে জনগণকে নিয়মিত ও সঠিক তথ্য অবহিত করতে হবে; ছ. নিয়মনীতির প্রাধান্য থাকবে, আমলাদের বিশেষ ক্ষমতা (discretionary power)-এর ব্যবহার যেন খুব কম হয়। এতে প্রশাসনে দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা অনেক হ্রাস পাবে।
এই নিবন্ধে বর্তমান উদ্ভূত মৌলিক বিষয়ের ওপর ধারণা দেওয়া হয়েছে, যেটা জনপ্রশাসনকে বাংলাদেশের সম্মুখপানে যাত্রা দ্রুততর করবে এবং বাংলাদেশকে একটি সত্যিকার কল্যাণমুখী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।
লেখক : সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত খবর
ষষ্ঠ বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন ও ইউনূস-মোদি বৈঠক
- ড. সুজিত কুমার দত্ত

গত ৩ ও ৪ এপ্রিল ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বিমসটেক (বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন) শীর্ষ সম্মেলন দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, নেপাল, ভুটান ও শ্রীলঙ্কার নেতারা অংশগ্রহণ করেন। বিশেষ করে সম্মেলনের পার্শ্বক্রমে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যকার বৈঠক আঞ্চলিক কূটনীতিতে নতুন সমীকরণ সৃষ্টি করেছে। সম্মেলনে সদস্য দেশগুলো বাণিজ্য ও পরিবহন সহযোগিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমন্বিত প্রচেষ্টার ওপর জোর দেয়।
ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে অনুষ্ঠিত আধাঘণ্টার দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি আঞ্চলিক কূটনীতির প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই বৈঠকটি এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হলো, যখন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক বেশ টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক যোগাযোগ অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়েছিল।
এই পরিস্থিতিতে ইউনূস-মোদি বৈঠকটি নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে এবং আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। বৈঠকের পর বাংলাদেশের প্রেস সচিবের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দুই সরকারপ্রধানের মধ্যে পারস্পারিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ। এ ছাড়া সীমান্ত হত্যা, তিস্তা নদীর পানিবণ্টনসহ অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় ইস্যু নিয়েও আলোচনা হয়েছে। প্রেস সচিবের মতে, বৈঠকটি অত্যন্ত গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ ছিল এবং দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।
 ইউনূস-মোদি বৈঠকের ফলাফল এবং এর প্রভাব আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর এই বৈঠকের প্রভাব পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বৈঠকে হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিষয়টি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অত্যন্ত সংবেদনশীল। সীমান্ত হত্যা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় সীমান্ত হত্যা বন্ধে এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে এই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। তিস্তা নদীর পানিবণ্টন দুই দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় সমস্যা সমাধানে নতুন করে আলোচনার পথ খুলেছে। তবে এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সমাধান না হলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে।
ইউনূস-মোদি বৈঠকের ফলাফল এবং এর প্রভাব আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর এই বৈঠকের প্রভাব পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বৈঠকে হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই বিষয়টি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অত্যন্ত সংবেদনশীল। সীমান্ত হত্যা ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি দুই দেশের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় সীমান্ত হত্যা বন্ধে এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে এই বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। তিস্তা নদীর পানিবণ্টন দুই দেশের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। বৈঠকে এই বিষয়ে আলোচনা হওয়ায় সমস্যা সমাধানে নতুন করে আলোচনার পথ খুলেছে। তবে এই বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সমাধান না হলে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে পারে।
বিমসটেক আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ ফোরাম। এই শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ইউনূস-মোদি বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ায় এই ফোরামের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিমসটেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনূস-মোদি বৈঠকের ফলাফল এবং এর প্রভাব আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলতে পারে। এই বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে পুনরায় কূটনৈতিক যোগাযোগের পথ খুলেছে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নতুন করে আলোচনার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে এই আলোচনার ফলাফল নির্ভর করবে দুই দেশের সরকারপ্রধানদের সদিচ্ছার ওপর। আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নের স্বার্থে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।
বিমসটেক সদস্য দেশগুলো বাণিজ্য, পরিবহন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশের চেয়ারম্যানশিপে এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়নে নতুন গতি আসবে বলে আশা করা যায়। তবে মায়ানমারের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও অন্যান্য দ্বিপক্ষীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাও জরুরি। ড. ইউনূস ও নরেন্দ্র মোদির বৈঠক দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। মায়ানমারের ভূমিকম্প ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে বিমসটেক সদস্য দেশগুলো উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে।
লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
datta.ir@cu.ac.bd
ড. ইউনূসের আরো স্থায়িত্বের প্রশ্নে কিছু কথা
- গাজীউল হাসান খান
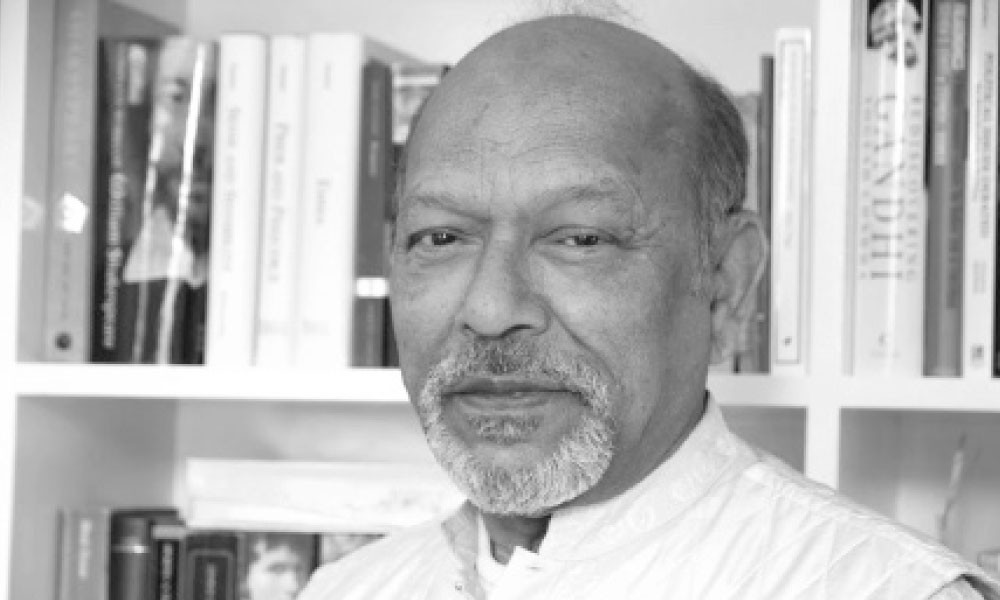
আজকাল কোনো রাজনৈতিক কথা বলা কিংবা লেখার ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সংকট দেখা দিয়েছে বলে মনে হয়। কোনো ব্যাপারে বক্তা কিংবা লেখকের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই একটি পক্ষ নির্ধারণের প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ বক্তা বা লেখক রাজনীতিগতভাবে কোন পক্ষের লোক, সেটি নির্ধারণের একটি প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এটি আমাদের পারস্পরিক সমঝোতা কিংবা বৃহত্তরভাবে বোঝাপড়ার অভাবেও হতে পারে।
আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দেড় দশক ধরে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছে, তাদের মধ্যে বর্তমানে একটি সুস্পষ্ট মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এই মতবিরোধ দেশের কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র মেরামত বা প্রয়োজনীয় সংস্কারকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মূল লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে আগামী জাতীয় নির্বাচন। দুই দিন আগে হোক আর পরেই হোক, গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে দেশ পরিচালনার জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কোনো বিকল্প পথ নেই।
নির্বাচিত প্রতিনিধিরা ক্ষমতায় এসে যদি সব কিছু অর্থাৎ গণবিরোধী সব আইনকানুন বদলে ফেলতে পারতেন, তাহলে বিগত বছরগুলোতে এ দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন, দুর্নীতি এবং সম্পদ পাচারসহ একটি জাতি বিধ্বংসকারী অবস্থার সৃষ্টি হতো না।
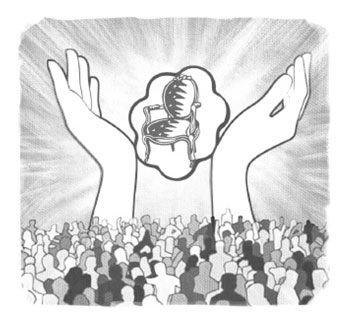 অর্থ-বিত্ত কিংবা সম্পদের মালিকরাই রাজনীতি করবেন, আর কেউ নয়—সেটি আর চলতে দেওয়া যেতে পারে না। আজ যাঁরা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রয়েছেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং একটি বৃহত্তর সমঝোতার মাধ্যমে দেশের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব কিংবা সংঘাত কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। সে জন্য বিভিন্ন সংকট নিরসনে এখনই বিভিন্ন দল ও নেতার মধ্যে ঘন ঘন অন্তর্দলীয় আলোচনা শুরু করতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে একটি সর্বদলীয় ঐক্য ও সমঝোতা। ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি একটি ন্যূনতম ঐক্য, সমঝোতা ও সংহতি গড়ে না ওঠে, তাহলে বৈদেশিক শক্তি, যারা আমাদের পদানত করে শোষণ করতে চায়, তারা আবার অবাধে আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইন্ধন জোগাতেই থাকবে। সে কারণেই দেশের অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচন নিয়ে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তা না করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান চলমান বিভেদ ও অনৈক্যকে আরো ব্যাপক এবং আত্মঘাতী করে তুলবে। এ দেশে রাজনীতি করতে হলে সবাইকে নিয়েই করতে হবে। কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। সুতরাং সে জাতি গঠনমূলক এবং জাতীয় স্বার্থের রাজনীতিতে সবাইকে ‘একদলীয় রাজনীতির মনোভাব’ দূর করতে হবে।
অর্থ-বিত্ত কিংবা সম্পদের মালিকরাই রাজনীতি করবেন, আর কেউ নয়—সেটি আর চলতে দেওয়া যেতে পারে না। আজ যাঁরা দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে রয়েছেন, দেশের বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং একটি বৃহত্তর সমঝোতার মাধ্যমে দেশের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। মতবিরোধ, দ্বন্দ্ব কিংবা সংঘাত কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। সে জন্য বিভিন্ন সংকট নিরসনে এখনই বিভিন্ন দল ও নেতার মধ্যে ঘন ঘন অন্তর্দলীয় আলোচনা শুরু করতে হবে এবং গড়ে তুলতে হবে একটি সর্বদলীয় ঐক্য ও সমঝোতা। ফ্যাসিবাদ-পরবর্তী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যদি একটি ন্যূনতম ঐক্য, সমঝোতা ও সংহতি গড়ে না ওঠে, তাহলে বৈদেশিক শক্তি, যারা আমাদের পদানত করে শোষণ করতে চায়, তারা আবার অবাধে আমাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ইন্ধন জোগাতেই থাকবে। সে কারণেই দেশের অত্যাবশ্যকীয় সংস্কার এবং ভবিষ্যৎ নির্বাচন নিয়ে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বৃহত্তর ঐক্য ও সমঝোতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। তা না করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদান চলমান বিভেদ ও অনৈক্যকে আরো ব্যাপক এবং আত্মঘাতী করে তুলবে। এ দেশে রাজনীতি করতে হলে সবাইকে নিয়েই করতে হবে। কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না। সুতরাং সে জাতি গঠনমূলক এবং জাতীয় স্বার্থের রাজনীতিতে সবাইকে ‘একদলীয় রাজনীতির মনোভাব’ দূর করতে হবে।
ওপরে উল্লিখিত বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোকে স্বদেশ থেকে পাঁচ হাজার মাইল দূরে অবস্থানরত বিএনপি নেতা তারেক রহমান বহুদিন ধরে অনেক গঠনমূলক কথাবার্তা বলেছেন। অনেকে সেগুলোকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখেছে আবার কেউ কেউ বিভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থ বা নেতৃত্বের টোপ হিসেবেও উল্লেখ করেছে। কিন্তু এই বিষয়টিকে গঠনমূলকভাবে জাতীয় স্বার্থের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করাই অত্যন্ত সমীচীন হবে বলে আমি মনে করি। আমি একজন সাংবাদিক, লেখক ও কলামিস্ট। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমি আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে একটি কথাই বলতে চাই—সব দল একসঙ্গে ক্ষমতায় যায় না। তবে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে দেশের ছোট-বড় সব দল একসঙ্গে কাজ করতে পারে। তাহলেই রাজনীতির ক্ষেত্রে সাফল্য আসে। দেশ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যায়। ফিরে আসি তারেক রহমানের সাম্প্রতিক বক্তব্যে। তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলেছেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তিনি একটি সর্বদলীয় সরকার (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য) গঠন করতে চান, যাতে শুরুতেই জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থ বিনষ্ট না হয়। উপরন্তু আগামী নির্বাচনে তারেক রহমান নবগঠিত নাগরিক পার্টির সঙ্গে একটি জোট গঠনেরও বাসনা প্রকাশ করেছেন।
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক রাজনৈতিক প্রস্তাব আসা শুরু হয়েছে। এতে বিরোধিতা থাকবে না এমন নয়। জাতীয় স্বার্থে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ কিংবা কর্মসূচির গঠনমূলক সমালোচনা থাকতেই পারে। কেউ না কেউ সরকারি পদক্ষেপ বা কর্মসূচির বিকল্প লাভজনক পথও দেখাতে পারে। এতে জাতীয় স্বার্থে ঐক্য, সংহতি কিংবা সমঝোতা বিনষ্ট হবে না। তা ছাড়া নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির কয়েকজন নেতা নির্বাচনের পর দেশে রাজনীতির কিংবা রাষ্ট্রব্যবস্থার এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে সফল উত্তরণের জন্য অর্থাৎ মধ্যবর্তী সময়ের জন্য একটি ‘ট্রানজিশনাল সরকার’ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন। গভীরে তলিয়ে দেখতে গেলে সে প্রস্তাব তারেক রহমানের প্রস্তাব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ আছে বলে মনে হয় না। মতবিরোধ যা-ই আছে, তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি সমঝোতায় পৌঁছা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিষ্ঠার সূচনায় রাষ্ট্র মেরামতের প্রশ্নে তারেক রহমান তাঁর একটি সংস্কার প্রস্তাব সংবলিত ৩১ দফা ঘোষণা করেছিলেন, যার মধ্যে বিবেচনা করার মতো যথেষ্ট বিষয়বস্তু রয়েছে। সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। যত দিন কোনো জাতি বা রাষ্ট্র থাকবে, তত দিনই এই প্রক্রিয়া চলমান থাকবে। তবে কথা হচ্ছে, অগণতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী শাসনের ফলে বর্তমানে রাষ্ট্র মেরামত বা জরুরি সংস্কারের যে বিষয়গুলো রয়েছে, সেগুলোকে তো অগ্রাধিকার দিয়ে বিবেচনা করতেই হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। এটি বিবেচনা করার সময় যাঁদের হাতে নেই, তাঁরা দীর্ঘ ১৮ বছর কোথায় ছিলেন?
দেশের আপামর জনগণ রাষ্ট্রক্ষমতায় যোগ্য নেতৃত্বের অবস্থান কামনা করে। সে কারণেই অনেকে মনে করে, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধ্যাপক ইউনূসের আরো কিছুটা সময় থাকা আবশ্যক। তাহলে দেশ ও জাতি একটি কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। এটি কোনো অযৌক্তিক দাবি বা আকাঙ্ক্ষা নয়। কারণ ড. ইউনূস আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তি, যাঁর প্রতি দেশের জনগণ এবং প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক মহলের আস্থা রয়েছে। অন্যরা এই মুহূর্তে ক্ষমতায় আসীন হলে পতিত ফ্যাসিবাদীদের দোসর এবং আধিপত্যবাদী আন্তর্জাতিক মহলের চাপ নেওয়ার মতো শক্তি দেখাতে সক্ষম না-ও হতে পারে। এই কথাটি কি সার্বিকভাবে অস্বীকার করা যায়? যায় না। সুতরাং যাঁরা ড. ইউসূসের প্রতি আস্থা দেখাচ্ছেন, তাঁদের অপরাধটা কী? একাত্তর-পরবর্তী দেশীয় রাজনীতিতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া ছাড়া কেউ তো তেমনভাবে কোনো আশার আলো দেখাতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে বিএনপির কেউ কেউ যদি মনে করেন, তাঁরা অনেকেই শহীদ জিয়া কিংবা খালেদা জিয়ার মতো পরীক্ষিত নেতা হয়ে গেছেন, তাহলে সেটি হবে একটি দিবাস্বপ্নের মতো। তাঁদের প্রতি জনগণের তেমন আস্থা থাকলে তো বহু আগেই শেখ হাসিনার পতন ঘটত। সুতরাং সমালোচকের মুখে কথা তুলে না দিয়ে বাস্তববাদী হওয়া অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। এ ক্ষেত্রে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে দিব্যদৃষ্টি ও বাস্তববাদিতা। একটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল টিমকে মাঠে নামিয়ে খেলায় হেরে যাওয়ার চেয়ে বাছাইকৃত শক্তিশালী একটি টিমকে মাঠে নামিয়ে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেওয়াই প্রকৃত ক্রীড়ামোদীদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এ ক্ষেত্রে দেশপ্রেমিক জনগণের লক্ষ্যও একটিই। বাংলাদেশকে জেতাতে হবে। সব ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন করতে হবে। শত্রুর সব অপকৌশল ঠেকাতে হবে। দেশের অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করতে হবে। বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির গতি বেগবান করতে হবে। তরুণদের দিয়ে সেটি সম্ভব। জরাগ্রস্ত বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের দিয়ে সেটি কতটুকু অর্জিত হতে পারে? এ কথা দেশপ্রেমিক জনগণ যতটা ভাবে, ক্ষমতালোভী দলীয় নেতাদের অনেকে মনকে সেটি বোঝাতে পারেন না।
এসব কারণে তরুণ নেতা তারেক রহমান চান জাতীয় ভিত্তিতে একটি বৃহত্তর ঐক্য, যা তাঁকে এবং দেশের তরুণ নেতৃত্বকে একটি বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করবে। লুকোছাপার কিছু নেই। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অনেকেই চায় অতি প্রয়োজনীয় বা আবশ্যকীয় সংস্কারগুলো সম্পন্ন করে অধ্যাপক ইউনূসের উল্লিখিত সময়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দেওয়া হোক। তা থেকে বাছাইকৃত তরুণ নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে (দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা কিংবা প্রাপ্ত ভোটের হিসাবে) একটি মধ্যবর্তী কিংবা Transitional Governmentগঠন করা হোক, যার নেতৃত্বে থাকবেন ড. ইউনূস। তাঁকে যেকোনো একটি আসন খালি করে পাস করিয়ে আনা সম্ভব হবে। তা ছাড়া সেই সরকারের নেতৃত্বে দ্বিতীয় অবস্থানে থাকবেন তরুণ নেতা তারেক রহমান। তাঁকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করবেন তরুণ নেতারা, যাঁদের দিনে দিনে যোগ্য রাজনীতিক ও নেতা হিসেবে গড়ে (প্রশিক্ষিত) তোলা যাবে। জামায়াতে ইসলামী কিংবা অন্যদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে বিরোধী দলের আসন অলংকৃত করতেও বাধা থাকবে না। দেশের বৃহত্তর বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবী মহলের একটি বিশাল অংশের ভবিষ্যৎ নির্বাচন ও সরকার গঠন নিয়ে চিন্তা-চেতনা এমনই। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষককুল কিংবা শহর-নগরে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষের ধ্যান-ধারণাও এখন এভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে। এগুলো আমার কোনো ব্যক্তিগত অভিলাষ নয়।
লেখক, সাংবাদিক কিংবা বিশেষ করে কলাম লেখকরা যা শোনেন, যা দেখেন, সেটি নিয়েই লিখে থাকেন। এতে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। এর পেছনে দেশপ্রেম বা দেশের বৃহত্তর স্বার্থ ছাড়া আর যা-ই থাক, কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র নেই। দেশের সাধারণ মানুষ অনেক কিছুই রাজনীতিকদের চেয়ে আগে ভেবে থাকে। তারা দেশের স্বার্থ, উন্নতি ও সমৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই চায় না। অন্যদিকে দেশের চিন্তাশীল মানুষ ও বুদ্ধিজীবীরা চান দেশের আর্থ-রাজনৈতিক সমৃদ্ধি ও মুক্তি। আধিপত্য কিংবা সম্প্রসারণবাদীদের প্রভাব কিংবা নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি দেশ, যেখানে থাকবে মানুষের গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার। এবং ঘটবে অর্থনৈতিক মুক্তি কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষ ও ছাত্র-জনতার।
লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
gaziulhkhan@gmail.com
নির্বাচন নিয়ে ধোঁয়াশা কাটছে না
- ড. নিয়াজ আহম্মেদ

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, গ্রহণযোগ্য এবং সর্বোপরি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সরকার গঠিত হয়, তাকেই আমরা গণতান্ত্রিক সরকার বলি। স্বাভাবিকভাবে দেশ পরিচালিত হয় নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্য দিয়ে সরকার গঠিত হয়ে। কিন্তু আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে আমরা মাঝেমধ্যে ব্যতিক্রম লক্ষ করি।
আমাদের অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এই বছরের ডিসেম্বর কিংবা আগামী বছরের প্রথমার্ধে নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে।
সম্প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন, রাজনৈতিক দলগুলো সংস্কারের ‘একটি সংক্ষিপ্ত প্যাকেজ’-এ সম্মত হলে ডিসেম্বরে নির্বাচন হতে পারে। তবে দলগুলো সংস্কারের ‘একটি বৃহত্তর প্যাকেজ’-এ সম্মত হলে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। সম্প্রতি জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক ইফতার মাহফিলে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘নির্বাচন যত দেরি হবে, তত বেশি বাংলাদেশের পক্ষের শক্তিকে পরাজিত করতে ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথাচাড়া দিতে শুরু করবে। একই সঙ্গে জঙ্গি ও উগ্র মনোভাব পোষণকারীরাও এই সুযোগগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবে।’ আরেক ইফতার মাহফিলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে বলেছেন, ‘নির্বাচনের জন্য যতটুকু সংস্কার দরকার, ততটুকু করে নির্বাচন দিন। নির্বাচনী সংস্কার করুন। বাকি সংস্কার নির্বাচিত সরকার করবে।’
আমাদের সামনে এখন তিনটি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। একটি সুন্দর আগামীর জন্য রাষ্ট্র সংস্কার, যা না হলে আমরা আগের মতোই রয়ে যাব বলে আমাদের ধারণা। একটি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং জাতিসংঘের বক্তব্য অনুযায়ী একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন নিয়ে কথা হচ্ছে। সংস্কারে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি। এরই মধ্যে সংস্কার কমিশনগুলো তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করছে। আশা করি, আরো গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে আমরা সংস্কার বিষয়ে এক জায়গায় আসতে পারব। এখন দরকার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা, তাদের মতামত এবং অঙ্গীকার গ্রহণ।
নির্বাচনের জন্য কমিশন প্রস্তুত। কাজেই সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচন সম্পর্কে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। সবাই এক হলে ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোনো বাধা থাকতে পারে না। আর অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন আদৌ সম্ভব কি না, তা-ও আলোচনার বিষয়। আমরা যদি এই কাজগুলো না করতে পারি, তাহলে নির্বাচন নিয়ে আমাদের ধোঁয়াশা কাটবে না। আমাদের খুব বেশি সময় নেই। সংস্কার একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। ফ্যাসিবাদের বিচারও একটি প্রক্রিয়া, যেখানে বেশ সময় লাগবে। আমরা যদি এই দুটি বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করি, তাহলে কোনোভাবেই ডিসেম্বরে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। আমাদের এখন উচিত সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা এবং একটি ঐকমত্যে পৌঁছা। আমাদের মনে রাখতে হবে, গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে হলে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতন্ত্র সুসংগঠিত হয়, যদি না কেউ নির্বাচনে জিতে অগণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে। আমরা চাই, একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দ্রুত গণতন্ত্র ফিরে আসুক।
লেখক : অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
nahmed1973@gmail.com
কৃষি খাতের পুনর্মূল্যায়ন ও কৃষি কমিশন গঠন প্রসঙ্গে
- ড. জাহাঙ্গীর আলম

বাংলাদেশের কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির বড় সমস্যা কৃষিজমির সীমাবদ্ধতা। বর্তমানে জনপ্রতি কৃষিজমির প্রাপ্যতা ০.১১ একর। মোট কৃষি খামারের সংখ্যা ১,৬৮,৮১,৭৫৭। নিচের ৯১.৭০ শতাংশ কৃষক প্রান্তিক ও ছোট।
কৃষিপণ্যের বাজারব্যবস্থা এখন কৃষকদের অনুকূলে নয়। এর নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে বড় ব্যবসায়ী, মিলার ও তাঁদের দ্বারা সংগঠিত সিন্ডিকেটের হাতে। বাজারে কৃষিপণ্যের মূল্য তাঁরাই নির্ধারণ করেন। এতে উৎপাদনকারী কৃষক ও ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত হন। বাজারে খামার প্রান্তের ক্রয়মূল্য ও ভোক্তা পর্যায়ে পণ্যের বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য বেশি। এর পুরো সুবিধা নিচ্ছেন মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীরা। তাঁরা শস্যের প্রক্রিয়াজাত করেন, মূল্য সংযোজন করেন এবং বাজারে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে মুনাফা হাতিয়ে নেন। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে উৎপাদনকারীরা চালের ভোক্তা-মূল্যের ৭১ শতাংশ থেকে বঞ্চিত হন। এ ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। কারণ খাদ্যশস্য মজুদের ক্ষেত্রে সরকারের সক্ষমতা কম। ব্যবসায়ী ও মিলারদের সক্ষমতা অনেক বেশি। বর্তমানে সরকারের খাদ্যশস্য মজুদের সক্ষমতা মাত্র ২২ লাখ টন। অন্যদিকে ব্যবসায়ী ও ছোট-বড় মিলারদের মজুদ সক্ষমতা প্রায় এক কোটি টন। শুধু ধান-চালের ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও কৃষকরা পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এবার আলু ও সবজির মূল্য ধসে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন উৎপাদনকারী কৃষকরা। জমি চাষ, শ্রমিকের মজুরি, বীজ, সার, কীটনাশক ও সেচের খরচ উচ্চহারে পরিশোধ করে তাঁরা অনেকটা নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। কৃষিকাজে বড় দাগে লোকসান দিয়ে তাঁদের অনেকেই এবার পথে বসেছেন।
 বাংলাদেশকে আমরা প্রায়ই খাদ্যে স্বনির্ভর বলে দাবি করি। কথাটি তেমন অর্থবহ নয়। কারণ প্রতিবছরই আমরা বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য আমদানি করছি। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ প্রায় ৭০ থেকে ৮০ লাখ টন। তেল, ডাল, পেঁয়াজ ও অন্যান্য মসলার ক্ষেত্রেও আমাদের বড় নির্ভরতা আমদানির ওপর। প্রতিবছর গড়ে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য আমাদের আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারের আকার প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার।
বাংলাদেশকে আমরা প্রায়ই খাদ্যে স্বনির্ভর বলে দাবি করি। কথাটি তেমন অর্থবহ নয়। কারণ প্রতিবছরই আমরা বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য কৃষিপণ্য আমদানি করছি। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ প্রায় ৭০ থেকে ৮০ লাখ টন। তেল, ডাল, পেঁয়াজ ও অন্যান্য মসলার ক্ষেত্রেও আমাদের বড় নির্ভরতা আমদানির ওপর। প্রতিবছর গড়ে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলারের কৃষিপণ্য আমাদের আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের বাজারের আকার প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার।
বর্তমান বিশ্বে কৃষি খাত খুবই ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে কয়েক বছর ধরে যুদ্ধবিগ্রহ, প্রথমে ইউক্রেন-রাশিয়া, পরে গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন। এসব কারণে সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে, উৎপাদন কমে গেছে। তেলের দাম বেড়েছে। মূল্যস্ফীতি বেড়েছে। এর আগে আবার করোনাকালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল। ওই সময় সরবরাহে বিঘ্ন ঘটেছে, পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের কারণেও খাদ্য পরিবহন ও বিতরণ বিঘ্নিত হয়েছে। এসব কারণে আন্তর্জাতিকভাবে খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছে। গত দুই বছরে বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়েছে। বিশেষ করে ২০২৩ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৪৮ ডিগ্রি এবং ২০২৪ সালে ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস অতিক্রম করেছে। অর্থাৎ শিল্পোন্নয়ন প্রাক্কালের চেয়ে দ্রুত বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়েছে। এই বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও খরার কারণে ধান ও গমের উৎপাদনসহ পুরো কৃষির উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তা ছাড়া অতি বৃষ্টি ও বন্যার কারণেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উৎপাদন। উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধি কমে যাচ্ছে। এই বৈশ্বিক পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। ২০২৪ সালের শুরুতে ছিল খরা, পরে হয়েছে বন্যা। কোথাও কোথাও হয়েছে অতি বৃষ্টি ও বন্যা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি। তারপর আঘাত হেনেছে ঘূর্ণিঝড় রিমাল। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ একসঙ্গে আঘাত করায় খাদ্য উৎপাদন কমেছে। এই অবস্থায় দরকার ছিল প্রচুর খাদ্য আমদানির, কিন্তু ডলার সংকটের কারণে প্রয়োজনীয় আমদানি সম্ভব হয়নি। ফলে চালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বেড়ে গেছে।
বৈশ্বিক অস্থির পরিস্থিতি, বাংলাদেশের আর্থিক সংকট ও উচ্চ মূল্যস্ফীতির ক্ষেত্রে কৃষিপণ্যের উৎপাদন বাড়ানো ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা ছাড়া কোনোভাবেই খাদ্য মূল্যস্ফীতি দমানো যাবে না। কৃষির উৎপাদন অনেক দিক থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এগুলোর একটি প্রকৃত মূল্যায়ন হওয়া দরকার। দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। তাদের কাজে সহায়তার জন্য কৃষি খাতের পুরো পরিস্থিতির একটি রিভিউ করা দরকার। আমরা কৃষি খাতে কোথায় আছি, তার মূল্যায়ন দরকার। এর জন্য দরকার কৃষি কমিশন। ওই কমিশন বর্তমান কৃষি ব্যবস্থার একটি বিস্তারিত রিভিউ উপস্থাপন করবে এবং বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের গভীর বিশ্লেষণ করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পদক্ষেপ গ্রহণে সুপারিশ করবে।
উৎপাদনের সবচেয়ে বড় খাত হচ্ছে কৃষি খাত। আসলে উৎপাদনশীল খাত বলতে প্রধানত কৃষিকেই বোঝায়। সুদূর অতীতেও কৃষিকেই উৎপাদনশীল খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। অন্যান্য খাত তথা শিল্প, সেবা, কলকারখানা—এগুলো সহযোগী খাত। শিল্পের কাঁচামাল কৃষি থেকেই আসে। এর ওপরই নির্ভর করে আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা। অতীতের মতো বিদেশের ওপর নির্ভরশীল থেকে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা যে নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না, তা এখন অবধারিত। তাই কৃষি খাতের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বর্তমানে কৃষির উৎপাদনে অনেকটা স্থবিরতা লক্ষ করা যাচ্ছে। এর আগে সত্তর ও আশির দশকের গোড়ার দিকে কৃষি খাতে ছোট করে মূল্যায়ন হয়েছিল। পরে ১৯৮৮-৮৯ সালে জাতিসংঘের সহায়তায় বিস্তারিতভাবে কৃষি খাতের রিভিউ করে দুই ভলিউমে তা বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছিল। সেখানে ক্রপস, লাইভস্টক, ফিশারিজ, ফরেস্ট্রি এবং মেকানাইজেশনসহ সব উপখাতের ওপর আলোকপাত করা হয়েছিল। কৃষিকে সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে গভীর বিশ্লেষণ করা হয়েছিল এবং সুপারিশ পেশ করা হয়েছিল। নব্বইয়ের দশকে অধ্যাপক রেহমান সোবহান পরিকল্পনা কমিশনের উপদেষ্টা থাকাকালে বিভিন্ন টাস্কফোর্স গঠন করেছিলেন। সেগুলো প্রকাশনী সংস্থা ইউপিএল থেকে চারটি ভলিউমে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে একটি বিষয় ছিল কৃষি। নব্বইয়ের পর প্রায় ৩৪ বছর ধরে কৃষি খাতে রিভিউ করা হয়নি। এখানে একটি গভীর বিশ্লেষণ প্রয়োজন।
কৃষি খাতে বর্তমান সমস্যাগুলো কী, তা আমরা মোটামুটিভাবে জানি। একটা সময় ছিল, যখন আমরা শস্য খাতের ওপর বেশি নির্ভরশীল ছিলাম। মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির প্রায় ৮০ শতাংশই ক্রপস সেক্টর থেকে আসত। কালক্রমে আমরা তা থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছি। বর্তমানে ক্রপস সেক্টর থেকে আসছে ৫০ শতাংশ এবং বাকি ৫০ শতাংশ আসছে লাইভস্টক, ফিশারিজ ও ফরেস্ট্রি সেক্টর থেকে। তবে পরিবর্তনের গতিটা খুবই কম। আমরা ধানের ওপর যতটা গুরুত্ব দিয়েছি, অন্যান্য শস্যের ওপর ততটা দিচ্ছি না। ধান উৎপাদনের জন্য ৭২ শতাংশ জমি ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন ধান উৎপাদনে মোটামুটিভাবে আমরা স্বয়ম্ভরতা অর্জন করেছি। যখন ভালো উৎপাদন হয়, তখন আমদানি করতে হয় না। তা ছাড়া অন্যান্য শস্যের ক্ষেত্রেও প্রচুর আমদানি করতে হয়। মসলাজাতীয় ফসল, ডাল, তেল ইত্যাদি আমদানি করতে হয় অনেক। তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। গ্রহণ করতে হবে আমদানি প্রতিস্থাপন নীতি।
দেশে কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে। ১৯৮৪ সালে বিস্তারিতভাবে দেশে কৃষি শুমারির আয়োজন করা হয়েছিল। সর্বশেষ ২০১৮-১৯ সালের কৃষি শুমারির হিসাব মতে, কৃষি খাতে গত ৩৫ বছরে জমির পরিমাণ বার্ষিক গড়ে ০.৫৮ শতাংশ হারে কমেছে। এই হারে যখন জমি কমছে, তখন আমরা কী করতে পারি? দেশে আইন রয়েছে—দুইফসলি ও তিনফসলি জমি কৃষি ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এটি কেউ মানছে না। আমাদের রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্যাটার্ন ও হাউজিং প্যাটার্নে কিভাবে পরিবর্তন আনা যায়, যাতে কৃষিজমি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা ভাবা দরকার। আমাদের বছরে জনপ্রতি প্রায় ৮২ কেজি খাদ্য অপচয় হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া এবং ভারতের চেয়েও এখানে খাদ্য অপচয় বেশি। এর কারণ হচ্ছে প্রসেসিং ও গ্রেডিং, পরিবহন ও সংরক্ষণে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি।
আমাদের দেশে প্রচুর কৃষি শ্রমিক আছে, কিন্তু অভাব রয়েছে উৎপাদনের আধুনিক উপকরণের। একসময় ভাবা হতো, দেশে প্রচুর গ্যাস আছে, তাই সার উৎপাদন সম্ভব। কয়েকটি কারখানাও স্থাপন করা হয়েছিল। ইউরিয়ার উৎপাদন ছিল আশাব্যঞ্জক। প্রয়োজনের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ ইউরিয়া দেশে উৎপাদন করা হতো। কালক্রমে সেই উৎপাদন কমে গিয়ে আমদানিনির্ভরতা বেড়েছে। এখন বছরে যা প্রয়োজন তার মাত্র ২০ শতাংশ উৎপাদিত হয়, বাকিটা আমদানি। বিভিন্ন কারণে আন্তর্জাতিক বাজারে সার তেমন সহজলভ্য নয়। তাই বিদেশের ওপর নির্ভর করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবেই হোক সারের উৎপাদন বাড়াতে হবে। বন্ধ থাকা কারখানাগুলো চালু করতে হবে। অন্যান্য কৃষি উপকরণেও নিজেদের আত্মনির্ভরশীল হওয়া দরকার। বছরে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টন কীটনাশক আমাদের আমদানি করতে হয়। আমরা জানি কীটনাশক তৈরিতে কী কী উপকরণ দরকার। তাই প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানি করে দেশেই কীটনাশক উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে ব্যবহৃত সেচযন্ত্রের প্রায় এক-চতুর্থাংশ বিকল। এগুলোর ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ বিদ্যুত্চালিত, বাকি সব ডিজেলচালিত। বর্তমানে বিদ্যুৎ ও ডিজেলের দাম বেড়েছে, তাতে বেড়েছে উৎপাদন খরচ। এ ক্ষেত্রে সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার খুবই সাশ্রয়ী হতে পারত। এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা দরকার।
অনেক দেশের তুলনায় কৃষি খাতে বাংলাদেশে ভর্তুকি কম। বহু বছর ধরে আমরা কৃষি খাতে ভর্তুকি দিয়ে আসছি, এখনো দিচ্ছি। আমাদের ৯২ শতাংশ কৃষক হচ্ছেন ক্ষুদ্র। তাঁরা প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করতে পারেন না। চীনে প্রত্যেক কৃষককে ভর্তুকি দেওয়া হয় ১৫৯ ডলার এবং বাংলাদেশে ৭.৮ ডলার মাত্র, এটি খুবই কম। কৃষি খাতে অর্থায়ন বড় সমস্যা। এ জন্য গরিব কৃষকদের জন্য অর্থের জোগান দেওয়া দরকার। সাম্প্রতিক সময়ে কৃষিঋণ গড়ে ৭-৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। ১৫ থেকে ২০ বছর ধরে কৃষিঋণ বাড়লেও দেশের কৃষকদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি এখনো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাচ্ছে না। মূল টাকাটা ধনিক শ্রেণির মানুষ নিয়ে যাচ্ছে। এসব সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। এ জন্য কৃষি খাতে গভীর বিশ্লেষণ দরকার।
কৃষি উৎপাদনের সরকারি পরিসংখ্যান খুব কম নির্ভরশীল। খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে মাছ-মাংস খাওয়ার যে পরিসংখ্যান আমরা পাচ্ছি, তা অনেক ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ নয়। আলু, পেঁয়াজ, ডিম, দুধ ও মাংসের ক্ষেত্রে উৎপাদনের যে হিসাব দেওয়া হয়, বাস্তবতার সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায় না। তা ছাড়া বিভিন্ন পণ্যের ভোগ চাহিদার ক্ষেত্রেও সঠিক পরিসংখ্যানের অভাব। আমাদের উৎপাদন ও ভোগের পরিসংখ্যান প্রদানের ক্ষেত্রে যে নিয়ম অনুসরণ করা হয় তার চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সঠিক পরিসংখ্যানের জন্য দরকার পদ্ধতিগত সংস্কার।
কৃষি খাতে উৎপাদনের স্থবিরতা এবং বড় ধরনের আমদানিনির্ভরতা আমাদের শঙ্কার কারণ। এর সঙ্গে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়া এবং কৃষিকাজে তাঁদের উৎসাহ হারানো খুবই উদ্বেগের বিষয়। তা ছাড়া কৃষিজমি মালিকানায় ক্ষয়িষ্ণু ধারা এবং ছোট ও প্রান্তিক কৃষকদের সংখ্যাবৃদ্ধি বাণিজ্যিক চাষাবাদের বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কৃষি উপকরণ জোগানের জন্য বিদেশনির্ভরতাও আমাদের উদ্বেগের বিষয়। আমাদের কৃষিব্যবস্থায় ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন ঘটছে। এর সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য সাম্প্রতিক তথ্য-উপাত্তের সমারোহ ঘটানো প্রয়োজন। এর জন্য গঠন করতে হবে কৃষি কমিশন। ওই কমিশন থেকে যে সুপারিশ আসবে, তা এই সরকার যতটুকু পারে বাস্তবায়ন করবে। ভবিষ্যতে নির্বাচিত সরকারের ওপর বাকিটা বাস্তবায়নের ভার থাকবে। এই অন্তর্বর্তী সরকার যদি কৃষি খাতে একটি রিভিউ করে যেতে পারে, তাহলে দেশের জন্য ভালো একটি কাজ হবে।
লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ। সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট। সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ



