বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক ধরনের প্রবৃদ্ধি আমরা লক্ষ করছি। এখানে উৎপাদন বৃদ্ধি করে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে আরো অনেক কিছু করার আছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেসব মার্কেটে যাচ্ছে, সেখানে অনেক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। সুতরাং সেদিক থেকে আমাদের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করার সক্ষমতা বাড়ানোর তাগিদ আগের তুলনায় বাড়ছে, তা আরো বাড়াতে হবে।
অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি
শ্রম ও প্রযুক্তিনির্ভরতা সমন্বয় করলে অগ্রগতি হবে
- মোস্তাফিজুর রহমান, সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি

 কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করতে হবে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ রপ্তানি খাতে পোশাকশিল্পে ৮৪ শতাংশ রপ্তানি করে। রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ যেভাবে হওয়ার কথা উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, শ্রম দক্ষতা বাড়িয়ে, পুঁজি দক্ষতা বাড়িয়ে, সে জায়গাটিতে আমাদের অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে; সেখানে বিনিয়োগ করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও গবেষণায় আরো বিনিয়োগ করতে হবে।
কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি করতে হবে। সেদিক থেকে বাংলাদেশ রপ্তানি খাতে পোশাকশিল্পে ৮৪ শতাংশ রপ্তানি করে। রপ্তানির বৈচিত্র্যকরণ যেভাবে হওয়ার কথা উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে, শ্রম দক্ষতা বাড়িয়ে, পুঁজি দক্ষতা বাড়িয়ে, সে জায়গাটিতে আমাদের অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে; সেখানে বিনিয়োগ করতে হবে। মানসম্মত শিক্ষা, দক্ষতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও গবেষণায় আরো বিনিয়োগ করতে হবে।শোভন কর্মসংস্থান এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ; এবং এটা শ্রমিকদের উৎপাদনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বৈশ্বিক বাজারের প্রেক্ষাপটেও এটি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি বেশি পণ্যের বাজারে প্রবেশের চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে, শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে হলেও এসব জায়গায় বেশি নজর দিতে হবে। কারণ শোভন কর্মসংস্থানের সঙ্গে উৎপাদনের একটা ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। আরেকটি বিষয়, যেটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, আমরা যে দেশগুলোর কাছে আমাদের পণ্য বিক্রি করি সেসব দেশ শোভন কর্মসংস্থানের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। এখন এটি বাজার ধরার একটি অনুঘটক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাত্ তারা আমাদের কাছ থেকে পণ্য কিনবে না, যদি আমরা শোভন কর্মসংস্থান, শ্রমিক নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ের দিকে গুরুত্বারোপ না করি। আর এ ধরনের শর্ত ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এ বিষয়গুলোকে রপ্তানি সক্ষমতা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতার অংশ হিসেবেই দেখতে হবে।
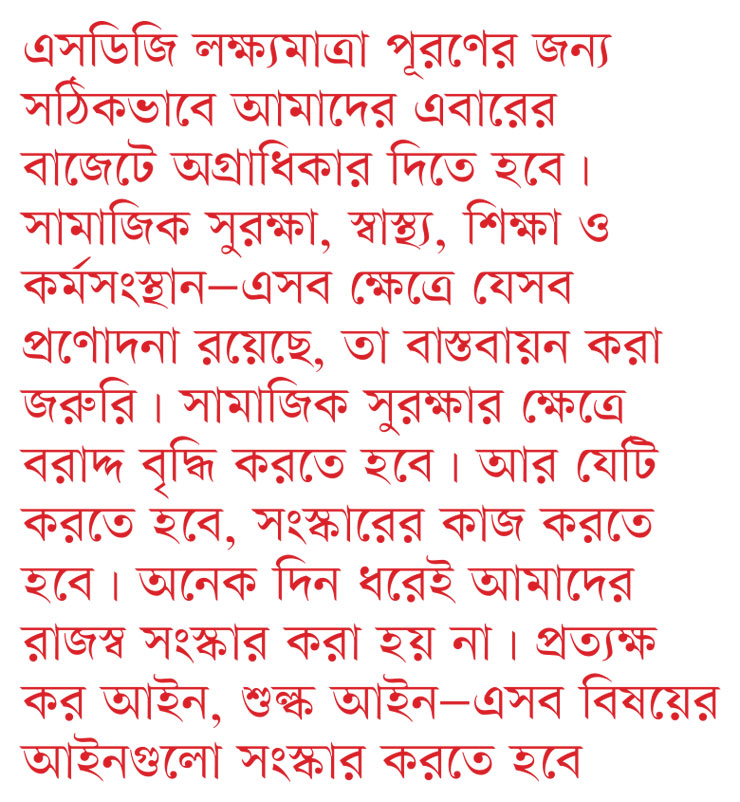 বাংলাদেশে এসডিজির সপ্তম বছর যাচ্ছে। আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচক, যেমন—খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধিতে আমরা ইতিবাচক অবস্থানে ছিলাম। এই চলমান করোনা মহামারি এসব অর্জনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে আমাদের যে অর্জন হয়েছিল, সেসব যে বাধাগ্রস্ত হলো, এখন সেসব কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে তা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত প্রান্তিক মানুষ যাতে সুফল পায় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের যে ধারাবাহিক অগ্রগতি ছিল, যেটি কভিডের কারণে পিছিয়ে গেছে, তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। বৈষম্য কমিয়ে আনার বিষয়ে এসডিজিতে আমাদের সূচক ছিল ১০। মহামারিতে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এভাবে নানা বিষয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
বাংলাদেশে এসডিজির সপ্তম বছর যাচ্ছে। আমাদের অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাও শুরু হয়ে গেছে। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক সূচক, যেমন—খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন, শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমিয়ে আনা, স্বাস্থ্যসেবা বৃদ্ধিতে আমরা ইতিবাচক অবস্থানে ছিলাম। এই চলমান করোনা মহামারি এসব অর্জনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যে আমাদের যে অর্জন হয়েছিল, সেসব যে বাধাগ্রস্ত হলো, এখন সেসব কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে তা পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত প্রান্তিক মানুষ যাতে সুফল পায় সেটি নিশ্চিত করতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে আমাদের যে ধারাবাহিক অগ্রগতি ছিল, যেটি কভিডের কারণে পিছিয়ে গেছে, তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। বৈষম্য কমিয়ে আনার বিষয়ে এসডিজিতে আমাদের সূচক ছিল ১০। মহামারিতে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এভাবে নানা বিষয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।
এসডিজি বাস্তবায়নে দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরই মধ্যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শুরু হয়েছে এসডিজি বাস্তবায়ন। সেটি হচ্ছে প্রথম ফেজ। এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকার হয়তো পুরো অর্থ জোগান দিতে পারবে না। কিন্তু অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। এসডিজি বাস্তবায়নে বেসরকারি উদ্যোক্তা, জনপ্রতিনিধি, এনজিও, গণমাধ্যমসহ সব শ্রেণির ভূমিকা রয়েছে। সেটি কাজে লাগাতে হবে। এসডিজি ব্যাপক, রূপান্তরযোগ্য, সংহত এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে তৈরি। এর লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের সময় নাগরিক অধিকারের প্রেক্ষাপটগুলো মাথায় রেখে পরিকল্পনা নিতে হবে। এসডিজি অর্জনের জন্য মানবাধিকার ও জেন্ডার সমতার বিষয়গুলো উপলব্ধি করা পথনির্দেশকের মতো কাজ করে। এগুলো নির্ভর করে উন্নয়নের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভারসাম্যের ওপর।
অর্থপাচারে বৈষম্য অবশ্যই বাড়ে। কয়েকটি পর্যায়ে বৈষম্য হয়। যে পরিমাণ অর্থ একজন পাচার করছে, সেটির ক্ষেত্রে পাচারকারী হয়তো ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছে অথবা কোনো দুর্নীতি করেছে। দুর্নীতি করলে সে হয়তো সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছে বা ঘুষ নিয়েছে। যেমন—বিদ্যুতের লাইন পেতে একজন যদি ১০০ টাকাও ঘুষ দেয়, সেটি তার আয় থেকে কমল। আর যে ঘুষ নিল তার আয় বাড়ল। এভাবেই বৈষম্যটা হয়। দুর্নীতি হচ্ছে বৈষম্যের একটি বড় উপায়। কারণ দুর্নীতি যে করছে সে সাধারণ মানুষের পকেট কাটছে। ২০১০ ও ২০১৬ সালে আমাদের বিবিএস যে খানা জরিপ করেছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে, আয়ের বিবেচনায় দেশের সর্বোচ্চ ৫ শতাংশে এবং সর্বনিম্ন ৫ শতাংশে অবস্থানকারীদের মধ্যে যে বৈষম্য, সেটি ২৩ গুণের জায়গায় ১২১ গুণ হয়ে গেছে। দুর্নীতিটা যখন হয়, তখন এক ধরনের বৈষম্য হয় ধনী-গরিবের মধ্যে। আর এই বৈষম্যই হলো এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের বড় বাধা। অর্থপাচারের অভিঘাত সমাজের ওপরে বিভিন্নভাবে পড়ছে। সুতরাং সেটিকে আমাদের থামাতে হবে।
এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য সঠিকভাবে আমাদের এবারের বাজেটে অগ্রাধিকার দিতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থান—এসব ক্ষেত্রে যেসব প্রণোদনা রয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা জরুরি। সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। আর যেটি করতে হবে, সংস্কারের কাজ করতে হবে। অনেক দিন ধরেই আমাদের রাজস্ব সংস্কার করা হয় না। প্রত্যক্ষ কর আইন, শুল্ক আইন—এসব বিষয়ের আইনগুলো সংস্কার করতে হবে। অনেক দিন ধরেই আমরা এসব অর্ধেক করে রেখেছি। এসব দ্রুত সংস্কার করার বিষয়ে তাগিদ দিতে হবে। ভ্যাট আইনের বাস্তবায়ন করতে হবে। নতুন বাজেটে এসব বিষয়কে চিহ্নিত করার পাশাপাশি বাস্তবায়নের একটি সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে।
বর্তমান পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেছে। এখন অপ্রত্যক্ষ করের পরিমাণ যদি কিছুটা কমিয়ে আনা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ তার সুবিধা পাবে। কর আদায়ের ক্ষেত্র আরো বিস্তৃত করতে হবে। তবে সেটা করতে গিয়ে যেন সাধারণের ভোগান্তি বৃদ্ধি না পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। সংস্কারগুলো করতে হবে। কম আয়ের মানুষদের বিশেষ সুবিধা দেওয়ার জন্য গত বাজেটে যে সুযোগ রাখা হয়েছিল, সেটি এবারও অব্যাহত রাখতে হবে। কিছু কিছু ভোগ্য পণ্য রয়েছে, সেসবের ভ্যাট-ট্যাক্স কমিয়ে আনতে হবে। তাতে কিছুটা সাশ্রয় হবে সাধারণ মানুষের। আর সর্বোচ্চ করের হার যেটি শুরুতে ৩০ শতাংশ ছিল, পরে সেটি কমিয়ে ২৫ শতাংশ করা হয়েছিল, আমার মনে হয় এটি আবার ৩০ শতাংশ করা উচিত। কারণ এটি ছিল অধিক আয় যাঁরা করেন তাঁদের জন্য। এ ছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু বৃদ্ধি করাই নয়, এর ব্যবস্থাপনায়ও গুরুত্ব দিতে হবে। এ ছাড়া ডিজিটাল ডিভাইসসহ ইন্টারনেট খাতের ভ্যাট-ট্যাক্স কমিয়ে আনতে হবে। এসব পদক্ষেপ নিয়ে যদি তার বাস্তবায়ন সঠিকভাবে করা যায় তাহলেই আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দিকে যেতে পারব।
সম্পর্কিত খবর
বৈশ্বিক অংশীদারত্ব
টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন বৈশ্বিক সহযোগিতা
- ড. মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, অর্থনীতিবিদ ও চেয়ারম্যান, বেসরকারি গবেষণা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র্যাপিড)

জাতিসংঘ ২০১৫ সালে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) গ্রহণ করে, যা ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বে শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এসডিজির মূল প্রতিশ্রুতি হলো—কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না। এসডিজির মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে বিশ্বব্যাপী অংশীদারত্বের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ১৭টি অভীষ্টের সর্বশেষটি হলো—‘টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা’।

এসডিজি-১৭ গৃহীত হওয়ার পরপর বিশ্ব বেশ কিছু ঘটনার সম্মুখীন হয়, যা বৈশ্বিক অংশীদারত্ব অর্জনে একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি করে। ২০১৫-১৬ সালের বৈশ্বিক মন্দা, মার্কিন যুক্তরাজ্যের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য যুদ্ধ, ভারত ও চীনের মধ্যে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সাম্প্রতিক সংঘাত সেসব ঘটনার কিছু উদাহরণ। কভিড-পরর্বতী সময়ে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সামষ্টিক অর্থনৈতিক সংকট আরো বেশ প্রকট করে তোলে।
এসডিজি ১৭-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করা। এই সূচকের মূল উদ্দেশ্য হলো ঋণগ্রস্ত দরিদ্র দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণের সংকট কমানো, যা দেশগুলোর জন্য টেকসই অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে। কিন্তু এসডিজির সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর অর্ধেকেরও বেশি ঋণখেলাপি হওয়ার ঝুঁকিতে আছে।
অফিশিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স (ওডিএ) নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতিসংঘ উন্নত দেশগুলোর জন্য তাদের মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ০.৭ শতাংশ ওডিএতে বরাদ্দ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ২০২২ সালের নেট ওডিএর পরিমাণ ছিল ২০৬ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২১ সালের চেয়ে ১৫.৩ শতাংশ বেশি। এই সাহায্য বৃদ্ধির প্রধান কারণ ছিল উন্নত দেশগুলো ইউক্রেন ও শরণার্থীদের সহায়তা করবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে প্রদত্ত সহায়তা প্রকৃতপক্ষে হ্রাস পেয়েছে। জাতিসংঘ প্রকাশিত দ্য লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ রিপোর্ট-২০২৩ অনুযায়ী, ২০২১ সালে ৪৬টি স্বল্পোন্নত দেশে সাহায্য হিসেবে দেওয়া মোট অর্থ ছিল প্রায় ৬৭ বিলিয়ন ডলার, যা তারা ২০২০ সালে প্রাপ্ত সর্বাধিক প্রায় ৭৩ বিলিয়ন ডলারের চেয়ে কম। বৈদেশিক সাহায্যের উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উন্নত দেশগুলো তাদের জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ ওডিএ হিসেবে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। ২০২২ সালে মাত্র পাঁচটি দেশ—লুক্সেমবার্গ, সুইডেন, নরওয়ে, জার্মানি ও ডেনমার্ক এই লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছিল। বেশির ভাগ উন্নত দেশের এই প্রতিশ্রুতি পূরণের ব্যর্থতা উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ওপর বোঝা চাপিয়ে দেয়।
 ২০১৪ সালে আংকটাডের হিসাব অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০১৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর প্রায় ৩.৯ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে। সে সময় আংকটাড ১০টি গুরুত্বপূর্ণ খাতকে বিবেচনা করে এবং এসব খাতে মোট বিনিয়োগের ঘাটতি ছিল ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী এই ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। জ্বালানি, পানি ও পরিবহন অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি। সেই সঙ্গে গত বছরের তুলনায় ২০২২ সালে বিশ্বে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ কমেছে ১২ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কমেছে।
২০১৪ সালে আংকটাডের হিসাব অনুযায়ী, উন্নয়নশীল দেশে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০১৫ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর প্রায় ৩.৯ ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে হবে। সে সময় আংকটাড ১০টি গুরুত্বপূর্ণ খাতকে বিবেচনা করে এবং এসব খাতে মোট বিনিয়োগের ঘাটতি ছিল ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার। জাতিসংঘের সাম্প্রতিক ওয়ার্ল্ড ইনভেস্টমেন্ট রিপোর্ট ২০২৩ সালের হিসাব অনুযায়ী এই ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার ট্রিলিয়ন ডলারেরও বেশি। জ্বালানি, পানি ও পরিবহন অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগের ঘাটতি সবচেয়ে বেশি। সেই সঙ্গে গত বছরের তুলনায় ২০২২ সালে বিশ্বে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ কমেছে ১২ শতাংশ। উন্নয়নশীল দেশে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কিছুটা বাড়লেও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এই বিনিয়োগের পরিমাণ কমেছে।
উন্নত দেশগুলো থেকে ওডিএ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি না পেলেও তাদের সামরিক ব্যয় রেকর্ড হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২২ সালে বিশ্বে সামরিক খাতে মোট ব্যয় হয়েছে প্রায় ২.২ ট্রিলিয়ন ডলার। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা অনুযায়ী, আট বছর ধরে এই খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।
এসডিজি ১৭-এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল দোহা উন্নয়ন এজেন্ডায় আলোচনা শেষ করার মাধ্যমে একটি সর্বজনীন, নিয়মভিত্তিক, উন্মুক্ত, অবৈষম্যহীন এবং ন্যায্য বহুপক্ষীয় বাণিজ্যব্যবস্থা তৈরি করা। দোহা ডেভেলপমেন্ট এজেন্ডার প্রধান উদ্দেশ্য হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বাণিজ্য সম্ভাবনা প্রসারিত করা। ২০০১ সালে কাতারের দোহায় মন্ত্রী পর্যায়ের চতুর্থ বৈঠকের ২২ বছর পর দোহা রাউন্ড, যেটাকে উন্নয়ন রাউন্ড হিসেবে দেখা হয়েছিল, তা এখন কোনো ফলাফল ছাড়াই মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে। এই রাউন্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বাজারে প্রবেশাধিকার সহজতর করে, ন্যায্য নিয়মসমূহের বাস্তবায়ন এবং টেকসই প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য বৃদ্ধি থেকে লাভবান হতে সক্ষম করা। দুর্ভাগ্যবশত এটা পরিহাসের বিষয় যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বর্তমানে যেভাবে কাজ করছে তা থেকে বোঝা যায়, দোহা রাউন্ড তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। এসডিজি ১৭-এর আরো একটি লক্ষ্য ছিল ২০২০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক রপ্তানিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর হিস্যা দ্বিগুণ করা। কিন্তু ২০১১ সাল থেকে বৈশ্বিক পণ্য ও সেবা রপ্তানিতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অংশ ১ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি করা যায়নি এবং ভবিষ্যতে তা বৃদ্ধি করা যাবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে এমন কিছু বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করার প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, যা দেশীয় বাজারে উৎপাদনকে উৎসাহিত করে বিশ্ববাণিজ্যকে নিরুৎসাহ করছে। আমেরিকার ইনফ্লেশন রিডাকশন অ্যাক্ট, ভারতের মেক ইন ইন্ডিয়া পলিসি বা চীনের মেড ইন চায়না : ২০২৫ পরিকল্পনা—এসব নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো অন্য দেশের ওপর নির্ভরশীলতা কমানো এবং দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ দেওয়া। বিশ্বের মোড়ল দেশগুলোর এই ধরনের নীতি বা কৌশল গ্রহণ করার অর্থ হলো তুলনামূলক সুবিধার বা কম্প্যারেটিভ অ্যাডভান্টেজের মাধ্যমে অন্য বাণিজ্য অংশীদারদের লাভ করার পথ বন্ধ করে দেওয়া। এতে বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নয়নের যে ধারণা এবং এসডিজির যে মূল প্রতিশ্রুতি, ‘কাউকে পেছনে ফেলে রাখা যাবে না’, সেটিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সেই সঙ্গে বিশ্বের বড় দেশগুলো তাদের বাণিজ্যনীতিতে যে ধরনের ভর্তুকির ব্যবস্থা রেখেছে, তা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কিন্তু বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার মধ্যে যে অচলাবস্থা চলছে, তাতে এ ধরনের নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে মনে হয় না।
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তার শক্তিশালী ও স্বচ্ছ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার কারণে অন্যান্য সংস্থা থেকে আলাদা। কিন্তু বর্তমানে আপিল বিভাগকে অকেজো করার মাধ্যমে এই সংস্থার বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া নিয়ে সদস্য দেশগুলো অনেক দিন ধরে আপত্তি জানিয়ে আসছিল। তাদের বিরোধের কারণে ডিসেম্বর ২০১৯ সালের পর থেকে আপিল বিভাগে বিচারক নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। বিচারকের অভাবে বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাচ্ছে না, যা বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে পারে।
বিশ্বব্যাপী চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা এবং দ্বন্দ্ব বৈশ্বিক সহযোগিতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে, যা এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে সংশয় তৈরি করেছে। বিশ্বব্যাপী অংশীদারত্ব এখন খণ্ডিত, এবং এই সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একটি সম্মেলনের প্রয়োজন রয়েছে। চলমান সম্যসাগুলো সমাধান না হলে ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত এবং ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলের আগ্রাসন আলোচিত হলেও ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রধান বিষয় হলো অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান এবং তা বিশ্বব্যবস্থায় কিভাবে সন্নিবেশিত হবে তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের রেষারেষি এবং এশিয়ার চীন ও ভারতের আঞ্চলিক প্রতিপত্তির লড়াই বিশ্ব অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকে উসকে দিচ্ছে। বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার বর্তমান দোদুল্যমান অবস্থার একটি বড় কারণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের উৎকাণ্ঠা, যেন নিয়মতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় চীন এবং বড় উন্নয়নশীল দেশগুলো বেশি সুবিধা না পায়।
বাণিজ্যের চিরাচরিত ক্ষেত্র, যেমন—পণ্যদ্রব্য ও সেবা খাতের পাশাপাশি নতুন বিষয়, যেমন—প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও তার বাণিজ্য নিয়ে রীতিমতো এখন তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। বস্তুত বিশ্ব বাণিজ্যের অনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এখন প্রকট হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যারা অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তাদের জন্য বিশ্ব বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যবস্থাপনা চরম দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
উন্নয়নশীল সব দেশেই ব্যাপক বিনিয়োগ দরকার। অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য-শিক্ষা, শিল্প—সর্বত্র প্রয়োজন রয়েছে নতুন পুঁজির। কিন্তু আবার বেল্ট ও রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় করা বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যকে চীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তারের উপায় হিসেবে দেখা হচ্ছে। ফলে অনেক উন্নয়নশীল দেশ, যারা চীনের বর্ধিত বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভবান হতে চায়, তাদের বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ১৯৬০ থেকে ১৯৯০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্নায়ুযুদ্ধের খেসারত দিতে হয়েছিল তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশকে। সে রকম একটা অবস্থার দিকে বিশ্ব আবার ঝুঁকে পড়েছে।
উন্নয়ন অংশীদারত্ব এখন খণ্ডিত, দুর্বল ও অস্পষ্ট। ভূ-রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার বিরূপ প্রভাবকে যথাযথভাবে মোকাবেলা করতে না পারলে উন্নয়ন সহযোগিতার কাঠামো সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়বে। এসডিজি সনদকে বিশ্ব উন্নয়ন কাঠামোর মূল নির্দেশিকা হিসেবে ধরে নিয়ে বিশ্বের অর্থনৈতিক ও ভূ-রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে কিভাবে একটি বহুমাত্রিক জবাবদিহির মধ্যে নিয়ে আসা যায়, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
একান্ত সাক্ষাৎকারে খলিলুর রহমান
বঙ্গবন্ধুর হাত দিয়ে শুরু হয়েছে ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কার
- খলিলুর রহমান ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি মাঠ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদ সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), জেলা প্রশাসক (ডিসি), বিভাগীয় কমিশনারসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে কাজ করেছেন। ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছে কালের কণ্ঠ। সাক্ষাত্কার নিয়েছেন দেলওয়ার হোসেন

ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন কিভাবে শুরু হলো?
বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত দিয়ে শুরু হয়েছে। এরপর যুগান্তকারী সংস্কারের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট ভূমিসেবায় রূপ লাভ করেছে। ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন ও স্মার্ট ভূমিসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় নিত্যনতুন উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এরই মধ্যে দেশের জনগণ ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন ও স্মার্ট ভূমিসেবার সুফল ভোগ করতে শুরু করেছে।
 ভূমি ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করতে বঙ্গবন্ধু কী উদ্যোগ নিয়েছিলেন?
ভূমি ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী করতে বঙ্গবন্ধু কী উদ্যোগ নিয়েছিলেন?
স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর গঠন করেন।
ডিজিটাল ভূমিসেবা চালু হলো কিভাবে?
আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১০ সালে মৌজা ম্যাপের ডিজিটাল প্রতিলিপি তৈরির কাজ শুরু করার মাধ্যমে ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের যাত্রা শুরু হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় উদ্যোগে ডিজিটাইজেশনের কাজ শুরু হয়। ২০১৬ সালে একটি সামগ্রিক ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়। ২০১৮ সালে ই-নামজারি সিস্টেম বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে সার্ভিস ডিজিটাইজেশনে প্রবেশ করে ভূমি মন্ত্রণালয়। ২০২১ সালে পুরো ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশনের রপরেখা তৈরি করা হয়।
স্মার্ট ভূমিসেবা বাস্তবায়নে ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা কী?
ভূমি সংস্কার ও ভূমিসেবা ডিজিটাইজেশন সর্বজনস্বীকৃত একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। এর পরও ২০৪১ সালের উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশে স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিসেবা নিশ্চিত করতে ভূমি মন্ত্রণালয় দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ জন্য রাজধানীর তেজগাঁওয়ে ভূমি ভবনে পরীক্ষামূলকভাবে একটি ‘স্মার্ট ভূমিসেবা কেন্দ্র’ চালু করা হয়েছে। এ রকম সেবা পর্যায়ক্রমে দেশব্যাপী বিস্তৃত করা হবে। এ ছাড়া স্মার্ট ভূমিসেবা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৩ সালে জাতীয় ভূমি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর, নামজারি, রেকর্ড, নকশা, ভূমিপিডিয়াসহ ভূমিসংক্রান্ত সব সেবা আরো স্মার্ট করার কাজ চলমান। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থাসমূহের সঙ্গে আন্ত সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবাগুলো আরো যুগোপযোগী, নির্ভুল ও নিরাপদ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
জরিপে ভুল রেকর্ড হলে সমাধানের উপায় কী?
জরিপ চলাকালে ভুল রেকর্ড সংশোধনের দুটি ধাপ রয়েছে, প্রচলিত ভাষায় যা ৩০ বিধি বা আপত্তি স্তর নামে পরিচিত। কেউ আপত্তি দেওয়ার পর জরিপ বিভাগের একজন কর্মকর্তা এর শুনানি গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন। এই সিদ্ধান্তের ওপর আবার কোনো আপত্তি থাকলে ৩১ বিধিতে আপিল করতে হবে। আপিলের সিদ্ধান্ত সঠিক না হলে ছাপানো রেকর্ড প্রকাশের পর রেকর্ড সংশোধনের ক্ষেত্রে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে যেতে হবে। তবে ট্রাইব্যুনালের রায়ে সংক্ষুব্ধ হলে ল্যান্ড সার্ভে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে এবং পরে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করা যাবে। কেউ সংক্ষুব্ধ হয়ে পরের ধাপে না গেলে আগের রায় চূড়ান্ত হবে। একজন জমির মালিক হিসেবে জরিপ চলাকালে আপনার প্রধান দায়িত্ব হলো চোখ-কান খোলা রাখা। অর্থাৎ জরিপ সম্পর্কে খোঁজখবর রাখা। বেশ কয়েকটি ধাপে জরিপকাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্রতিটি ধাপে আপত্তি বা আবেদন দিয়ে মালিকানা নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি ধাপে স্বীয় স্বার্থ সঠিক আছে কি না যাচাই করবেন। তবে জরিপের গেজেট প্রকাশের পর ভুলটি যদি কেবল গাণিতিক বা করণিক ভুল হয়, তাহলে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর নিকট আবেদন করলে সংশোধন হতে পারে। একবার জরিপের রেকর্ডের গেজেট প্রকাশিত হওয়ার পর যতবার জমি কেনাবেচা হবে বা অন্যভাবে মালিকানা পরিবর্তন হবে, ততবারই উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিস থেকে নতুন ক্রেতার নামে নামজারি বা রেকর্ড সংশোধন করতে হবে। এই প্রক্রিয়াকে আমরা নামপত্তন বা নাম খারিজ বা নামজারি বলি। সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ কাজটি সম্পাদন করে থাকেন।
ভূমিসেবা ডিজিটাল হওয়ায় সরকারের কী সুবিধা?
ভূমিসেবার ডিজিটাইজেশন একদিকে যেমন মানুষের হয়রানি ও ভোগান্তি কমিয়েছে, ঠিক অন্যদিকে এই সিস্টেমগুলোর কারণে সরকারের রাজস্ব আয় বেড়েছে বহুগুণ। অফলাইন থেকে অনলাইনে আসার কারণে শুধু ভূমি উন্নয়ন করই বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৫৬ শতাংশ। ডিজিটাল ভূমিসেবা থেকে অনলাইনে সরকারের প্রতিদিন গড় রাজস্ব আদায় পাঁচ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে। এসব ডিজিটাল ভূমিসেবা সফলভাবে বাস্তবায়ন করায় ভূমি মন্ত্রণালয় এরই মধ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২০ সালে ই-নামজারির জন্য অর্জন করেছে জাতিসংঘ জনসেবা পদক। ২০২২ সালে ডিজিটাল ভূমি উন্নয়ন করের জন্য পেয়েছে সম্মানজনক ডাব্লিউএসআইএস ও ডিজিটাল বাংলাদেশ পুরস্কার।
ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?
আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী স্মার্ট ভূমিসেবা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হবে। এ ছাড়া ২০২৬ সাল নাগাদ ভূমিসেবার কল্পচিত্র হলো, ভূমিসংক্রান্ত সব সেবা এক প্ল্যাটফরমে পাওয়া যাবে। সব ভূমিসেবা ও ভূমি রেকর্ড এবং মৌজা ম্যাপ ইন্টারকানেক্টেড থাকবে। ভূমি নিয়ে কোনো মামলা-মোকদ্দমা তেমন থাকবে না। সীমানা বিরোধ হবে প্রায় শূন্য। নাগরিকদের খুব প্রয়োজন ছাড়া ভূমি অফিসে যেতে হবে না। এনআইডি দিয়েই পাওয়া যাবে একজন নাগরিকের জমির সব তথ্য। আর জমি ক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাবে ভূমি মালিকানা সনদ বা সিএলও (সার্টিফিকেট অব ল্যান্ড ওনারশিপ)। যেসব জায়গায় একবার ডিজিটাল জরিপ সম্পন্ন হবে, সেখানে ভবিষ্যতে আর জরিপ করার প্রয়োজন পড়বে না।
মানবপাচারের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও করণীয়
- যীশু বড়ুয়া, ফোকাল পার্সন, মানবপাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম, ইপসা

মানবপাচার একটি সংঘবদ্ধ জঘন্যতম এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা ও সামাজিক ব্যাধি। বিশ্বে প্রতিবছর হাজার হাজার সাধারণ মানুষ, বিশেষত নারী, শিশু ও পুরুষ মানবপাচারের শিকার হয়। বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। যদিও বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার অনেক আগে থেকেই এ অঞ্চলে মানবপাচার সংঘটিত হয়ে আসছিল।

পাশাপাশি মানবপাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও সহযোগিতার জন্য কোনো ব্যবস্থা ছিল না।
ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের কারণে বাংলাদেশ বহু আগে থেকেই মানবপাচারের উৎসভূমি এবং ট্রানজিট হিসেবে মানবপাচারকারীদের কাছে কৌশলিক ও নিরাপদ স্থান।
২০১৪ সালের ট্রাফিকিং ইন পারসন (টিআইপি) রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশকে নারী, শিশু ও পুরুষ, বিশেষ করে শ্রম পাচারের একটি উৎস এবং রুট কান্ট্রি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এর মধ্যে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা অন্যতম। কারণ এই দুটি জেলা উপকূলীয় ও সীমান্তবর্তী। আর্থ-সামাজিক ও ভৌগোলিক কারণে এখানকার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে হতদরিদ্র ও বেকার যুবসমাজ মানবপাচারকারীদের খপ্পরে পড়ে আর্থিক ও সামাজিকভাবে শোষণের শিকার হচ্ছে। এই দুটি জেলা, বিশেষ করে কক্সবাজারে শিক্ষার হার বাংলাদেশে সবচেয়ে কম। এখানে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চল গড়ে না ওঠার কারণে এ অঞ্চলের অসংখ্য যুবক-যুবতি বেকারত্বে ভোগে। এই অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে এক শ্রেণির দালালচক্র অতি কৌশলে দেশের অভ্যন্তরে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা বা মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন উন্নত দেশে ভালো চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে পাচার করে থাকে, যা এরই মধ্যে বিশ্বব্যাপী আলোচিত।
বাংলাদেশের এই দুটি জেলা—চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে ইপসা (ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল অ্যাকশন) একটি বেসরকারি সংস্থা হিসেবে সরকারের পাশাপাশি মানবপাচার প্রতিরোধ এবং মানবপাচারের শিকার ব্যক্তিদের সুরক্ষাকল্পে দুই দশক ধরে কাজ করে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে ইপসা এই সময়ের মধ্যে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। অভিজ্ঞতার আলোকে এ অঞ্চলে যেসব কারণে মানবপাচার সংঘটিত হচ্ছে এবং মানবপাচারকারীদের কেন শাস্তির আওতায় আনা যাচ্ছে না তার বিশ্লেষণ করা যাক। পাশাপাশি কী কী পদক্ষেপ নিলে এই অবস্থার উত্তরণ করা যেতে পারে সে সম্পর্কে কিছু সুপারিশ প্রদানের প্রয়াস নেওয়া হলো।
মানবপাচার সংঘটিত হওয়ার কারণ
অধিক জনসংখ্যা, শিক্ষার অভাব, বেকারত্ব, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কর্মসংস্থানের অভাব, অসচেতনতা, অজ্ঞতা, পর্যটনপল্লী, পারিবারিক সহিংসতা, উন্নত জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, বিস্তৃত জলসীমায় অপর্যাপ্ত সীমান্তরক্ষী বাহিনী থাকার কারণে অবাধে মানবপাচারের সুযোগ।
মানবপাচারকারীরা অসহায় যুবক-যুবতিদের বিদেশে অবস্থানরত পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিদের উন্নত জীবনের উদাহরণ দিয়ে থাকে, যাঁরা একসময় অবৈধভাবে (পাচারকারীদের সহায়তায়) বিদেশে গিয়ে অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের দালানঘর তৈরি করেছেন। এই সব উদাহরণ সামনে এনে পাচারকারীরা সহজেই স্থানীয় বেকার যুবক-যুবতিদের প্রলুব্ধ করে অবৈধভাবে অথবা বৈধভাবে বিদেশে পাচার করছে এবং এর মাধ্যমে যুবক-যুবতিরা মানব পাচার চক্রের মাধ্যমে আর্থিক, সামাজিক, শারীরিক, মানসিক ও যৌন শোষণের শিকার হচ্ছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যুবক-যুবতিরা ঘনিষ্ঠজনদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাচারকারীদের মাধ্যমে অতি অল্প সময়ে বিদিশে যেতে উদ্বুদ্ধ হয়।
কেন মানবপাচারকারীরা আইনের আওতার বাইরে
পাচারের শিকার ব্যক্তিরা আইনি ঝামেলায় যেতে ভয় পায়। কারণ মানবপাচারকারীরা স্থানীয় এবং তারা প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়। পাচারকারীদের নেটওয়ার্ক অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মূল পাচারকারীরা সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে। অনেক পাচারকারী আবার রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে, যার কারণে তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে চায় না। এ ছাড়া আইনে জামিন অযোগ্য উল্লেখ থাকলেও জামিন পেয়ে যায় পাচারকারীরা। আইনের সঠিক ব্যবহার না হওয়াও একটি কারণ। সব জেলায় আলাদা ট্রাইব্যুনাল না থাকায় মানবপাচারের মামলাগুলো নারী ও শিশু কোর্টে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় মামলাগুলোর দীর্ঘসূত্রতা বেড়ে যায়, যার ফলে ভিকটিম মামলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের এ আইন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় মানবপাচারের মামলাগুলো অন্য মামলার ধারায় ফেলা হয়। যার কারণে পাচারকারীরা জামিন পেয়ে যায়। যদিও আইনে আছে, মানবপাচারের মামলা কোর্টের বাইরে মীমাংসা করা যাবে না, তার পরও পাচারকারীদের চাপে পড়ে ভিকটিমরা বাধ্য হয়ে, ভয়ে মীমাংসা করে থাকে।
মানবপাচার প্রতিরোধে করণীয়
মানবপাচার প্রতিরোধে ব্যাপক হারে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২ সম্পর্কে আরো বেশি প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। সরকারি-বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করতে হবে। মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন-২০১২ ও জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-১৭, ২০১৮-২২ ও ২০২২-২৬ অনুযায়ী মানবপাচারের শিকার সারভাইভরদের জন্য শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক সেবার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।
রোহিঙ্গা ইনফ্লাস্ক ও মানবপাচার
২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট রোহিঙ্গা আগমনের পর বাংলাদেশে কক্সবাজারে মানবপাচারের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। রোহিঙ্গাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এক শ্রেণির দালালচক্র, বাংলাদেশি নাগরিক ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী সম্মিলিতভাবে মানবপাচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী মানবপাচারের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। নভেম্বর ২০২৩-এ অবৈধভাবে মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার সময় ট্রলার ভাসতে দেখে টেনে কূলে নিয়ে আসায় তিন শতাধিক রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ ও শিশু প্রাণে রক্ষা পায়। এমনকি টেকনাফ এলাকায় মানবপাচারের ঘটনায় বাধা দিতে গিয়ে স্থানীয় দুজন যুবককে পাচারকারীরা গুলিবিদ্ধ করে এবং গুরুতর আহত করে। মানবপাচারের এই ঘটনাগুলো এখনই থামানো না গেলে এর চেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়ে গেছে।
শিশু সুরক্ষা
শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ : প্রয়োজন সমন্বিত পদক্ষেপ
- মনিরুজ্জামান মুকুল, সাধারণ সম্পাদক, স্ট্রিট চিলড্রেন অ্যাক্টিভিস্টস নেটওয়ার্ক (স্ক্যান), বাংলাদেশ

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ। একটি শিশুর জন্ম মানেই একটি নতুন সম্ভাবনা তৈরি হওয়া। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমরা সেই সম্ভাবনা কাজে লাগাতে পারি না। শিশুর প্রতি নির্যাতন-নিপীড়ন-সহিংসতার কারণে অকালেই অসংখ্য সম্ভাবনার মৃত্যু ঘটে।
 আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রতিদিন পরিবারের প্রতি ১০ জনে ৬ জন শিশু শারীরিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। আর ১৪ বছর বয়সের আগেই বাংলাদেশে প্রায় ৮২ শতাংশ শিশু বিভিন্নভাবে সহিংসতার শিকার হয়। ৭৭.১ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ ছাড়া ৫৭ শতাংশ শিশু কর্মক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশনের এক গবেষণায় বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রতিদিন পরিবারের প্রতি ১০ জনে ৬ জন শিশু শারীরিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। আর ১৪ বছর বয়সের আগেই বাংলাদেশে প্রায় ৮২ শতাংশ শিশু বিভিন্নভাবে সহিংসতার শিকার হয়। ৭৭.১ শতাংশ শিশু বিদ্যালয়ে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ ছাড়া ৫৭ শতাংশ শিশু কর্মক্ষেত্রে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।
উন্নয়ন সংস্থা মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ)-এর শিশু পরিস্থিতি প্রতিবেদন-২০২২-এর তথ্যানুসারে, এক বছরে ১২টি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ২৮ শতাংশ। সেগুলো হলো—যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, ধর্ষণচেষ্টা, সড়ক দুর্ঘটনা, অন্য দুর্ঘটনা, অপহরণ, হত্যা, নির্যাতন, আত্মহত্যা, অপরাধে সংশ্লিষ্ট শিশু, নিখোঁজ ও পানিতে ডুবে মৃত্যু। এসব ক্ষেত্রে ২০২১ সালে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা ছিল দুই হাজার ৪২৬। ২০২২ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় তিন হাজার ৯৪।
জাতিসংঘ শিশু তহবিলের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ৫৬.৯ মিলিয়ন শিশুর মধ্যে পাঁচ বছরের নিচে ৪৪ শতাংশ শিশুর জন্ম নিবন্ধন নেই, পথশিশুদের মধ্যে প্রায় ৮২.৯ শতাংশ শোষণ ও নির্যাতনের শিকার, পথশিশুদের ৩১.১ শতাংশ খোলা জায়গায় ঘুমায়, ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ১১.৩ শতাংশ শিশুশ্রম ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের সঙ্গে যুক্ত, ৫১.৪ শতাংশ বাল্যবিবাহের শিকার এবং মোট শিশুর ২০ শতাংশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির মধ্যে আছে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিশু ভর্তির হার ৯৭.৪২ শতাংশ হলেও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করতে পেরেছে ৬৪.২৪ শতাংশ শিশু। আর ১-১৪ বছর বয়সী শিশুদের প্রায় ৮৯ শতাংশ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার। প্রতি মাসে প্রায় ৪০০ জন নারী ও শিশু পাচারের শিকার হয় বলে তথ্য দিয়েছে জাতিসংঘ শিশু তহবিল।
 জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের জন্য ১৯৭৪ সালে শিশুনীতি প্রণয়ন করেন। আর শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও সুরক্ষায় ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করে। ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন সম্ভব হয়। এরপর ২০১৫ সালে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগের ধারাবাহিকতায় সরকার এসডিজি অর্জনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ওই সব পদক্ষেপে ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ নীতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিশুদের জন্য ১৯৭৪ সালে শিশুনীতি প্রণয়ন করেন। আর শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও সুরক্ষায় ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষর করে। ধারাবাহিক পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন সম্ভব হয়। এরপর ২০১৫ সালে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগের ধারাবাহিকতায় সরকার এসডিজি অর্জনে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ওই সব পদক্ষেপে ‘কাউকে পেছনে ফেলে নয়’ নীতির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।
এসডিজিতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সরকার স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে এসংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আন্তরিক। তবে বরাদ্দকৃত বাজেট ব্যয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট খাত উল্লেখ না থাকায়, শুধু বাজেট বরাদ্দ সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। এরই মধ্যে শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের সুরক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পথশিশুদের সুরক্ষা, যৌন নির্যাতন থেকে সুরক্ষা, দুস্থ বা সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের জন্য বিভিন্ন ধরনের ভাতা, সমাজসেবা অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে। সরকারের এই ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যেও নির্দিষ্ট সময়ে এসডিজি অর্জন কিছুটা হলেও বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
ইউনিসেফের দেওয়া তথ্য মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে পাঁচ কোটি ৭০ লাখের কাছাকাছি শিশু রয়েছে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। এর মধ্যে ১৪ বছরের নিচে প্রায় সাড়ে চার কোটি শিশু বাড়িতে শারীরিক ও মানসিক সহিংসতার শিকার হচ্ছে। অর্থাৎ প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ৯ জন নির্যাতিত এবং প্রতি সপ্তাহে মারা যাচ্ছে ২০ জন শিশু, যা আমাদের এসডিজি অর্জনকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দিচ্ছে।
এসডিজির ২০২১ সালের মূল্যায়ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, শিশুদের মধ্যে পুষ্টিহীনতার ব্যাপকতা ২০১৬ সালে ছিল ১৫.১০ শতাংশ। সেটা ২০২০ সালে ১৩ শতাংশে নেমে এসেছে। কমেছে খর্বতা ও কৃশতা এবং নবজাতকের মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে ১৫)। জন্ম নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এরই মধ্যে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছে উল্লেখযোগ্য।
তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশেষ করে শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়নে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যা শিশুদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার সহিংসতা, নির্যাতন, শোষণ ও পাচারের মতো অপতৎপরতা রোধে বাধা সৃষ্টি করছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিচালনার ক্ষেত্রে শিশু সুরক্ষা ঝুঁকিতে আছে, এমন পরিবারের অন্তর্ভুক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে না। ফলে যথাযথ বরাদ্দ দেওয়ার পরও শিশুপাচার, শিশুশ্রম, পথশিশু বা পুষ্টিহীনতা বন্ধ হচ্ছে না। নাগরিক পরিষেবাসমূহ বেশির ভাগই নগরকেন্দ্রিক হওয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ বা জীবনধারণের জন্য মানুষ নগরমুখী হচ্ছে। নদীভাঙন, উপকূলীয় এলাকায় জলোচ্ছ্বাসসহ বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়ে শহরের বস্তিতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে।
এ ছাড়া সরকারের বিভিন্ন দপ্তর ও সেবাসমূহের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়হীনতা রয়েছে। পথশিশুসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে দেখা যায়, মাদকাসক্ত শিশুদের নিরাময়ে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হচ্ছে। তবে মাদকাসক্তমুক্ত হওয়ার পর ওই শিশুরা আবার ওই পথে চলে আসছে। আবার সরকারি সেবা প্রাপ্তির জন্য যথাযথ তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে কম পৌঁছাচ্ছে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ তা গ্রহণ করতে পারছে না। সরকারের লিগ্যাল এইডের অর্থের যথাযথ ব্যয় হচ্ছে না। শিক্ষা সম্পর্কিত আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দরিদ্র মানুষের পক্ষে শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করা দুরূহ হয়ে পড়ছে। ফলে স্কুল থেকে ঝরে পড়া, শিশুশ্রম, বাল্যবিবাহ বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়ছে। প্রতিটি জেলায় শিশুপাচার প্রতিরোধে কমিটির পাশাপাশি স্থানীয় সরকারের পারিবারিক বিরোধ নিরসন এবং নারী ও শিশু কল্যাণ কমিটি আছে। কিন্তু কমিটিগুলো অনেকটাই কাগুজে, ফলে শিশুর ঝুঁকি মোকাবেলা কঠিন হয়ে পড়ছে।
সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রমে প্রাতিষ্ঠানিক খাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অথচ প্রায় ৯৫ শতাংশ শিশুশ্রম অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শিশুশ্রমের গুরুত্ব কম থাকায় এবং শিশুশ্রম মনিটরিং কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় শিশুশ্রম নিরসন দুরূহ হয়ে পড়ছে। নাগরিক পরিষেবা প্রাপ্তির বা নাগরিকের প্রাথমিক প্রমাণপত্র হিসেবে কাজ করে জন্ম নিবন্ধন সনদ। সুবিধাবঞ্চিত শিশু, বিশেষ করে পতিতালয়ের শিশু ও পথশিশুদের জন্ম নিবন্ধন প্রাপ্তি এখনো একটি জটিল প্রক্রিয়া। ফলে ওই শিশুরা পড়ালেখাসহ অন্যান্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে সমন্বিতভাবে কাজ করলে এসডিজি অর্জন সহজতর হবে।
এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিশুদের জন্য আলাদা অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয়তা এখন সময়ের দাবি। এই অধিদপ্তর শিশুদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, প্রয়োজনীয় বাজেট, কর্মসূচি, সরকারি-বেসরকারি কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৩৩ শতাংশ শিশুর সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। শিশু সুরক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থা ও সেবা গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা, প্রয়োজনে শিশুবান্ধব আইন ও নীতিমালা তৈরি করবে। শিশুর জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পাশাপাশি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।


