শাহদারাতে আমার অবস্থান তখন ৯ মাসের মতো হয়েছে। ওখানকার প্রশাসন, লোকজন, তাদের সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি জানা হয়ে গেছে। এদিকে আমার বস শেখপুরা জেলার ডিসি। তিনি প্রাদেশিক সার্ভিসের অফিসার ছিলেন এবং লাহোর বিভাগের কমিশনার ফতেহ খান বুন্দিয়াল আমাকে যেতে দেবেন না। তাঁরা পাঞ্জাবের চিফ সেক্রেটারি আফজাল আগা (?)-কে খুব করে বললেন আদেশ বাতিল করতে। কিন্তু কাজ হলো না। চিফ সেক্রেটারি আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললাম, ‘দেখুন, জাতীয় সংসদ (ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) নির্বাচনের আর মাত্র মাস চারেক বাকি। মহকুমা প্রশাসক হিসেবে আমাকেই ওই সময় সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। মন্ডি বাহাউদ্দিনের মতো আয়তনে বড় এবং ক্রিমিনাল একটি এলাকায় এই অল্প সময়ের মধ্যে সবকিছু জেনেশুনে গুছিয়ে উঠে নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করা তো খুবই দুরূহ হবে। মেহেরবানি করে আমার বদলির আদেশটা বাতিল করে দিন।’ তিনি শুনলেন, কিন্তু কাজ হলো না। আমার নিবেদনের জবাবে তিনি বললেন, তুমি যাও। আমার বিশ্বাস তুমি পারবে। তুমি পারবে বলেই তোমাকে আমি সিলেক্ট করেছি। আর আমি তো আছি। তোমার যেকোনো প্রয়োজনে আমাকে সরাসরি জানাতে পারো। ফলে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি একদিন লাহোর থেকে প্রায় এক শ মাইল উত্তরে মন্ডি বাহাউদ্দিন গিয়ে নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করলাম।
আমার জেলা শহর এবার মন্ডি বাহাউদ্দিন থেকে ৫০ মাইল দূরের গুজরাত। দু-চার দিনের মধ্যেই জানতে পারলাম, আমি, আমার স্ত্রী ও আমাদের দুই শিশুসন্তান ব্যতীত আশপাশে শ-সোয়া শ মাইলের মধ্যে কোনো বঙ্গসন্তান নেই। আমার প্রাচীরঘেরা মোটামুটি সুদৃশ্য একতলা বাসস্থানটির মালিক ছিল স্থানীয় পৌরসভা। উর্দুতে পৌরসভাকে বলে বলিদয়া। মহকুমা প্রশাসক হিসেবে আমার অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল বলিদয়ার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব। সেই সুবাদে ওই বাড়ি ও একটি প্রায় নতুন জিপগাড়ি পাওয়া গেল। এ ছাড়া একজন বাবুর্চি ও বর্শাহাতের একজন নৈশপ্রহরী ছিল ফাউ।
যেহেতু ডিসেম্বর ’৭০-এ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, তাই আমার প্রথম দায়িত্ব হলো মহকুমাটি ও তার লোকজনকে জানা। সেই উদ্দেশ্যে আমি দ্রুত শুরু করলাম ব্যাপক সফর।
সবই ঠিক ছিল, শুধু দুশ্চিন্তা ছিল আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন ও পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে। তখন পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যে টেলিযোগাযোগব্যবস্থাও ছিল অনুন্নত। চিঠিপত্রও সময়মতো পাওয়া যেত না। আমার সহকর্মী ও ব্যাচমেট সফিউর রহমান তখন পাঞ্জাব সচিবালয়ে সেকশন অফিসার। আখতার আলী ভাইও মুলতান থেকে লাহোরে এসে পাঞ্জাব সচিবালয়ে উপসচিব হিসেবে যোগ দিয়েছেন। তাঁর ভাই শওকত আলী, আমার ব্যাচমেট, আমার পাশের মহকুমা পিন্ড দাদন খান থেকে বদলি হয়ে লাহোরে মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফিসে যোগ দিয়েছে। বাংলাদেশের খবর যেটুকু পেতাম এদের মাধ্যমেই। আর ছিল রেডিও। মন্ডিতে সেটাও সব সময় ধরা যেত না। তবু আমি রোজ সকালে অফিসে যাওয়ার আগে রেডিওতে ঢাকা স্টেশন ধরে দেশের খবর জানার চেষ্টা করতাম।
এদিকে ১৯৭০-এর ৭ ডিসেম্বর পূর্ব-পশ্চিম দুই পাকিস্তানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল। পাকিস্তানের দুই অংশেই সুষ্ঠু সুন্দর অবাধ নির্বাচন হলো। মন্ডি বাহাউদ্দিনেও খুবই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট হয়ে গেল। অন্যান্য প্রায় সব এলাকার মতো এখানেও সরকারি দল কনভেনশন মুসলিম লীগ পরাজিত হলো, জয়লাভ করল জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)। তবে সবকিছু ছাপিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ভূমিধস বিজয় দেশব্যাপী আলাপ-আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। মন্ডিতে আমার সহকর্মী ও নেতাফেতারা দেখা হলেই আমাকে অভিনন্দন জানাতে শুরু করল : ‘মুবারক হো জনাব। শেখ মুজিব সাব তো আব পাকিস্তান কা উজিরে আজম বন জায়েঙ্গে। উসমে কোই শক্ (সন্দেহ) নেহি।’ এসব কথা তারা বলত হাসিমুখেই। তবে আমি বুঝতাম, এ যেন জ্বর সারানোর সে যুগের তেতো কুইনাইন ট্যাবলেটের মতো, ঠেকায় পড়ে খেতে হচ্ছে তাই খাচ্ছি!
এদিকে ডিসেম্বর মাসের পহেলা ভাগে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর ডিসেম্বর গেল, জানুয়ারি গেল, ফেব্রুয়ারি গেল, তবু ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন বসে না। মিলিটারি শাসক জেনারেল এহিয়া খান মনে হচ্ছিল নানা ছুতায় গদি আঁকড়ে বসে থাকতে চান। আর জুলফিকার আলী ভুট্টোরও খায়েশ রাষ্ট্রক্ষমতায় ভাগ বসাতে। তাঁর দল পিপিপি সংসদে আওয়ামী লীগের মতো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় দল হিসেবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক দাবি তুলে শেখ মুজিবের সঙ্গে যৌথভাবে সরকার গঠন করতে চায়। আওয়ামী লীগ তা মানবে কেন? ফলে শুরু হয়ে গেল আন্দোলন। এহিয়া খান জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসার জন্য দু-একবার তারিখ ঘোষণা করেও কথা রাখলেন না। এই প্রেক্ষাপটে মার্চ একাত্তরে শেখ মুজিব ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলনের। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিব লাখ লাখ মানুষের সমাবেশে ঘোষণা দিলেন : ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।’ ব্যস, এরপর আর লড়াই শুরু হতে বাকি রইল না। মার্চ মাসের ২৫ তারিখ রাতে পাক বাহিনী ঢাকায় এক অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করল রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পিলখানা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলের সদর দপ্তর এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে। এক রাতেই শহীদ হলো কয়েক শ বাঙালি ছাত্র, পুলিশ ও ইপিআর সদস্য।
পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানরত আমরা বাঙালিরা এই নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে কিছুই জানতে পারলাম না। ২৬ মার্চ সকালে মন্ডি বাহাউদ্দিনে অফিসে যাওয়ার আগে আমি প্রতিদিনের মতো আমার মারফি ট্রানজিস্টারটি খুললাম ঢাকা রেডিওর খবর জানতে। কিন্তু ঢাকা স্টেশন কিছুতেই ধরা গেল না। অনেক চেষ্টা করে এক জায়গায় ক্ষীণকণ্ঠের আওয়াজ শোনা গেল : ‘...মার্শাল ল হুকুম নম্বর...’ ইত্যাদি। ঘোষক সামরিক আইন পড়ে শোনাচ্ছেন। বোঝা গেল, ঢাকা তথা পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হয়েছে। কিন্তু কেন? আগের দিনও তো রেডিওতে মোটামুটি স্বাভাবিক প্রোগ্রাম হচ্ছিল মার্শাল ল জারির মতো কিছু ঘটেছে বলে তো মনে হলো না। তাহলে? অন্যমনস্কভাবে নাশতা খাচ্ছি আর সাত-পাঁচ ভাবছি।
আমাকে গম্ভীর ও চিন্তান্বিত দেখে আমার স্ত্রী জানতে চাইলেন কী হয়েছে। জবাবে আমি শুধু বললাম, ঢাকার অবস্থা বোধ হয় ভালো না। ওখানে মার্শাল ল জারি হয়েছে। শুনে তিনিও চুপসে গেলেন। ভারি চিন্তায় পড়লাম। কী করা যায়। অগত্যা লাহোরে ফোন করলাম সফিউরের কাছে। সফিউর রহমান কনফার্ম করল, পূর্ব পাকিস্তানে মার্শাল ল জারি হয়েছে। পঁচিশে মার্চ রাতে ঢাকায় আর্মির অ্যাকশনে বহু লোক মারা গেছে। এর বেশি কোনো কিছু জানাতে পারল না আমার বন্ধু। শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, দুশ্চিন্তা গেল বেড়ে।
এদিকে স্থানীয় অফিসার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যারা আগে দেখা হলেই ‘মুবারক হো জনাব’ সম্ভাষণ জানিয়ে পাকিস্তানে এবার বাঙালিরা মন্ত্রী-প্রধানমন্ত্রী হবে বলে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করত, তারা দেখলাম কেমন যেন চুপ মেরে গেছে। তাদের আবদার : শেখ মুজিব সাহেব ভুট্টো সাহেবের প্রস্তাব মেনে একটা কোয়ালিশন সরকার গঠন করলেই পারেন। তাতে সবাই মিলেমিশে দেশের কাজ করতে পারবে। জবাবে আমি যা বলতাম তা হচ্ছে, শেখ মুজিবের কী এত ঠেকা পড়েছে যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েও অন্য কারো সাহায্য নিয়ে সরকার গঠন করতে হবে। বরং সংসদে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকলে সেটাই রাষ্ট্র পরিচালনায় অধিকতর সহায়ক হবে। আমার জবাবে পাকিস্তানিরা কেউই খুশি হতো না। মুখ বেজার করে চলে যেত তারা।
আমার এক তরুণ সহকর্মী ওই মহকুমার ইলেকশন অফিসার, আমার খুব ভক্ত ছিল। সে একদিন আমাকে জানাল, আমার মন্তব্যে নাকি পাঞ্জারিরা খুবই নাখোশ। এটা নিয়ে তারা কানাঘুষা করছে। অতএব, আমি যেন একটু সতর্ক হই কথাবার্তায়। ওই অফিসারটির কাছে তথ্য পেয়ে বাধ্য হয়ে আমি রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনা বন্ধ করে দিলাম। টেলিফোনেও সহকর্মী সফিউর বা শওকতের সঙ্গে আগের মতো উচ্ছ্বাস থাকল না। এমনকি ঢাকার পরিস্থিতি নিয়ে কথাবার্তাও কমাতে হলো। পূর্ব পাকিস্তানেও কী হচ্ছে জানি না, আব্বা-আম্মা, শ্বশুর-শাশুড়ি, ভাই-বোন কারো কোনো খবর পাচ্ছি না মাসের পর মাস, নিশ্চয়ই তাঁরাও আমাদের জন্য দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।
এই পরিস্থিতিতে একদিন লাহোর থেকে ফোন পেলাম সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস মুজিবুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে। তিনি কোর্টের লাহোর অধিবেশনে যোগ দিতে ঢাকা থেকে লাহোর এসেছেন। জাস্টিস সাহেব ঢাকায় আমার শ্বশুরের প্রতিবেশী। তিনি জানালেন আমার শ্বশুর সাহেব নাকি একটি চিঠি দিয়েছেন তাঁর কাছে, আমাকে পৌঁছানোর জন্য। তিনি ওটা ডাকে পাঠানো ঠিক হবে না বলে জানালেন। কারণ চিঠিপত্র নাকি আজকাল ডাক বিভাগ খুলে সেন্সর করে। অতএব, আমি যদি লাহোর যাই তাহলে চিঠিটি পাব। পরে চিঠিটা সংগ্রহ করেছিলাম লাহোর গিয়ে। ওতে সবচেয়ে বড় দুঃসংবাদ ছিল আমার ভায়রা ভাই ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যাপক আব্দুল হালিম খানের পাক বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হওয়ার কথা।
এদিকে আখতার আলী ভাইদের পুরো ব্যাচ (১৯৬৫ ব্যাচ) ফিরে যাচ্ছে ঢাকায়। আখতার ভাইকে লাহোর রেলস্টেশনে বিদায় জানাতে ও বাঙালি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে আমি লাহোর যাব ঠিক করলাম। তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শুধু করাচি-ঢাকা ফ্লাইট চালু ছিল, তা-ও যেতে হতো শ্রীলঙ্কার আকাশপথে। আখতার ভাইরা লাহোর থেকে তাই ট্রেনে যাবেন করাচি, সেখান থেকে ঢাকার ফ্লাইট।
আমি বউ-বাচ্চা নিয়ে আমার সেকেন্ড হ্যান্ড ভোকস্ওয়াগন চালিয়ে যথাসময়ে হাজির হলাম লাহোর। সেখানে রাত্রিবাস সফিউরের বাসায়। পরদিন লাহোর রেলস্টেশনে দুপুরে আখতার ভাইদের বিদায় জানাতে গিয়ে মনটা হু হু করে উঠল। হায়, আমরা কি আর দেশে ফিরে যতে পারব! যা হোক, ওই দিনই বিকেলে রওনা হয়ে গেলাম মন্ডি বাহাউদ্দিন। আবার প্রায় সোয়া শ মাইলের ড্রাইভ। মন্ডি পৌঁছতে পৌঁছতে রাত হয়ে গেল।
বাসায় বারান্দা পার হতে না হতে বাবুর্চি বশীর খবর দিল, লাহোর থেকে সফিউর রহমান নাকি কয়েকবার ফোন করেছে। জরুরি আলাপ। আমি যেন তক্ষুনি ফোন করি। করলাম। সফিউরের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর : ‘মোফাজ্জল করিম, কনগ্র্যাচুলেশন। গাঠরি-বোঁচকা বাঁধেন। ইসলামাবাদ থেকে অর্ডার এসেছে, আমাদের ব্যাচের যে সাতজন আগে এসেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, তাদের সবাইকে ঢাকা বদলি করা হয়েছে।’ শুনে আমি ও আমার স্ত্রী চিৎকার দিয়ে লাফাতে শুরু করলাম। সারা রাত কাটল আমাদের হৈচৈ ও চিৎকারে। পারলে রাত পোহালেই রওনা হয়ে যাই আমরা। আমি ফোনে গুজরাতে আমার ডিসিকে খবরটা দিলাম। ডিসি ক্যাপ্টেন (অব.) নাসির আহমেদ ১৯৬৩ ব্যাচের অত্যন্ত ভদ্র ও সজ্জন একজন অফিসার ছিলেন। তিনি শুনে খুশি হলেন। ‘তুমি চলে গেলে ক্ষতিটা হবে আমার। তবু তোমাকে যেতে হবে, যাও। গড ব্লেস ইউ’, বললেন বস নাসির সাহেব।
তবে আমার বদলির সংবাদে মন্ডি বাহাউদ্দিনে দেখলাম আমার কর্মকর্তা-কর্মচারী সবাই দুঃখিত। দুঃখিত পৌরসভার কাউন্সিলররাও। দৃশ্যত সবচেয়ে শোকাহত মনে হলো পৌরসভার আমার সেক্রেটারি গোলাম হোসেন খানকে। এই অত্যন্ত সৎ, দক্ষ ও ধার্মিক লোকটি ছিলেন আমার প্রতিবেশী। অফিসের কাজকর্ম নিয়ে রোজ রাত ৮টা-৯টায় আমি তাঁর সঙ্গে বসতাম আমার বাসায়। আমার মেয়ে দুই-আড়াই বছরের কান্তাকে কোলে বসিয়ে গল্প শোনাতেন তিনি। আমার নিরাপত্তা নিয়ে আমার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন খানসাহেব। রাতে শুধু বর্শাহাতে পাহারাদার এনায়েতকে আমার নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট মনে করতেন না তিনি। অনেকবারই বলেছেন ডিসি-এসপিকে বলে পুলিশি পাহারার ব্যবস্থা করতে। আমি রাজি হইনি।
আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে আমি মন্ডি বাহাউদ্দিনের মতো নির্বান্ধব একটি জায়গায় আমার ছোটখাটো একটি অস্ত্রোপচার করালাম ওখানকার হাসপাতালে। সার্জন ছিলেন ডা. রশীদ নামক এক ভদ্রলোক। তিনি বললেন, ‘স্যার, আপনি চাইলে লাহোর গিয়েও আপনার কটিদেশের এই টিউমারটি কাটাতে পারেন। তবে দেরি করবেন না।’ তখন মে মাস। তখনো ঢাকায় বদলির ব্যাপারে কিছুই জানি না। আমি নির্দ্বিধায় ডা. রশীদকে বললাম, না, আপনিই করবেন অপারেশন। একদিন দুপুরে একাই গিয়ে হাজির হলাম মন্ডির সিভিল হসপিটালে।
অপারেশনের কথায় মনে পড়ল ওই সময় আমাদের পরিবারে একটি বড় দুর্ঘটনা থেকে আমার একমাত্র ছেলে পাঁচ বছরের মিতুলের বেঁচে যাওয়ার কথা। মিতুলকে তখন ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম বাসার কাছের মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারিতে। উর্দু মিডিয়াম ওই স্কুলই ওর জীবনের প্রথম স্কুল। বাসায় প্রায় সারাক্ষণ সে তার খেলনা সাইকেলটি চালাত প্রশস্ত বারান্দায়। একদিন দুপুরে আমি অফিস থেকে বাসায় এসেছি খেতে। ড্রাইভার মোহাম্মদ হোসেন আমাকে নামিয়ে দিয়ে প্রায় নতুন টয়োটা জিপটি ‘ব্যাক’ করে নিয়ে যাচ্ছিল গাড়ি বারান্দা থেকে গ্যারেজের দিকে। এরই মধ্যে মিতুল যে কোন ফাঁকে জিপের পেছনে ওঠার চেষ্টা করছিল তা মোহাম্মদ হোসেন লক্ষ করেনি। জিপের মৃদু ঝাঁকুনিতে মিতুল ছিটকে পড়ে গিয়ে চিৎকার দিয়ে ওঠে। ভাগ্যিস, তার চিৎকারধ্বনি মোহাম্মদ হোসেন শুনতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে হার্ড ব্রেক করে গাড়ি থামায়। ফলে মিতুলের এক পায়ের হাঁটু চাকার নিচে যায়নি বটে, তবে ওটাতে প্রচণ্ড ব্যথা পায় সে। আমার অগ্রজ ডা. তফজ্জুল করিম তখন পার্শ্ববর্তী ঝিলাম ক্যান্টনমেন্টের হাসপাতালে কর্মরত। সেখানে একাই থাকেন তিনি। আমি মিতুলকে নিয়ে সোজা চলে গেলাম তাঁর কাছে। পরে প্রায় দুই সপ্তাহ সকাল ৭টায় আমি নিজে আমার ভোকস্ওয়াগন চালিয়ে মিতুলকে নিয়ে যেতাম ঝিলাম। সেবার অলৌকিকভাবে রক্ষা পায় মিতুলের পা।
মার্চের পর একাত্তরের দিনগুলো মন্ডিতে কাটত শুধু দুশ্চিন্তায়। সবচেয়ে খারাপ লাগত কারো সঙ্গে কোনো কিছু শেয়ার করতে না পেরে। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে তখন যুদ্ধ চলছে, মরছে লাখ লাখ মানুষ। খানসেনাদের অনেকের বাড়ি ছিল ঝিলাম ও গুজরাত এলাকায়। এ দুই জেলাই ছিল সৈনিক সরবরাহকারী জেলা হিসেবে পরিচিত। পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায়ই যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের লাশ আসত এ দুই জেলায়। তখন মন্ডি ও গুজরাতের মানুষদের মধ্যে দেখা দিত চাপা উত্তেজনা। অনেকে যুদ্ধের খবর, সৈনিকদের মৃত্যুসংবাদ ইত্যাদি নিয়ে অফিসে আলাপ-আলোচনা করত আর বাঁকা চোখে তাকাত আমার দিকে। আমি মুখে কুলুপ এঁটে নথিপত্রে মনোযোগ দেওয়ার ভান করতাম।
এর মধ্যে একদিন আমি নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছিলাম বলা যায়। এত কিছুর মধ্যেও বিকেলে রোজ টেনিস খেলতে যেতাম মাইল দেড়েক দূরের ওয়াপদা কলোনিতে। ওখানে কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন খেলার সাথি। ইয়াকুব খান নামের একজন নির্বাহী প্রকৌশলী তো আমাদের পারিবারিক বন্ধুই হয়ে গিয়েছিলেন। তা, একদিন টেনিস খেলে ঘর্মাক্ত শরীরে গাড়ি চালিয়ে বাসায় ফিরছিলাম। মূল শহরে ঢোকার মুখে একটা রেলগেট ছিল। ওটা খোলাই ছিল। আমি গেট পার হওয়ার বোধ হয় এক সেকেন্ড পরই হুশহুশ করে একটা ট্রেন পার হলো। অর্থাৎ আর এক সেকেন্ড আগে হলেই...। আমি গাড়ি থেকে নেমে হাঁকডাক দিতেই গেটম্যান এসে হাজির। আমি আচ্ছাসে বকাঝকা দিলাম তাকে উর্দু-পাঞ্জাবি ভাষা মিলিয়ে। তাকে দুটো কিল-চড় মারতে গিয়েও কী মনে করে থেমে গেলাম। ভাগ্যিস। তা না হলে আশপাশের জনগণ গেটম্যান নয়, এই বাঙালি সাহেবকেই ধোলাই দিত। লক্ষ করলাম, আমার বকাঝকা শুনে পাবলিক জড়ো হয়ে গেছে গেটম্যানের পক্ষে।
তবে আরেক দিনের একটা ঘটনা বাঙালি-পাঞ্জাবি সব মহলে মন্ডিতে-লাহোরে খুব আলোচিত হয়েছিল। সেদিনও আমি টেনিস খেলে সন্ধ্যা ৭টার দিকে বাসায় ফিরেছি ক্লান্ত হয়ে। বাসায় এসে শুনলাম গুজরাত থেকে আমার বস ক্যাপ্টেন নাসির সাহেব কয়েকবার ফোন করেছিলেন কী একটা জরুরি বিষয়ে। আমি তাঁকে ফোন করতেই নাসির সাহেব সেদিন খুব বিরক্তির সঙ্গে বললেন, ‘কোথায় থাকো তুমি, তোমাকে ফোন করে পাওয়া যায় না। এদিকে তোমার এলাকার রুক্কনে স্কুলের ছেলেরা তো পরীক্ষার হলে গার্ডদের পিটিয়ে মেরে ফেলতে গিয়েছিল। তিন-চারজন শিক্ষককে তোমার মন্ডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজন তো বাঁচে কি না সন্দেহ।’ আমি জানতে চাইলাম ছাত্ররা কেন মারল শিক্ষকদের। ‘কেন আবার, শিক্ষকরা তাদের পরীক্ষায় নকল করতে দিতে চাননি তাই।’
সিভিল সার্ভিসে আসার আগে আমি প্রায় সাড়ে তিন বছর কলেজে শিক্ষকতা করেছি। আমি শিক্ষক হব—এটাই ছিল ছোটবেলা থেকে আমার জীবনের লক্ষ্য। শিক্ষকদের জন্য আমার ভালোবাসা এবং তাঁদের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল নিখাদ। ডিসি সাহেবের কাছ থেকে খবরটা শুনেই আমি ছুটলাম হাসপাতালে। গিয়ে দেখি, সত্যি চার-পাঁচজন শিক্ষক মাথায়-হাতে-পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছেন।
মন্ডি বাহাউদ্দিনে পুলিশের বড়কর্তা বলতে ছিলেন একজন ইন্সপেক্টর। তাঁকে আমি খবর দিয়ে এনেছিলাম হাসপাতালে। ‘আপনি কাল ভোরেই ফোর্স নিয়ে চলে যান ওই এলাকায়। গিয়ে সবগুলো বদমাশকে পাকড়াও করেন। ব্যাটাদের জেলের ভাত খাওয়ান কিছুদিন।’ আমি তাঁকে নির্দেশ দিয়ে ফিরে গেলাম বাসায়।
সে রাতে দুশ্চিন্তায় ভালো করে ঘুমাতে পারলাম না। সকালে ৯টার দিকে পৌরসভার টয়োটা জিপগাড়ি নিয়ে রওনা হলাম ওই স্কুলের উদ্দেশে। সঙ্গে শুধু ড্রাইভার ওয়ালি মোহাম্মদ। তবে চালক সে নয়, আমি।
একসময় পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। দূর থেকে চোখে পড়ল স্কুলের বেশ বড়সড় দোতলা ভবনটি। তারই একটার নিচে দেখলাম চেয়ারে সপারিষদ বসে আছেন আমাদের ইন্সপেক্টর সাহেব। আমাকে দেখে হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট ঠুকলেন তিনি। ‘কই, ইন্সপেক্টর সাহেব, আপনার আসামিরা কোথায়?’ জানতে চাইলাম আমি। ‘স্যার, কেউ তো কিছু স্বীকার করছে না। এদিকে আজকের পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেছে। ছেলেরা সবাই হলে ঢুকে পড়েছে।’ শুনে আমার মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। আমি জানতে চাইলাম এই এলাকার লম্বরদারের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন কি না। ‘না, স্যার। ওকে খবর দিয়েছিলাম। ও এখনো আসেনি।’ বুঝলাম পুলিশ ইন্সপেক্টর সাহেব তলে তলে দুই নম্বরি করে ফেলেছেন।
লম্বরদার হচ্ছেন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এলাকার ভূমি রাজস্ব আদায়কারী গণ্যমান্য ব্যক্তি। তিনি বেতনভুক কর্মচারী নন। যে পরিমাণ রাজস্ব তিনি আদায় করবেন তার শতকরা পাঁচ ভাগ (পাচোত্রা) তিনি পাবেন। তিনি এলাকার সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। সরকারি সব কাজে সাহায্য-সহযোগিতা তিনি করবেন এটাই দস্তুর। নইলে তাঁর লম্বরদারি চলে যাবে। আমি ডেকে পাঠালাম লম্বরদারকে।
একটু পরেই এলেন লম্বরদার সাহেব। বছর চল্লিশেক বয়স। মাথায় ইয়া বড় এক পাগড়ি। এসেই লম্বা সালাম দিয়ে তাঁর ‘গরিবখানায়’ যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। আমি অসম্মতি জানিয়ে জানতে চাইলাম এই স্কুলে সেদিন কী হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, ওই দিন তিনি গুজরাত গিয়েছিলেন, এখানে কী হয়েছে তিনি জানেন না। যতই জিজ্ঞেস করি তাঁর একটাই জবাব : মেনু কোই পাতা নেহি জনাব (আমি কিছুই জানি না জনাব)। একই উত্তর বারবার শুনে শুনে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। হঠাৎ এক লাফে চেয়ার থেকে উঠে ওই ছ’ফুট লম্বা লোকটাকে দিলাম এক চাঁটি। তার মাথার পাঁচ কেজি ওজনের পাগড়ি ছিটকে পড়ল মাটিতে। আর সে শুধু ‘হুজুর, আর মারবেন না। আমি সব বলছি’ বলে হাতজোড় করে মাপ চাইতে লাগল।
রুক্কনের সেদিনের (জুন ১৯৭১) সেই ঘটনা মনে পড়লে এখনো আমার হাত-পা কাঁপে। কোথা থেকে যে এমন রাগ চড়ল মাথায়, আর ওই আড়াই মণ ওজনের লোকটাকে কী করে এত লোকের সামনে কষে থাপ্পড় লাগালাম সে যেন আজও আমার কাছে এক রহস্য।
এখন মনে হয় প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে সর্বাগ্রে যা দরকার তা হলো ন্যায়নীতি, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিজের একটা স্ফটিকস্বচ্ছ বিবেক। এখনকার আমার তরুণ সহকর্মীদের এই মেসেজটি আমি সব সময় দিয়ে থাকি। একাত্তরের সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে নির্বান্ধব পাঞ্জাবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে, সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশে আটকে পড়া দিনগুলোতে এটাই ছিল আমার মূল চালিকাশক্তি। তবে সর্বোপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ার ওপর আস্থা তো ছিলই। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেই আস্থা যেন বজায় থাকে সেটাই প্রার্থনা।


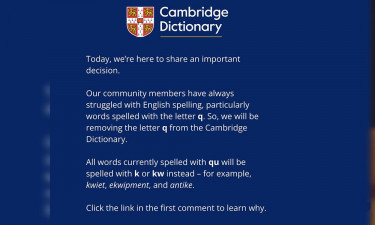




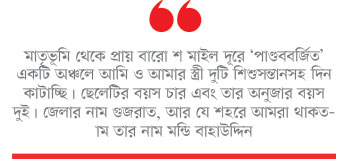 নভেম্বর
নভেম্বর 
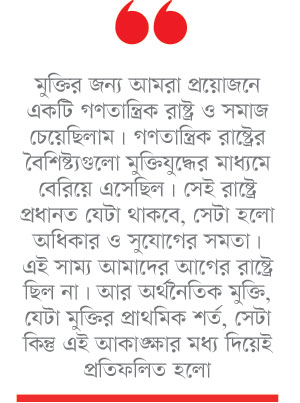 অথচ সেই আকাঙ্ক্ষা একেবারেই পূর্ণ হয়নি। ভৌগোলিকভাবে আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র, সংবিধান, রাষ্ট্রভাষা পেলাম, পরিচয় পেলাম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে। পাকিস্তান একটা অস্বাভাবিক রাষ্ট্র ছিল। ওই রাষ্ট্র ভাঙতই। এবং সেটা শুধু ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই নয়, ভাঙত বৈষম্যের কারণে। ভৌগোলিক দূরত্ব ওই বৈষম্যই বৃদ্ধি করছিল। আশা ছিল, বাংলাদেশে আঞ্চলিক বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্যের জায়গায় আমরা বাংলাদেশে পেলাম শ্রেণিগত বৈষম্য। শ্রেণিগত বৈষম্যটা ক্রমাগত বাড়ছে। অধিকার ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা না করে রাষ্ট্র উল্টো দিকে যাচ্ছে। ক্রমাগত বৈষম্য বাড়াচ্ছে।
অথচ সেই আকাঙ্ক্ষা একেবারেই পূর্ণ হয়নি। ভৌগোলিকভাবে আমরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র, সংবিধান, রাষ্ট্রভাষা পেলাম, পরিচয় পেলাম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে। পাকিস্তান একটা অস্বাভাবিক রাষ্ট্র ছিল। ওই রাষ্ট্র ভাঙতই। এবং সেটা শুধু ভৌগোলিক দূরত্বের কারণেই নয়, ভাঙত বৈষম্যের কারণে। ভৌগোলিক দূরত্ব ওই বৈষম্যই বৃদ্ধি করছিল। আশা ছিল, বাংলাদেশে আঞ্চলিক বৈষম্য থাকবে না। কিন্তু আঞ্চলিক বৈষম্যের জায়গায় আমরা বাংলাদেশে পেলাম শ্রেণিগত বৈষম্য। শ্রেণিগত বৈষম্যটা ক্রমাগত বাড়ছে। অধিকার ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা না করে রাষ্ট্র উল্টো দিকে যাচ্ছে। ক্রমাগত বৈষম্য বাড়াচ্ছে।