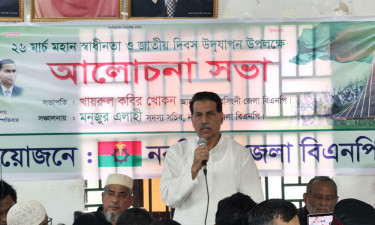একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল পুরোপুরি একটি জনযুদ্ধ। এ যুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে নানাভাবে অংশ নিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ। তবে এমন সাধারণ মানুষ হতেও প্রয়োজন অসাধারণ গুণাবলি। মুক্তিযোদ্ধাদের ভাষ্যে উঠে আসা একাত্তরের এমন কিছু অসাধারণ মানুষের সাহসের ইতিহাস তুলে ধরতেই এ লেখার অবতারণা।
মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ
- সালেক খোকন

মুক্তিযুদ্ধ তখন চলছে। একবার নির্দেশ আসে বড়লেখায় সাতমাছড়া সেতু উড়িয়ে দেওয়ার। আমার সঙ্গে ১৩ জন। ক্যাম্প থেকে মুভ করি রাতে।
মনের ভেতর এখনো ভেসে ওঠে ওই মেয়েটির মুখখানা। গ্রামবাসীর চোখ এড়িয়ে, জীবনের ঝুঁকি জেনেও ওই রাতে সে এসেছিল শুধুই মুক্তিযোদ্ধাদের পার করিয়ে দিতে। এর চেয়ে বড় যুদ্ধ আর কী হতে পারে!
একাত্তরের ইতিহাসের ভেতরের এমন একটি ঘটনা তুলে ধরেন যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আহম্মদ বাবু। তিনি যুদ্ধ করেছেন ৪ নম্বর সেক্টরে, কুকিতল ক্যাম্পের কমান্ডারও ছিলেন।
কুকিতল ক্যাম্পেরই আরেক মুক্তিযোদ্ধা নূর উদ্দিন আহমেদ (বীরপ্রতীক) একাত্তরের অজানা একটি ঘটনা। তার ভাষায়, “লাঠিটিলা বর্ডারে ছিল পাকিস্তানি আর্মিদের একটা ক্যাম্প। ওখানে আক্রমণ চালাতে হবে। রেকি করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকে। গোপনে ওই এলাকায় গিয়ে লোক মারফত নানা তথ্য নিয়ে রেকি করি। এভাবেই ঠিক করা হয় টার্গেট। রাতে পজিশন নিয়ে আমরা ভোরে আক্রমণ করি।
ওই অপারেশনে দুজন পাকিস্তানি আর্মি রাস্তা ভুলে চা-বাগানের এক কুলিকে বলে, ‘আমাদের জুড়ি ক্যাম্পে নিয়ে যাও।’ তখন ওই কুলি কৌশলে তাদের ইন্ডিয়ার ভেতরে নিয়ে আসে। খবর পেয়ে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করে আমরা ওদের ‘হ্যান্ডস আপ’ করাই।
এ সফলতায় বিশাল অবদান ছিল ওই বাঙালি কুলির। পাকিস্তানি আর্মির হাতে অস্ত্র। জীবন যাওয়ার ভয়ও ছিল। তবু তাদের ভুল পথে নিয়ে আসছে। এভাবে সাধারণ মানুষ আমাদের সহযোগিতা করেছে। ফলে স্বাধীনতা আনাও সহজ হয়েছে।”
তার ভাষায়, ‘আগস্ট মাসের ঘটনা। নীলফামারীর ডিমলায় টুনিরহাট নামক একটি জায়গায় ছিল পাকিস্তানি সেনাদের ক্যাম্প। ওরা ছিল এক প্লাটুন, ত্রিশজনের মতো। একটি বাড়ির একতলার ওপরে পজিশন নিয়ে থাকত। তাদের সঙ্গে পাহারায় ছিল রাজাকাররা।
আমদের কম্পানি তখন ঠাকুরগঞ্জ নামক জায়গায়। কম্পানি কমান্ডার অপিল, আমি ছিলাম সেকশন কমান্ডার। অপারেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয় আমাকেই।
টার্গেট ছিল ওদের ওপর আক্রমণ করেই ফিরে আসব। সন্ধ্যায় ক্যাম্পে আসে ওই গ্রামেরই নবম শ্রেণি পড়ুয়া এক ছেলে। নাম রফিকুল্লাহ। সে এসে বলে, আপনারা কি মুক্তিযোদ্ধা? প্রশ্ন শুনে একটু অবাক হই। ভাবলাম পাকিস্তানিদের দালাল। বললাম, তোমার জানার দরকার কী? তার অকপট উত্তর, ‘মুক্তিযোদ্ধা হলে সাহায্য করব। ক্যাম্পে ওরা কয়জন আছে, কোন দিক দিয়ে যেতে হবে—সব আমার জানা। আমি নিয়ে যেতে পারব।’ মৌখিক যাচাই করে তাকে আমরা গাইড হিসেবে সঙ্গে নিলাম।
ও সামনে, আমরা পেছনে। আকাশে বেশ মেঘ জমেছে। হঠাৎ পাকিস্তানিরা টের পেয়ে যায়। ওদের পজিশন খানিক উঁচুতে হওয়ায় সামনে থাকা রফিকুল্লাহকে তারা দেখে ফেলে। ফলে গুলি চালায়। গুলিটি রফিকুল্লাহর বুকে এসে লাগে। মাটিতে পরেই যন্ত্রণায় সে কাতরাচ্ছে। সমতল ভূমি। ধান কাটাও শেষ। পজিশন নেওয়ারও সুযোগ নেই। সঙ্গে ছিল না তেমন অ্যামুনেশনও। আমরা তাই নীরব থাকি।
কিন্তু ছটফট করতে করতে রফিকুল্লাহ বলে, ‘ওদের আপনারা ছেড়ে দিয়েন না। আক্রমণ করেন। ওদেরও গুলি করে মারেন ভাই।’ এর পরই তার দেহ নিথর হয়ে যায়।
ওর কথাগুলো এখনো কানে বাজে। তার কথা রাখতে পারিনি ওই দিন। এটা ভাবলেই কষ্ট হয়। রফিকুল্লাহও ছিল একজন বীর যোদ্ধা। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতায় তার রক্তও মিলে আছে।’
কথা হয় আরেক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু মোহাম্মদ সরওয়ার হোসাইন চৌধুরী। তার বাড়ি চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে। একাত্তরে ফটিকছড়ির যোগ্যাছোলায় এক অপারেশনে পাকিস্তানি সেনাদের মর্টারের স্প্লিন্টারে আহত হওয়ার পর ফিরে আসেন ক্যাম্পে। কী দেখলেন এসে? তিনি বললেন যেভাবে, “দেখি খাবার রেডি, গরম গরম ভাত। যুদ্ধের সময়ও এসব নিয়ে এলো কে? স্থানীয় এক মাদরাসার হুজুরের বউ। তাকে ডেকে সবাই বলে, জীবন বাঁচাতে এলাকার সবাই চলে গেছে, আপনি যাননি কেন? উনি বলেন, ‘বাবা, কোথায় যামু, আমার ছেলেরা যুদ্ধে গেছে, মা হয়ে আমি কি পালায়া যাইতে পারি?” এ ঘটনা বলতে বলতে কাঁদতে থাকেন এই মুক্তিযোদ্ধা। বলেন, ‘এটাও একটা বড় যুদ্ধ, যা করেছিল সাধারণ মানুষ। একাত্তরে ওই নারীর অবদানও কিন্তু কম ছিল না।’
আরেকটি ঘটনার কথা তুলে ধরেন সরওয়ার। তার ভাষায়, ‘রাঙামাটি এলাকায় এক বুড়ির বাড়িতে আমরা উঠি। উনি মুক্তিযোদ্ধাদের জন্যই বাড়িতে পানি রাখতেন। শীতের দিন। আমার প্রচণ্ড জ্বর ছিল। জোর করে ওই বুড়ি একটি কাঁথা দিয়ে দেন। নিতে চাই না প্রথম। নেওয়ার নিয়মও নেই। কিন্তু বুড়িটি আধাকিলোমিটার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে কাঁথাটি শরীরে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। তিনিও তো একজন মুক্তিযোদ্ধা। ওটাও তো দেশপ্রেম ছিল। কিন্তু ইতিহাসে কি ওই বুড়ির নাম লেখা হয়েছে?’
একাত্তরে সাধারণ মানুষের অবদান বিষয়ে ঢাকার গেরিলা বীরমুক্তিযোদ্ধা তৌফিকুর রহমান অকপটে বলেন, ‘একটি দেশে গেরিলা তখনই থাকতে পারে, যখন সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যায়। জনগণের সমর্থন ছাড়া গেরিলা অপারেশনও হয় না। সেই সমর্থন আমরা শতভাগ পেয়েছিলাম। এ কারণেই একাত্তরের যুদ্ধটি ছিল একটি জনযুদ্ধ, যেটি না বললে কিন্তু ভুল হবে। আমি গেরিলা, পথে আমাকে গ্রামবাসী খাইয়েছে। প্রতিটি ধাপে এরাই আমাদের হেল্প করেছে। ’
উদাহরণ টেনে তিনি আরো বলেন, ‘সাভারের শিমুলিয়া ইউনিয়নের গাজীবাড়ি গ্রামে স্থানীয় যুবকদের ট্রেনিং করাই আমরা। এসএলআরের ওপর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। শিমুলিয়ার তৎকালীন চেয়ারম্যান আহম্মেদ আলী সব সময় খোঁজ নিতেন কোনো অসুবিধা হচ্ছে কি না। কোন বাড়িতে গিয়ে আমরা থাকতে পারব। ঈদে একটু ভালো খেতে পারব। সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। একাত্তরে এমন মানুষদের কন্ট্রিবিউশনও কম ছিল না।’
মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের সহযোগিতার কথা আমরা ভুলে গেছি বলে মনে করেন চিলাহাটী সাব-সেক্টরের কমান্ডার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশীদ। অকপটে তিনি বলেন, ‘যারা সৈনিক বা মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, আমাদের পাকিস্তানি সেনারা অ্যাটাক করলে ইন্ডিয়াতে সরে যেতে পারতাম। কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা গ্রাম বা শহরে ছিল, তারা কোথায় যাবে? তারাই সরাসরি ওদের অত্যাচার ফেস করেছে। গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা আসছে এই অপরাধে গ্রামের বাড়িগুলো পাকিস্তানি সেনারা জ্বালিয়ে দিত। ৯ মাসে এভাবেই নির্যাতিত ও সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছে সাধারণ মানুষ।’
তিনি আরো বলেন, ‘পাকিস্তানি আর্মিরা কোথায় লুকিয়ে আছে, তা আগেই এসে আমাদের বলে যেত সাধারণ মানুষ। কারণ তারা আমাদের সঙ্গে ছিল। পাকিস্তানি আর্মিই বলেছিল, ‘যেদিকে দেখি সেদিকেই শক্র দেখি। উই ক্যান্ট ট্রাস্ট আ সিঙ্গেল বেঙ্গলি।’ শক্তিতে তারা তো কোনো অংশেই কম ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে ছিলেন না। মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অন্যতম কারণ ছিল এটা। তাই একাত্তরে সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল সাধারণ মানুষের। উই মাস্ট স্যালুট দেম। কিন্তু স্বাধীনতার এত বছরেও উই ডোন্ট স্যালুট দ্য পিপল।’
সম্পর্কিত খবর
বাংলা সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ
- তুহিন ওয়াদুদ

বাংলা কবিতায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ। কবিতা যেহেতু শিল্পের অপরাপর শাখা থেকে একেবারেই ভিন্ন, তাই এখানে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে কবিতাঙ্গিক বজায় রেখে। এখানে রূপক, প্রতীক, ইঙ্গিত, ইশারা, উপমার ওপর ভর করে যেমন মুক্তিযুদ্ধ এসেছে, তেমনি কাহিনি হিসেবেও এসেছে অনেকবার।
বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে বেশি এসেছে মুক্তিযুদ্ধ।
ছোটগল্পকারগণ তাদের গল্পের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধকে। আবু জাফর শামসুদ্দীনের ‘চাঁদমারি, শওকত ওসমানের ‘দুই ব্রিগেডিয়ার’, সরদার জয়েনউদ্দীনের ‘বকেসা আলী পণ্ডিত’, আবুবকর সিদ্দিক এর ‘খরা পোড়া শ্রাবণ, জহির রায়হানের ‘সময়ের প্রয়োজনে’, শহীদ আখন্দের ‘একাত্তরের ছিন্নভিন্ন ভালোবাসা’ উল্লেখযোগ্য। হাসান আজিজুল হক, রাহাত খান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সেলিনা হোসন, ইমদাদুল হক মিলন, হরিপদ দত্তসহ খ্যাতিমান কিংবা খ্যাতি নেই এমন গল্পকাররাও ছোটগল্প রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন।
বাংলা উপন্যাসেও গভীরভাবে উঠে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ।
আনোয়ার পাশার ‘রাইফেল রোটি আওরাত’, সৈয়দ শামসুল হকের ‘নিষিদ্ধ লোবান’, ‘বৃষ্টি ও বিদ্রোহীগণ’ সাড়া জাগানো উপন্যাস। শওকত ওসমানের ‘জাহান্নাম হইতে বিদায়’, আনিসুল হকের ‘মা’ মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে লেখা। হুমায়ূন আহমেদের ‘জোছনা ও জননীর গল্প’সহ বেশ কয়েকটি উপন্যাস পাঠকনন্দিত হয়েছে। আহমদ ছফার ‘অলাতচক্র’ মুক্তিযুদ্ধের বাতাবরণে রচিত। সেলিনা হোসেনের ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’, মাহমুদুল হকের ‘জীবন আমার বোন’, শহীদুল জহিরের ‘জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা’ এই ধারার গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস।
মমতাজ উদ্দীন, ইনামুল হক, সৈয়দ শামসুল হক, মামুনুর রশীদ, নিলীমা ইব্রাহীম, সাঈদ আহমেদসহ অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের কাহিনি নিয়ে নাটক রচনা করছেন।
বাংলা কবিতায় বারবার ঘুরেফিরে এসেছে মুক্তিযুদ্ধ। কবিতা যেহেতু শিল্পের অপরাপর শাখা থেকে একেবারেই ভিন্ন, তাই এখানে মুক্তিযুদ্ধ এসেছে কবিতাঙ্গিক বজায় রেখে। এখানে রূপক, প্রতীক, ইঙ্গিত, ইশারা, উপমার ওপর ভর করে যেমন মুক্তিযুদ্ধ এসেছে, তেমনি কাহিনি হিসেবেও এসেছে অনেকবার। একাত্তর, ছাব্বিশ মার্চ কিংবা ষোলো ডিসেম্বর সংখ্যাও হয়ে উঠেছে কবিতার অনন্য শব্দসম্ভার।
ঠিক মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী কিংবা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে যেসব কবিতা লেখা হয়েছে তার অনেকগুলোতে আছে আবেগের আধিক্য। কারণ মুক্তিযুদ্ধ লেখকদের এতটাই আলোড়িত করেছে যে কবিতা লেখার সময়ে আবেগ আর সংযত থাকেনি। আমাদের কবিরা যেহেতু মাটি সংলগ্ন, জীবনঘনিষ্ঠ হয়ে কবিতার আঙিনায় এসেছেন, ফলে তাদের লেখনীতে কবিতা মুহুর্মুহু উচ্চারিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ।
কবিতায় উঠে আসা মুুক্তিযুদ্ধবিষয়ক কবিতা পাঠকদের মধ্যে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। শামসুর রাহামন, আহসান হাবীব, আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, আবুল হাসান, রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, নির্মলেন্দু গুণ, মোহাম্মদ রফিক, আসাদ চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, হাসান হাফিজুর রহমানসহ অনেকেই এ ধারার উল্লেখযোগ্য কবি।
রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ‘বাতাসে লাশের গন্ধ’ একটি বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতা মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত। নির্মলেন্দু গুণের ‘স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো’ কবিতাটি গণকবিতায় পরিণত হয়েছে। শামসুর রাহমানের ‘স্বাধীনতা তুমি’ কিংবা ‘তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা’ বাংলা কবিতার দুটি জনপ্রিয় কবিতা। ‘স্বাধীনতা তুমি’ কবিতায় তিনি লিখেছেন—‘স্বাধীনতা তুমি/ রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।/ স্বাধীনতা তুমি/ কাজী নজরুল, ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো/ মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা।’ ‘তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা’ কবিতা কবি লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে। এই কবিতায় সেই সময়ে দীপ্ত দৃঢ় উচ্চারণ ছিল তার। আবুল হাসান ‘উচ্চারণগুলি শোকের’ কবিতায় লিখেছেন—‘কেবল পতাকা দেখি/ কেবল উৎসব দেখি/ স্বাধীনতা দেখি/ তবে কি আমার ভাই আজ/ ঐ স্বাধীন পতাকা/ তবে কি আমার বোন, তিমিরের বেদীতে উৎসব?
কার্যত মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে লেখা বাংলা সাহিত্যের অসংখ্য লেখক অজস্র লেখা লিখেছেন। কেবল লেখকের নামই আছে হাজার হাজার। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সাহিত্যগুলো প্রধানত এক গভীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।
একটি কবিতার জন্মকথা
- বিশ্বজিৎ ঘোষ

‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ কবিতায় ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলা ছেড়ে লাখ লাখ শরণার্থীর কলকাতা যাওয়ার দুঃসহ অবর্ণনীয় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শরণার্থীর পথযাত্রার কষ্ট ও যন্ত্রণা গিনসবার্গের কবিতায় মর্মস্পর্শী বাসায় শিল্পিতা পেয়েছে
১৯৭১ সালে সংঘটিত বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে রচিত হয়েছে অনেক কবিতা, অসংখ্য সাহিত্যকর্ম। অনেক সাহিত্যকর্মের মধ্যে একটি কবিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রচিত ব্যতিক্রমধর্মী সেই কবিতার নাম ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ কবির নাম অ্যালেন গিনসবার্গ (১৯২৬-১৯৯৭)।
September On jessore Road
Allen Ginsberg
Millions of babies watching the skies
bellies swollen, with big round eyes
On jessore Road - Long bamboo huts
No place to shit but sand channel ruts.
Millions of fathers in rain
Millions of mother in pain
Millions of brothers in woe
Millions of sister nowhere to go
পাক-মার্কিন ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বাঙালির গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিযুদ্ধের সময় গিনসবার্গের এই কবিতা প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে।
‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ কবিতায় ১৯৭১ সালে পূর্ববাংলা ছেড়ে লাখ লাখ শরণার্থীর কলকাতা যাওয়ার দুঃসহ অবর্ণনীয় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শরণার্থীর পথযাত্রার কষ্ট ও যন্ত্রণা গিনসবার্গের কবিতায় মর্মস্পর্শী বাসায় শিল্পিতা পেয়েছে। খান মোহাম্মদ ফারাবিকৃত কবিতাটির অনুবাদ থেকে একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলেই উপলব্ধি করা যাবে এর উপজীব্য :
লক্ষ প্রাণের উনিশ শত একাত্তর
উদ্বাস্তু যশোর রোডে সব ধূসর
সূর্য জ্বলে ধূসর রঙে মৃতপ্রায়
হাঁটছে মানুষ বাংলা ছেড়ে কলকাতায়।
১৯৭১ সালে আমেরিকার কবি গিনসবার্গ ভারতে এসেছিলেন কলকাতায় আশ্রয় নেওয়া পূর্ববাংলার শরণার্থীদের দুঃখ-কষ্ট দুর্ভোগ সরেজমিন ঘুরে একটি প্রতিবেদন রচনার জন্য। তিনি কলকাতা এসেছিলেন ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আর নিউইয়র্ক ফিরে যান মধ্য নভেম্বরে। কলকাতায় অ্যালেন গিনসবার্গের সঙ্গী হয়েছিলেন তখন বিবিসির হয়ে রিপোর্ট করতে আসা মেহতা। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও গিনসবার্গকে নিয়ে ঘুরে বেরিয়েছেন কলকাতার পার্শ্ববর্তী শরণার্থী শিবিরগুলোতে। শরণার্থী শিবিরে লাখ লাখ মানুষ অবর্ণণীয় দুঃখ-কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে। পানি নেই, খাবার নেই, ওষুধ নেই—এসব দেখে ভীষণভাবে মর্মাহত হন গিনসবার্গ। দুঃসহ এই স্মৃতি, মানুষের এই অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বিশ্ব মানুষের গোচরে আনার জন্যই আমেরিকা পৌঁছে গিনসবার্গ রচনা করলেন ঐতিহাসিক এক কবিতা—নাম যার ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’।
অ্যালেন গিনসবার্গ ছিলেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ঘোর বিরোধী। আমেরিকার বুকে বসেই তিনি আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন তার কবিতার মাধ্যমে, তার গানের মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, অস্ত্র সরবরাহ করেছে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে, জাতিসংঘকে প্রভাবিত করতে চেয়েছে বাংলাদেশের অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য। মার্কিনি এসব অপকর্ম ও ষড়যন্ত্র গিনসবার্গকে গভীরভাবে মর্মাহত করে। মার্কিনি ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে তিনি লিখেছেন আলোচ্য কবিতা। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতা পাঠের আসরে আবৃত্তি করেছেন ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’—কবিতাটিতে সুর সংযোজন করে আমেরিকার বিভিন্ন শহরে গেয়েছেন যশোর রোডে দেখা তার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার শিল্পকুসুম এই শব্দ-আয়ুধ। এই কবিতা কিংবা একটি গান যে হতে পারে শক্তিশালী বড় অস্ত্র, গিনসবার্গের এই কবিতা তার উজ্জ্বল উদাহরণ।
অ্যালেন গিনসবার্গ আর নেই, কিন্তু আছে তার কবিতা ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে একটি কবিতার মাধ্যমে বিজড়িত হয়ে আছেন এই মার্কিন কবি। জয়তু ইরউইন অ্যালেন গিনসবার্গ, জয়তু ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ কবিতা।
একাত্তরের টুকরো স্মৃতি
- মোফাজ্জল করিম

এই স্মৃতিচারণায় কেন জানি আজ অর্ধশতাব্দী পরেও এগুলো আমাকে প্রায়ই তাড়িয়ে মারে। আমি যেন এক ভীতসন্ত্রস্ত যুবকের আর্তনাদ এখনো শুনতে পাই : মিনহাজ চাচা, দোহাই আপনার ‘বসকে’ বলুন এক্ষুনি কিছু একটা করতে। ওরা তো আমাদের লাইনআপ করাতে শুরু করেছে
একাত্তরের শুরুতে আমি ছিলাম তখনকার পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটি মহকুমার প্রশাসক। মহকুমাটির নাম মণ্ডি বাহাউদ্দিন।
এমন সময় জুন মাসের ২৫ না ২৬ তারিখ লাহোর থেকে টেলিফোনে বন্ধু ও ব্যাচমেট সফিউর রহমান একদিন সন্ধ্যায় জানাল, আমাকে ও আমাদের ব্যাচের আরো কয়েকজন যারা বছর দেড়েক আগে একসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে এসেছিলাম, তাদের ঢাকায় বদলি করা হয়েছে। শুনে আমি ও আমার স্ত্রী ভীষণ খুশি। যাক বাবা, আপনজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দিনরাত টেনশনে তো আর ভুগতে হবে না। সফিউর রহমান (বর্তমানে মরহুম) ওই সময়ে পাঞ্জাব সচিবালয়ে সংস্থাপন বিভাগে সেকশন অফিসার ছিল। সপ্তাহখানেক পর ঢাকা যাওয়ার পথে লাহোরে সপরিবারে এক রাত ছিলাম সফিউরের বাসায়।
ঢাকায় পাঁচ-ছয় দিন ছিলাম গোপীবাগে আমার শ্বশুরালয়ে। তারপর ১৬ জুলাই রওনা দিলাম কুমিল্লা। আমার নতুন কর্মস্থল। তখন কুমিল্লা বিমানবন্দর সচল ছিল। পিআইএর একটি ছোট বিমান ২০ থেকে ২২ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকা-কুমিল্লা সার্ভিস চালিয়ে যাচ্ছিল। আমি একাই গেলাম কুমিল্লা। বাচ্চাদের নিয়ে আমার স্ত্রী মমতাজ ঢাকায় পিত্রালয়ে থেকে গেলেন। কুমিল্লা বিমানবন্দরে আমাকে ‘রিসিভ’ করতে এসেছিল আমার আরেক ব্যাচমেট পাঞ্জাবের ছেলে তারিক সাইদ হারুন। কুমিল্লায় আমি তারই স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছিলাম।
কুমিল্লা বিমানবন্দর থেকে জেলা বোর্ডের ডাকবাংলো যেতে যেতে তারিক আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ব্রিফিং দিল। বিশেষ করে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টের সিনিয়র আর্মি অফিসারদের সম্পর্কে। তখন ব্রিগেডিয়ার আতিফ (এককালে পাকিস্তান অলিম্পিক হকি দলের ক্যাপ্টেন) ছিলেন ওই এলাকার জিওসি।
আমাকে জেলা বোর্ডের ডাকবাংলোয় উঠতে হলো, সার্কিট হাউসে নয়। কারণ কুমিল্লার সুদৃশ্য ও সুপরিসর দ্বিতল সার্কিট হাউসকে আর্মি তাদের দপ্তর বানিয়েছিল। ওটার দায়িত্বে ছিলেন লে. ক. নওয়াজ। আর্মির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ এই ভদ্রলোকের মাধ্যমেই হতো। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, এই ভদ্রলোকের মধ্যে কোনো উগ্রতা বা বদমেজাজ ছিল না। বরং কেমন একটা সিভিলিয়ান সিভিলিয়ান ভাব ছিল। আমি পশ্চিম পাকিস্তানে দুই বছর অবস্থানকালে পাঞ্জাবি ভাষাটা মোটামুটি রপ্ত করে ফেলেছিলাম। শেষের দিকে তো ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনের আগে আমার সাবডিভিশন মণ্ডি বাহাউদ্দিনের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় লোকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে পাঞ্জাবি ভাষায় কথা বলতে হতো। কুমিল্লায় কর্নেল নওয়াজ এবং তার সহকর্মীরা আমার পাঞ্জাবি ভাষাজ্ঞানে রীতিমতো পুলকিত বোধ করতেন। আর আমিও এটার অ্যাডভান্টেজ নিতে কসুর করতাম না। আজ ৫৩ বছর পর দুটি ঘটনার উল্লেখ করে আল্লাহপাকের শুকুর আদায় করতে চাই : মাবুদ, ভাগ্যিস ভাষা শেখার একটা সহজাত ক্ষমতা অল্প হলেও তুমি আমাকে দিয়েছ।
একদিন দুপুরে অফিসে বসে কাজ করছি। এমন সময় কুমিল্লা পৌরসভার সেক্রেটারি মিনহাজ উদ্দিন সাহেব আমার কামরায় প্রবেশ করলেন। সঙ্গে বছর ৩০ থেকে ৩৫-এর এক ভদ্রলোক, যিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। কী ব্যাপার? না, ওই ভদ্রলোকের বিএসসিপড়ুয়া অনুজকে আর্মি সকালবেলা বাসা থেকে ধরে নিয়ে গেছে। ওদের পাড়ায় নাকি আগের দিন রাতে একটা মিলিটারি জিপে কে বা কারা হাতবোমা মেরেছে। যদিও তাতে কেউ হতাহত হয়নি, তবু ব্রিগেডিয়ার সাহেবের হুকুমে ওই পাড়ার সব জওয়ান ছেলেপুলেকে আর্মি ধরে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে ওই বিএসসি ক্লাসের মেধাবী ছেলেটাও আছে। সর্বশেষ তথ্য পাওয়া গেছে, ক্যান্টনমেন্টে নাকি ওদের সবাইকে লাইনআপ করে ব্রাশফায়ারে খতম করার হুকুম হয়েছে। মিনহাজ সাহেবের কাছে ছেলেটির ভাই ছুটে এসেছেন আমাকে বলেকয়ে কোনোমতে ছেলেটিকে বাঁচানোর জন্য। ঘটনাচক্রে আমি কুমিল্লা পৌরসভার চেয়ারম্যানও ছিলাম। আমার সেক্রেটারি স্বল্পভাষী মিনহাজ সাহেব, বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর, একজন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও ধর্মপরায়ণ কর্মচারী ছিলেন। তিনিও বললেন ওই ছেলেটি নাকি অত্যন্ত মেধাবী, ভালো একটি ছেলে। ‘স্যার, যে করে হোক ছেলেটিকে এবং তার সঙ্গীদের বাঁচান। আর দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।’
আমি সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল নওয়াজকে টেলিফোনে অনুরোধ করলাম মৃত্যুদণ্ডাদেশ রদ করার জন্য। ‘ও জনাবো, তুসি কি করদে হো! সাডা জেড়ে সোনাদা বাচ্চো হ্যায়, উয়ো সারেকো আগর তুসি হালাক করদে তো ইয়ে মুলক কা জিম্মাদার কোন হয়েগা?’ এভাবে কিছুক্ষণ আমার টুটাফাটা পাঞ্জাবি এস্তেমাল করে নওয়াজ সাহেবকে রাজি করালাম বিষয়টি দেখতে।...সেই যাত্রায় শুধু ওই ছেলেই নয়, এলাকার সব বন্দিই রেহাই পেয়েছিল।
তবে আরেকটি ঘটনা, যেটা মনে পড়লে আজও আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়, সেটা ঘটেছিল গভীর রাতে। তখন এডিসি ভবনে ডিসি সাহেব, আমি ও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের একজন স্বনামখ্যাত আইজি পুলিশ, সেই সময়ে কুমিল্লার এসপি আমার বন্ধু এ এস এম শাহজাহান একসঙ্গে মেস করে থাকতাম। তিনজনেরই পরিবার থাকত ঢাকায়। তা কুমিল্লার প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ের এই তিন কর্মকর্তার একসঙ্গে একই ভবনে মেস করে থাকার পেছনে ছোট একটি ঘটনা আছে। আগেই বলেছি, আমার ঠাঁই হয়েছিল জেলা বোর্ডের ডাকবাংলোয়। ওখানে উঠেছিলাম ১৬ জুলাই, ১৯৭১-এ। তার ঠিক দুই দিন পর একদিন গভীর রাতে বর্ডারের ওপার থেকে কয়েকটি শেল এসে পড়ে কুমিল্লা শহরে। শহরবাসী তখন ঘুমে অচেতন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শাহজাহানের ফোন : এই, শব্দ শুনেছিস? শেলিং হচ্ছে বর্ডারের ওদিক থেকে। শেল পড়েছে সিভিল হাসপাতালের কাছে। আমি যাচ্ছি দেখতে। তুই যাবি নাকি? আমি তো শুনেই লাফিয়ে উঠলাম। যাব না মানে? নিশ্চয়ই যাব। একে তো নাচইন্যা বুড়ি, তার ওপর ঢোলের বাড়ি। কুমিল্লা আসার দুই দিনের মাথায় এই রকম একটা অ্যাডভেঞ্চারের দেখা মিলে যাবে, তা ভাবতেই পরিনি। জুন, ’৭১ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের এক পাণ্ডববর্জিত মহকুমায় আটকে পড়ায় মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার সুযোগ হয়নি। সেই আফসোস তখন প্রায়ই পোড়ায় আমাকে। যা হোক, শাহজাহানের সঙ্গে রাতদুপুরে অকুস্থলে গিয়ে জানলাম, এক নিঃস্ব ভিখারিনীর কুঁড়েঘরে শেল পড়ে তাকে এবং তার দুটি শিশুসন্তানকে ছাতু করে ফেলেছে। শাহজাহান ওই দৃশ্য আমাকে দেখতে দেয়নি। ‘তুই গাড়িতেই বসে থাক। এসব বীভৎস দৃশ্য পুলিশ দেখতে পারে, তোদের মতো ভদ্রলোক এগুলো সইতে পারবে না।’ উপস্থিত ক্ষেত্রে কী আর করি, আমি হাকিম হয়েও পুলিশের রায় মেনে নিলাম। ডাকবাংলোয় ফিরে সেই রাতে আর ঘুম এলো না। খালি মনে হতে লাগল, শেলটা ডাকবাংলোর ছাদেও তো পড়তে পারত।
তা পড়েনি ঠিকই। তবে দিন কয়েক পরে ডাকবাংলোয় রীতিমতো অ্যাটম বোমা পড়ল। তা-ও আবার আমার ঘরেই। একদিন রাতে কী কারণে একটু দেরিতে ফিরেছি ঘরে। বাতি জ্বালাতেই চমকে উঠলাম। আমার খাটের পাশে আরেকটি খাট ফেলা হয়েছে। আর তাতে মশারি টানিয়ে কে একজন ঘুমাচ্ছেন। দারোয়ান বলল, অন্য কোনো কামরায় একটুও খালি জায়গা না পেয়ে আমার এখানেই খাট পেতে বিছানা করে দেওয়া হয়েছে ওই আগন্তুকের জন্য। আর ভদ্রলোক দিব্যি আরামসে ঘুমাচ্ছেন।
মশারির জালের ভেতর দিয়ে তার নাক ডাকার ভোঁস ভোঁস আওয়াজ আসছে। জানতে চাইলাম, ইনি কে? জবাব এলো ইনি প্রফেসর গোলাম আজম। শুনে আমার মাথা ভোঁ করে চক্কর দিয়ে উঠল। এর চেয়ে যদি বলত, সুন্দরবন থেকে বেরিয়ে একটা বেঙ্গল টাইগার বা কেনিয়ার মাসাইমারা অভয়ারণ্য থেকে একজন পশুরাজ এসে শয্যা গ্রহণ করেছেন এই গরিবালয়ে, তবু এত চমকাতাম না। জানি না, সংবাদটা স্থানীয় মুক্তিবাহিনীর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে পৌঁছেছে কি না। যা হোক, আধো ঘুম আধো জাগরণে একসময় বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বেশ বেলা করেই ঘুম ভাঙল। ফোন করলাম জেলার শান্তিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত এসপি সাহেবকে। বললাম, আমি আর এক দিনও এই ডাকবাংলোয় থাকব না। তুই ডিসি সাহেবকে বলে আমার জন্য একটা বাসার ব্যবস্থা করে দে। আমার নিজের অসুবিধার কথা গুছিয়ে বলতে পারব না। আমার কথার মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে এসপি বাহাদুর বলল, “আমিও এই এসপি কোয়ার্টারে থাকতে চাই না। এর চাল অ্যাসবেস্টসের। একেবারে পলকা। এটার ওপর একটা শেল পড়লে আমার দশা ওই ‘ফইরনির’ মতো হবে।”
...এরপরের কাহিনি সংক্ষিপ্ত। ওই দিনই আমি আর এসপি পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে লাকসাম রোডের এডিসি ভবনে হাজির। ডিসি সাহেবই নাকি প্রস্তাবটা দিয়েছিলেন। দোতলার বড় বেডরুমে ডিসি সাহেব, আর তার পাশের অপেক্ষাকৃত ছোট রুমে দুটি খাট ফেলে আমরা দুই বন্ধু। সারা দিনের ব্যস্ততা, ছোটাছুটি ও টেনশনের পর যখন বিছানায় গা এলিয়ে দিতাম তখন আমরা দুজন শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ গল্প করতাম। গল্পেও উপজীব্য অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ, পাক আর্মি ও বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের স্মৃতি রোমন্থন। আর একটা অবশ্য উচ্চারিত ডায়ালগ ছিল : এই দ্যাখ, ঘুমের মধ্যে যদি একটা শেল পড়ে শেষ হয়ে যাই, তাহলে মাপসাপ করে দিস।
তা একদিন রাতে—রাত তখন প্রায় দুটো, একটা ফোন এলো আমার। কাঁচা ঘুমটা ভেঙে যাওয়ায় রীতিমতো বিরক্তিসহকারে ফোন ধরলাম। ফোন এসেছে বরুড়া (বর্তমানে উপজেলা, তখন ছিল থানা) থেকে। ফোনের অন্য প্রান্তে টেলিফোন অপারেটর। গলার স্বরে বুঝলাম সে খুবই উত্তেজিত। কথা বলছে ফিসফিস করে। ‘স্যার, আপনাদের সিও রেভিনিউকে আর্মি ধরে নিয়ে গেছে। আমরা জানতে পেরেছি তার কবর খোঁড়া হচ্ছে। রাতেই তাকে শেষ করে দেওয়া হবে।’ সিও, রেভিনিউ অর্থাৎ সার্কেল অফিসার, রাজস্ব, এখনকার এসি ল্যান্ড।
ঘটনা শুনে আমি বজ্রাহতের মতো কয়েক মুহূর্ত বিছানার ওপর বসে রইলাম। একবার ভাবলাম, শাহজাহানকে জানাই। পরক্ষণে মনে হলো, তাকে জাগিয়ে কোনো লাভ হবে না। বেচারা সারা দিনের দৌড়ঝাঁপের পর শান্তিতে একটু ঘুমাচ্ছে, ঘুমাক। তার চেয়ে ‘অগতির গতি হোমিওপ্যাথি’ কর্নেল নওয়াজকেই বরং কল দিই। তোমাদের লোকেরা রাতবিরেতে যা-তা করবে, আর সেটা তোমাদের জানানোও যাবে না, তাই হয় নাকি? যা থাকে কপালে, নওয়াজকেই জানাতে হবে। ও যদি রেগেমেগে আমাকেই ধরে নিয়ে যায় তো নেবে। ‘হ্যালো, কর্নেল সাহেব? আমি এডিসি, জেনারেল বলছি। এত রাতে আপনার ঘুম ভাঙানোর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু কী করব, একটা মস্ত বড় অন্যায় ঠেকাতে আপনাকে ফোন না করে পারলাম না।’ এরপর উর্দু-পাঞ্জাবি-ইংরেজি মিশিয়ে যা বললাম তা হচ্ছে এই : বরুড়ার ওই অফিসারটার মতো সাচ্চা ঈমানদার পাকিস্তানি এই জেলায় আর দ্বিতীয়টা নেই। সে খুবই সৎ, ধর্মভীরু একজন অফিসার। ঘুষ খায় না বলে কিছু লোকের শত্রু সে। তারা মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে আর্মির হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। ‘কর্নেল সাহেব, ভাই, আপনার দোহাই লাগে লোকটিকে বাঁচান। তা না হলে আপনি-আমি দুজনেই নির্ঘাত দোজখে যাব।’ কর্নেল নওয়াজ একটুক্ষণ গাঁইগুঁই করে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন কিছু না করতে, কোনো শাস্তি না দিতে।
কুমিল্লার জুলাই-ডিসেম্বরের (’৭১) এ ধরনের টুকরো স্মৃতি আরো আছে। তবে যে দুটো ঘটনার উল্লেখ করলাম এই স্মৃতিচারণায় কেন জানি আজ অর্ধশতাব্দী পরেও এগুলো আমাকে প্রায়ই তাড়িয়ে মারে। আমি যেন এক ভীতসন্ত্রস্ত যুবকের আর্তনাদ এখনো শুনতে পাই : মিনহাজ চাচা, দোহাই আপনার ‘বসকে’ বলুন এক্ষুনি কিছু একটা করতে। ওরা তো আমাদের লাইনআপ করাতে শুরু করেছে। আর সিও রেভিনিউ, বরুড়া, যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না পাশের ওই কবরটি খোঁড়া হচ্ছে তারই জন্য।
মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
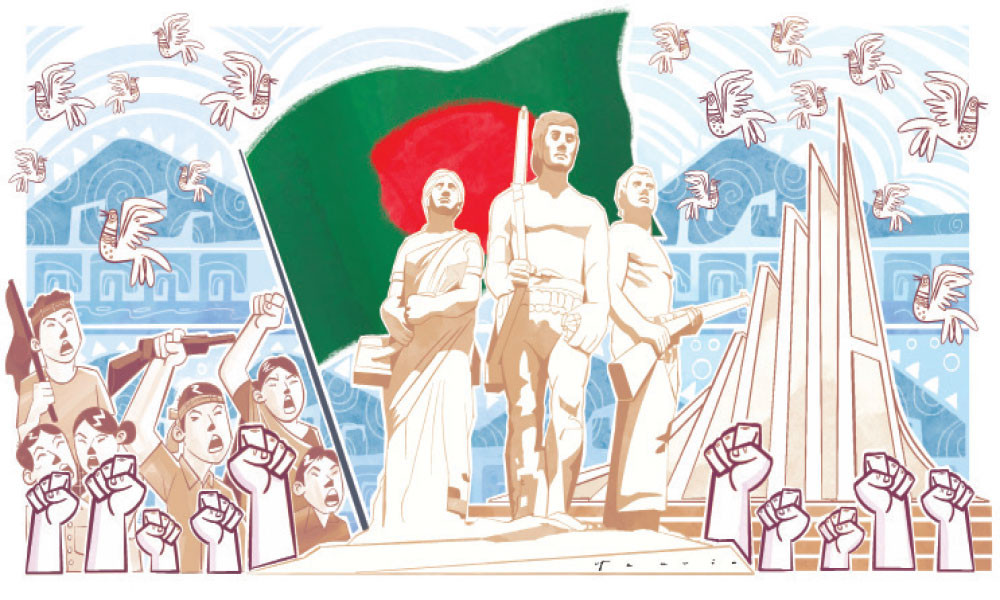
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সমষ্টিগত ইতিহাসের অংশ। সমষ্টির পক্ষে ইতিহাস ভুলে যাওয়া এবং ব্যক্তির পক্ষে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া একই রকমের দুর্ঘটনা। তবে ইতিহাস তো শুধু ঘটনার ধারাবিবরণী নয়; ইতিহাসে ঘটনার পর্যালোচনা থাকে, থাকতে হয় কার্যকারণ-সম্পর্কের বিশ্লেষণ, আবশ্যক হয় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের খবরও
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। সেই যুদ্ধে পূর্ববঙ্গের সব অংশের, শ্রেণির, সম্প্রদায়ের, পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করে।
গণহত্যার সূচনায় হানাদার বাহিনী যে কয়টি লক্ষ্যবস্তুকে ভেঙে ফেলার জন্য নির্দিষ্ট করেছিল, সেগুলোর মধ্যে একটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা তাদের শত্রুপক্ষের প্রধান অবস্থানভূমি হিসেবে স্থির করে নিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। ‘অপারেশন সার্চলাইট’ নামের যে গণহত্যার পরিকল্পনা তারা তৈরি করেছিল তাতে সুস্পষ্টভাবেই লেখা ছিল Operation-এর সাফল্যের জন্য প্রথমে দরকার হবে ঢাকা শহরের শতভাগ নিয়ন্ত্রণ; এবং তার জন্য ‘Dacca University will have to be occupied and searched’ পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৫ মার্চ রাতে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আক্রমণ চালায় এবং গোলাবারুদ ব্যবহার, অগ্নিসংযোগসহ নির্বিচারে গণহত্যা ঘটাতে থাকে।
বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘দখল’ করার সেই রাতে এবং পরের দিন সকালেও তারা কাউকেই গ্রেপ্তার করেনি, যাকে সামনে পেয়েছে ঝটপট হত্যা করেছে। বস্তুত গণহত্যার ৯ মাসে তারা গ্রেপ্তার করেছে নগণ্যসংখ্যক মানুষকেই, এবং যাদের ধরে নিয়ে গেছে তাদেরও বেশির ভাগকেই হত্যা করেছে। হত্যাই ছিল তাদের নীতি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কত মানুষ যে নিহত হয়েছে, তার হিসাব করা সহজ ছিল না। পরে তালিকা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। সেই তালিকায় শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী সবার নামই উঠে এসেছে। তবে কর্মচারীর সংখ্যা ও পরিচয় সেভাবে পাওয়া যায়নি, যেভাবে অন্যদের পরিচয় পাওয়া গেছে। এর কারণ হয়তো কয়েকটি। একটি হলো তাদের সংখ্যা ছিল অনেক এবং শুধু যে কর্মচারীরা শহীদ হয়েছেন তা নয়, তাদের পরিবারের সদস্যরাও বাদ পড়েনি। দ্বিতীয় কারণ হলো শ্রেণিগত অবস্থানে তারা দুর্বল ছিল। তৃতীয়ত, ২৫ মার্চের পরে তারা বেশির ভাগই চলে গিয়েছিলেন গ্রামের দিকে; পরে তারা ফিরে এসেছেন ঠিকই, কিন্তু শিক্ষক ও ছাত্রদের মতো দৃশ্যমান থাকেননি। সেই প্রচ্ছন্নতা আবার পেশাগতভাবে তাদের অবস্থানের সঙ্গে জড়িত।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরাও মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন। তারা যে এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই সত্য তো রয়েছেই। সভা, সমাবেশ ও মিছিলে তারা নিজেরা এবং তাদের পরিবারের সদস্যরাও যোগ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া এবং আন্দোলনে উপস্থিত থাকা, দুটিই হানাদারদের চোখে ছিল অপরাধ। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের অন্য একটি যুদ্ধে যুক্ত হতে হয়েছিল। সেটা ছিল জীবনযুদ্ধ। বেঁচে থাকার সংগ্রাম। ওই সংগ্রামও কিন্তু মুক্তিযুদ্ধেরই অংশ। কেননা দেশ মানে তো শুধু একটি ভূখণ্ড নয়, ভূমির চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় হচ্ছে মানুষ। আমরা দেশের কথা বলি ও শুনি, দেশ মানে আসলে তো দেশের মানুষ। হানাদাররা মানুষ চায়নি, জমি চেয়েছে; যার সরল অর্থ দেশের মানুষকে ঔপনিবেশিক শোষণের জালে আবদ্ধ রেখে নিজেদের সমৃদ্ধ করা। মানুষকে মারতে চেয়েছে, বাকি মানুষকে গোলাম করে রাখবে বলে। ওই মানুষদের জন্য তো মুক্তিযুদ্ধ; যুদ্ধের সময়ে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যে কঠিন সংগ্রাম, সেটাও মুক্তিসংগ্রামেরই অংশ বৈকি। জীবন বাঁচানো দেশ বাঁচানো থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার ছিল না। ছিল অবিচ্ছেদ্য। ভুক্তভোগীরাও যোদ্ধাই ছিলেন। মুক্তিযোদ্ধা।
জীবন বাঁচানোর জন্য যারা আশ্রয়ের খোঁজে বের হয়েছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা ছিল মর্মান্তিক। মানুষের দুর্ভোগ নিয়ে সাহিত্য রচনা করা হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের প্রকৃত দুর্ভোগ যে সাহিত্যের যেকোনো বর্ণনার তুলনায়ও নির্মম হতে পারে একাত্তরে তার প্রমাণ রেখে গেছে।
যুদ্ধের ওই দিনগুলোতে বেঁচে থাকাটা সহজ ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কর্মচারীরা আশ্রয়ের খোঁজে বের হয়েছিলেন তারা কোথায় গিয়ে থাকবেন, কেমন করে যাবেন, কিছুই জানতেন না। প্রায় সব ক্ষেত্রেই পরিবারের যিনি প্রধান তিনিই প্রথমে নিহত হয়েছেন। এমনিতেই তাদের আয়-উপার্জন ছিল সীমিত; তার মধ্যে অপ্রত্যাশিত ও অবিশ্বাস্য ওই সব মৃত্যু। শোকে দুঃখে বেদনায় প্রতিটি পরিবার ছিল অভিভূত। কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। দুঃসহ ওই যন্ত্রণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আশ্রয়হীনতা এবং টাকা-কড়ির অভাব। খাবারদাবার নেই। জামাকাপড়ের পর্যন্ত অভাব। এমন ঘটেছে যে গায়ের যে জামা বা শাড়িটি পরে বের হয়েছেন ৯ মাস ধরে সেটিই পরে থাকতে হয়েছে। ওদিকে আবার দেশে তখন শুরু হয়ে গেছে নীরব দুর্ভিক্ষ। চারদিকে অভাব। সর্বোপরি রয়েছে হানাদারদের আক্রমণের শঙ্কা।
একসময় সমগ্র বাংলাদেশে চলছিল মানুষের মনুষ্যত্বের অসম্ভব কঠিন এক পরীক্ষা। সহ্যের পরীক্ষা, পরীক্ষা দয়ামায়ারও। ওই বিপদে মানুষ মানুষকে সাহায্য করেছে, যে যেভাবে পারে। সামর্থ্যের প্রাচুর্য ছিল না, অভাব-অনটন, নিরাপত্তাহীনতা ছিল সর্ববিস্তারী। ওই পরীক্ষায় বেশির ভাগ মানুষই উত্তীর্ণ হয়েছে। হানাদাররা হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষকে আলাদা করতে চাইত। অমুসলিমদের হত্যা করাটাও তাদের বিশেষ রকমের নেশায় পরিণত হয়েছিল। জগন্নাথ হল এলাকায় বসবাসকারীদের ওপর যে হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয় তার অতিরিক্ত কারণ এটি যে সেখানে বসবাসকারী কর্মচারীদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য। কিন্তু হানাদারদের ওই আক্রমণে বাংলাদেশ থেকে তখন সাম্প্রদায়িকতাকে প্রায় অনুপস্থিত করে দিয়েছিল। বিপন্ন মানুষ সাম্প্রদায়িক পরিচয় ভুলে গিয়ে পরস্পরের আত্মীয় হয়ে উঠেছিল। মসজিদের ইমাম নিজে বিপন্ন হিন্দু পরিবারকে বাঁচিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের কয়েকটি পরিবার আশ্রয়ের খোঁজে যখন দিশাহারা তখন হোসেনি দালানে শিয়াদের ইমামবাড়ায় প্রাথমিকভাবে আশ্রয় পেয়েছিল, সেখানকার ধর্মপ্রাণ মানুষ আশ্রয়প্রার্থীরা যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য সেটা জানত, কিন্তু হিন্দু মুসলমানের পার্থক্য তাদের বিবেচনায় আসেনি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে মনুষ্যত্বের পরাজয় যে ঘটেনি তা-ও নয়। রাজাকাররা ছিল। পরে আলবদর, আলশামস গঠিত হয়েছিল বুদ্ধিজীবী হত্যা সংঘটনে। লুণ্ঠনকারীদেরও দেখা গেছে। যুদ্ধের সময়েই রোকেয়া হল ও জগন্নাথ হলে ডাকাতির ঘটনা ঘটে।
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সমষ্টিগত ইতিহাসের অংশ। সমষ্টির পক্ষে ইতিহাস ভুলে যাওয়া এবং ব্যক্তির পক্ষে স্মৃতিভ্রষ্ট হওয়া একই রকমের দুর্ঘটনা। তবে ইতিহাস তো শুধু ঘটনার ধারাবিবরণী নয়; ইতিহাসে ঘটনার পর্যালোচনা থাকে, থাকতে হয় কার্যকারণ-সম্পর্কের বিশ্লেষণ, আবশ্যক হয় অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের খবরও।
একাত্তরে যা ঘটেছিল তা হলো পাকিস্তান নামের অস্বাভাবিক রাষ্ট্রটির ভেতরে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অনিবার্য দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। রাষ্ট্রটি ভাঙতই; কিভাবে ভাঙবে, কত দিন পরে ভাঙবে—সেটাই ছিল প্রশ্ন। ভাঙনকে ত্বরান্বিত করেন রাষ্ট্রের শাসকরাই, গণহত্যার মধ্য দিয়ে।
তা রাষ্ট্র তো ভাঙলই, কিন্তু প্রশ্ন রইল তাতে পূর্ববঙ্গের সংগ্রামী মানুষের মুক্তি এলো কি? যে মানুষের এমন কঠিন সংগ্রাম, দুর্ভোগ, আত্মত্যাগের কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, তার অভ্যন্তরে দেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল যে মুক্তির, যার জন্য যুদ্ধটাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধ বলি, মুক্তির সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে কি? এককথায় তার জবাব হলো, না, ঘটেনি। যুদ্ধে প্রধান শক্তি ছিল জনগণ, জনযুদ্ধ ছিল মূলত মেহনতিদের জনযুদ্ধ, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা ছিলেন ওই মেহনতিদেরই অংশ। নেতৃত্বে ছিলেন উঠতি বুর্জোয়ারা। তাদের কেউ কেউ যুদ্ধে গেছেন, কিন্তু বড় অংশই হয় ছিল নিষ্ক্রিয়, নয়তো শরণার্থী। যুদ্ধ শেষে উঠতি বুর্জোয়ারাই কিন্তু রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা পেয়ে গেছেন। ক্ষমতা পেয়ে তারা নিজেদের উন্নতি ঘটিয়েছেন এবং পাকিস্তানি শাসকরা যা করেছিলেন তা-ই করেছেন। শোষণ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে ধনী হয়েছেন এবং ওই ধনের বেশ কিছুটা পাচার করে দিয়েছেন বিদেশে।
পাচারের ব্যাপারে আগের শাসকদের চেয়ে তাদের আচরণ ভিন্ন ছিল না। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে মেহনতিদের শ্রমেই—তারা শ্রম দিয়েছে দেশের ভেতরে এবং বিদেশে গিয়ে। কিন্তু উন্নয়নের ফল থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। আগের শাসকদের শাসনকালে যেমনটা ঘটত; স্বাধীন বাংলাদেশের শাসকের কর্মকাণ্ডও ঠিক তেমনটাই ঘটেছে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে ধনীদের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছে। আগের কালে সম্পদ চলে যেত দিল্লিতে, লন্ডনে, এবং পিন্ডিতেও; এখন যায় বিভিন্ন দেশে। সাধারণ মানুষের বঞ্চনা ও দৈন্য ঘোচে না। সামগ্রিক বিচারে দেশ দরিদ্রই রয়ে যায়। এই হচ্ছে স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাস। এই ইতিহাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রামী কর্মচারীদের জীবনেও সত্য বৈকি।
ইতিহাসের ক্ষেত্রে আরো একটি জিজ্ঞাসা থাকে। জিজ্ঞাসাটা হলো ওই যে পাকিস্তান হিন্দুস্তানে যে ভাগাভাগি, যার ফলে দুর্ভোগের এত সব ঘটনা, সেটার জন্য দায়ী কারা? জবাবটা আমাদের জানা আছে : দায়ী একদিকে ব্রিটিশ শাসকরা, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী দুই রাজনৈতিক দল, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ। ব্রিটিশের প্ররোচনা ও আগ্রহ ছিল দেশভাগে। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ছিল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। ওই দুই জাতীয়তাবাদী দলের কোনোটাই এই সত্যটাকে মেনে নেয়নি যে ভারতবর্ষ একটি বা দুটি নয়, বহুজাতির একটি উপমহাদেশ। কংগ্রেস বলেছে জাতি এখানে একটাই, সেটি ভারতীয়; মুসলিম লীগের দাবি জাতি রয়েছে দুটি—হিন্দু ও মুসলমান, তাই মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র একটি বাসভূমি চাই। এই দ্বন্দ্বে সাতচল্লিশের দেশভাগ ঘটে, যেটি ছিল আমাদের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের পর দ্বিতীয় ট্র্যাজেডি এবং ওই ট্র্যাজেডির ধারাবাহিকতায়ই একাত্তরের যুদ্ধটি ঘটেছে।
ইতিহাস পাঠকালে জিজ্ঞাসা থাকে এটাও যে স্বাধীন হয়েও আমরা যে মুক্ত হতে পারলাম না, সেই সমস্যার সমাধান কী? অর্থাৎ মুক্তি আসবে কোন পথে? কোন পথে এগোলে সাধারণ মানুষের দুঃখ ঘুচবে। জবাবটাও পাওয়া যাবে আমাদের ইতিহাসের মধ্যেই। সেটি হলো এই যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তন বেশ কয়েকবার ঘটেছে, সর্বশেষ পরিবর্তনটি ঘটল একাত্তরে। কিন্তু যেটা ঘটেনি সেটি হলো সামাজিক বিপ্লব। রাষ্ট্র বদলেছে নামে ও আয়তনে; শাসকবদলও দেখতে পেয়েছি, কিন্তু সমাজের ভেতরে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তাতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। সেই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩ সালের, যার মধ্য দিয়ে মূল সামাজিক সম্পর্কটা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল জমিদার ও প্রজার, সেই সম্পর্কটাই নানা নামে ও ভাবে পুনরুৎপন্ন হয়েছে। ওই ব্যবস্থা না ভাঙলে মুক্তি যে আসবে না, সেটা ঐতিহাসিকভাবে ও কারণে সত্য।
লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়