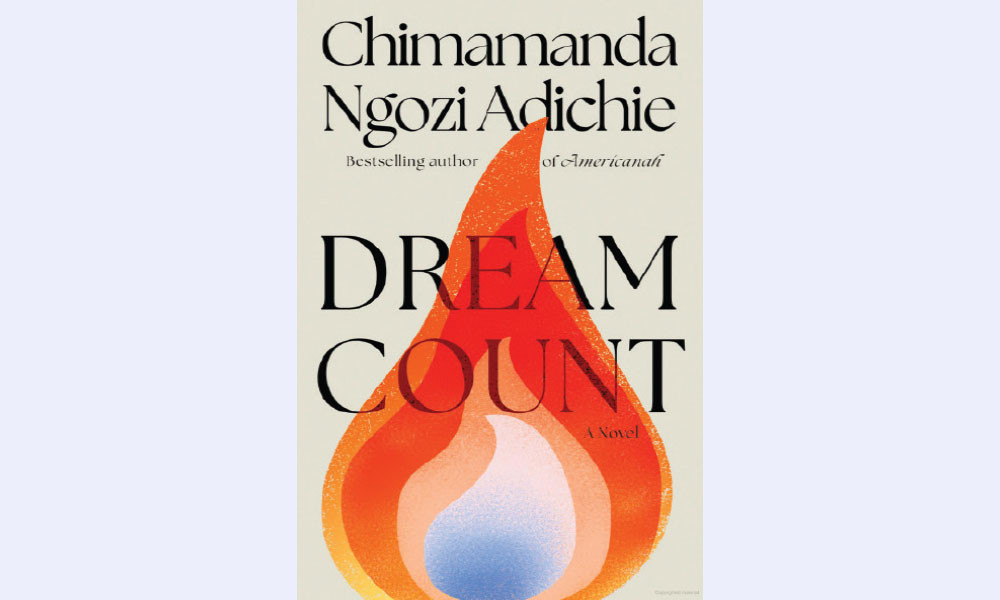কেউ কেউ তো এখানে সত্যিকারের কাবুলিওয়ালা হয়ে ওঠে। রহমত কাবুলিওয়ালার চেহারাটা স্পষ্টই ভর করে। আমাদের আজমল স্যার সে রকমই একজন কাবুলিওয়ালা ছিলেন।
আজমল স্যারের কাবুলিওয়ালা হয়ে ওঠার যে গল্প, সেটা বলার আগে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু বলি। তিনি ছিলেন বাংলাদেশে একটি স্বনামধন্য কলেজের রসায়নের সহকারী অধ্যাপক। ছাত্রজীবনেও তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। রসায়ন বিষয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণি পেয়ে মাস্টার্স করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে সরাসরি একটা কলেজে প্রভাষকের চাকরি নেন। একটু দেরিতে অবশ্য বিয়ে করেন। একটা ছেলেসন্তান ছিল।
এমন ভালো ছাত্র হওয়ার পরও তিনি চাকরিজীবনে খুব একটা সফলতার মুখ দেখেননি। এর পেছনে একটাই কারণ ছিল, তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ছিলেন। আজকালকার সমাজে নয়কে ছয় বা ছয়কে নয় করা, এর কিছুই বুঝতেন না। তাঁর সহকর্মী বন্ধুরা যখন তরতর করে ওপরে উঠে যাচ্ছিল, তখন তিনি সেই একই কলেজে সহকারী অধ্যাপক হয়ে পড়ে ছিলেন।
আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। সূর্য সেন হলের আবাসিক ছাত্র। আজমল স্যার মাঝেমধ্যে আমার ছাত্রাবাসে চলে আসতেন। কখনো একা, কখনো আমার বাবার সঙ্গে। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন।
একদিন আজমল স্যার আমার ছাত্রাবাসে এসে বলেন, ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি নিউজিল্যান্ড যাব।’
আমি অবাক হই। জিজ্ঞেস করি, ‘কেন?’
তিনি বলেন, ‘হায়ার স্টাডি করতে।’
‘হায়ার স্টাডি?’
‘হ্যাঁ, হায়ার স্টাডি। কলেজে আমার কলিগরা বলেছে, বিদেশে হায়ার স্টাডি করে এলে এখানে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বড় কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি হবে। আর মানুষ তো বাইরে গিয়ে হায়ার স্টাডি করেই’।
আজমল স্যারের কথা ঠিক। এটা সত্য, মানুষ তো বাইরে হায়ার স্টাডি করতেই যায়। অনেকে হায়ার স্টাডি করে বিদেশেই সেটেল্ড হয়ে যায়। কিন্তু আজমল স্যার এই বয়সে যাবেন? তাঁর বয়স তো পঞ্চাশের ওপরে। তেপ্পান্ন-চুয়ান্ন বছর হবে। আমি তাই মুখ ফসকে বলে ফেলি, ‘স্যার, এই বয়সে?’
আজমল স্যার অবশ্য সেদিন বুদ্ধিমানের মতো কথা বলেন, ‘লেখাপড়ার কোনো বয়স নেই।’
দুই.
আজমল স্যার উনিশশো পঁচানব্বই সালে নিউজিল্যান্ডে চলে যান। বিদেশ যাওয়ার পর তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উনিশশো সাতানব্বই সালের জানুয়ারিতে আমি নিউজিল্যান্ডে এলে এর এক মাস পর হকসবে অঞ্চলের হেস্টিং শহরে ফেব্রুয়ারির এক সকালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁকে দেখে আমি চমকে উঠি। তাঁর এ কী হাল! চেহারা ভেঙে গেছে। চোখ দুটো বসে গেছে। বয়সটা বেড়ে গিয়ে মনে হচ্ছে ষাট হয়ে গেছে। অথচ তিনি দেখতে খুব ফরসা ও সুন্দর ছিলেন। যে কেউ তাঁকে দেখলে বলত, রাজপুরুষ। তিনি সত্যি রাজপুরুষ ছিলেন। একবার কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বাংলা সিনেমের শুটিং দেখতে গেলে এক চলচ্চিত্র পরিচালক তো তাঁকে নায়ক বানানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু তাঁর অতিরিক্ত সহজ-সরল স্বভাবের জন্য তিনি জীবনে এক কলেজের শিক্ষক বাদে কিছুই হতে পারেননি। আর কলেজে শিক্ষকতা করতে গিয়ে খুব যে সুখে ছিলেন, তা নয়। সাদাসিধে হওয়ার জন্য পদে পদে কলিগ, প্রিন্সিপাল, এমনকি ছাত্রদের কাছে অপদস্থ হতেন।
আমি সেদিন আজমল স্যারের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে হেস্টিংস শহরের একিনা সাবার্বের উইলো পার্কের এক বেঞ্চিতে গিয়ে বসে জিজ্ঞেস করি, ‘স্যার, আপনার কী হয়েছে?’
আজমল স্যার সরল গলায় জিজ্ঞেস করেন, ‘কেন, কিছু হয়েছে নাকি?’
‘আপনার চেহারা কী বানিয়েছেন?’
‘টেনশনে, অতিরিক্ত টেনশনে’।
‘কেন এত টেনশন?’
‘আমি বিদেশ আসার আগে তুমি একদিন ঠিকই বলেছিলে, আমার এই বয়সে বিদেশে আসা ঠিক হয়নি। আমার জন্য বিদেশ না। এখন নিউজিল্যান্ডে কিছুই করতে পারছি না। ওদিকে বাংলাদেশের কলেজের চাকরিটাও যায় যায় অবস্থা।’
‘খুলে বলেন তো। এই দুই বছর তো আপনার কোনো খবর পাইনি।’
আজমল স্যার চেহারা একটু ভারী ও বিষণ্ন করে বলেন, ‘তুমি তো জানো, আমি হ্যামিল্টনের ওয়াইকাটো বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের টাকায় টিউশন ফি দিয়ে ভর্তি হয়ে এসেছি। কোনো স্কলারশিপ নিয়ে নয়। বাংলাদেশে অনেকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে ও নিজের জমিজমা বিক্রি করে আমার বাইশ হাজার ডলার টিউশন ফি জমা দিতে হয়েছে। এ ছাড়া এয়ার ফেয়ার আরো কত কী! কিন্তু নিউজিল্যান্ডে এসে তো অকূল দরিয়া নয়, রীতিমতো প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ি। হ্যামিল্টন শহরে এমনিতেই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টরা কোনো চাকরি পায় না। তার ওপর আমার বয়স অনেক বেশি।’
আমি নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করি, ‘তারপর?’
‘তারপর আমার না খেয়ে থাকার মতো অবস্থা। ওখানকার কিছু বাঙালি আমাকে পরামর্শ দেয় তাওরাঙ্গা বা হেস্টিংস শহরে চলে আসতে। এখানে তো ফলের বাগানে প্রচুর কাজ’।
‘আপনি তাই করলেন?’
আজমল স্যার মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, ‘হ্যাঁ’।
আমি জিজ্ঞেস করি, ‘তারপর?’
আজমল স্যার বলেন, ‘তারপর আর কি, আমি কিছুদিন তাওরাঙ্গা শহরে কাজ করে পরে হেস্টিংসে চলে আসি।’
‘আপনার ওয়াইকাটো ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি?’
‘ওটা আর করা সম্ভব হয়নি। একে তো দেশে অনেকের কাছ থেকে ঋণ করে নিউজিল্যান্ডে এসেছি। ওরা চাপ দিচ্ছিল। তাই ওয়াইকাটো ইউনিভার্সিটি থেকে আমার টিউশন ফি তুলে ফেলেছি। তুলে দেশে আবার টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি।’
‘তাহলে এখন কী করবেন, দেশে চলে যাবেন?’
‘হ্যাঁ, তাইতো করতে হবে। আমার ছেলেটার কথা খুব মনে পড়ে। এখানে মন টিকছে না। আমি তিন মাস হ্যামিল্টন শহরে বসে বসে খেয়েছি। বেশ ঋণ হয়ে গেছে। দেশে আরো কিছু ঋণ আছে। নিজেও কিছু টাকা না নিয়ে যাই কিভাবে?’
আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বলি, ‘তাইতো!’
তিন.
আজমল স্যারের আর দেশে যাওয়া হয়নি। দেশে কলেজের গভর্নিং বোর্ড তাঁর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁকে চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়। আধাসরকারি কলেজ। গভর্নিং বোর্ড এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। কলেজের চাকরিটা চলে যাওয়ার পর আজমল স্যার দেশে যাওয়ার চিন্তা বাদ দেন। এদিকে তাঁর নিউজিল্যান্ডে লিগেল স্টুডেন্ট ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। তিনি দ্বিধা ও দ্বন্দ্বে অনেকটা দেরি করে সঠিক কোনো গ্রাউন্ড তৈরি না করেই রাজনৈতিক আশ্রয় চান। যেহেতু তিনি স্টুডেন্ট ভিসা শেষ হওয়ার পর অবৈধ হয়ে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছিলেন, তাই নিউজিল্যান্ড সরকার তাঁকে সোশ্যাল বেনিফিটও দেয়নি। ব্যাপারটা এমন হয়েছিল, তাঁর রাজনৈতিক আশ্রয়ের কেস যত দিন ইমিগ্রেশনে চলবে তত দিন তিনি থাকতে পারবেন, কিন্তু সরকারের কোনো সুযোগ-সুবিধা তিনি পাবেন না।
আমি যখন তাওরাঙ্গা শহরের কাছে মাউন্ট মাঙ্গানুই শহরে মামার বাসায় থাকি, তখন আজমল স্যারকে মামার বাসায় নিয়ে আসি। পুরো এক বছর তিনি আমার সঙ্গে রুম শেয়ার করেন। স্যারের সঙ্গে কত সুখদুঃখের আলাপই না করতাম। স্যার আমার দ্বিগুণ বয়সী হলেও আমরা কেমন বন্ধু হয়ে উঠি। স্যার সারাক্ষণ শুধু ছেলের গল্পই করতেন। স্যারের ছেলের নাম ছিল আবরার হোসেন। আজমল হোসেন স্যার নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছিলেন। স্যার যখন ছেলেকে বাংলাদেশে রেখে আসেন তখন আবরারের বয়স ছিল আট বছর। রুমে থাকলে স্যার সারাক্ষণ শুধু আট বছর বয়সী আবরারের একটি ছবির দিকেই ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতেন। কতবার তাঁকে ছেলের ছবির দিকে তাকিয়ে একা একা কাঁদতে দেখেছি!
আজমল স্যার একটা কথা প্রায়ই বলতেন, ‘নিউজিল্যান্ডে এই অনিশ্চিত জীবন, এত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা, এত কষ্ট সবই সহ্য করছি আমার এই ছেলেটার জন্য। আবরারের একটা গতি করে যেতে পারলে আমি মরে গিয়েও শান্তি পাব!’
আজমল স্যারের সঙ্গে উইকএন্ডে বা কোনো বিকেলে হাঁটতে বের হলে আমি একটা ব্যাপারে খুব বিরক্ত হতাম। তিনি ফুটপাতে বা পার্কে আট বছর বয়সী কোনো ছেলে দেখলেই গায়ে পড়ে কথা বলতেন। ওদের কেউ কেউ কথা বলত। কেউ কেউ না বুঝে স্যারকে অবহেলা করে চলে যেত। একটা সময় দেখলাম, স্যার পকেটে চকোলেট, ললি বা ললিপপ নিয়ে হাঁটেন। আট বছর বয়সী কোনো ছেলে দেখলেই চকোলেট বা ললিপপ সাধাসাধি করেন। অনেকেই তাঁর দেওয়া ললিপপ বা চকোলেট নিত। অনেকে ‘নো থ্যাংকস’ বলে চলে যেত। আমি স্যারকে সতর্কও করেছিলাম এটা না করতে। কিন্তু স্যার তো অতশত বোঝেন না।
আরেকটা ব্যাপার আমাকে অবাক করত, আজমল স্যারের মাথায় শুধু তাঁর ছেলের আট বছর বয়সটাই কাজ করত। ছেলের আট বছর বয়স থেকে তিনি বের হতে পারতেন না। আবরারের যে বয়স বাড়ছে, ওটা স্যারের মাথায়ই ছিল না। এর পেছনে আরেকটা কারণও ছিল। আবরারের আট বছর বয়সী ছবিটা। তখন অবশ্য ইন্টারনেটের তেমন যুগ ছিল না। সবার হাতে মোবাইলও ছিল না। আমি যে গল্পটা করছি সেটা উনিশশো সাতানব্বই-আটানব্বই সালের গল্প।
চার.
উনিশশো আটানব্বই সালের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে আমি অকল্যান্ডে চলে যাই। আজমল স্যার মাউন্ট মাঙ্গানুই ছেড়ে আবার হেস্টিংস শহরে চলে যান। মাঝখানে কর্মব্যস্ততায় স্যারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। একদিন শুনি, আজমল স্যারকে হেস্টিংস পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। আমি খবরটা শুনে আঁতকে উঠি। হেস্টিংসে বন্ধুসম একজনকে ফোন করে জানতে পারি, স্যার বিকেলে পার্কে হাঁটতে গিয়ে আট বছরের এক ছেলের হাত ধরে টানাটানি করেছেন। এ জন্য ছেলেটা ভয় পেয়ে চিৎকার করে বাসায় গিয়ে তার মা-বাবাকে গিয়ে বলে। ছেলের মা-বাবা তৎক্ষণাৎ পুলিশ ডাকে। আজমল স্যার অ্যারেস্ট হন।
এদিকে নিউজিল্যান্ডের বাঙালি মহলে ছড়িয়ে পড়ে, ‘ওয়ান এইট ইয়ার্স ওল্ড বয় হ্যাজ বিন সেক্সুয়ালি এসাল্টেড বাই আজমল হোসাইন...!’ হেস্টিংসের কমিউনিটি নিউজপেপারে মনে হয় এই সংবাদটি ছাপাও হয়। কিন্তু আমি তো জানি কী হয়েছে। আমি স্যারকে আগেও কয়েকবার সতর্ক করেছিলাম। তিনি সরল মনে যা-ই করুন, নিউজিল্যান্ডে ছেলেমেয়েদের এ ব্যাপারগুলো খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখে। পুলিশ সর্বোচ্চ পন্থা অবলম্বন করে।
আজমল স্যারের সেই ব্যাপারটা অবশ্য বেশিদূর গড়ায়নি। কোর্ট পর্যন্ত ওঠেনি। হেস্টিংস শহরে বসবাস করে আবু সাইদ ও আসাদ রহমান নামের দুই ভালো মনের মানুষ স্যারের হয়ে বেশ পরিশ্রম করে সেই ছেলেটার মা-বাবাকে অনেক বুঝিয়ে কেসটি কোর্ট পর্যন্ত তুলতে দেয়নি। তিন দিন পর আজমল স্যারকে হেস্টিংস পুলিশ স্টেশন থেকেই ছাড়িয়ে নিয়ে আসে।
তারপর আজমল স্যার আর হেস্টিংস শহরে বেশিদিন থাকেননি। তাওরাঙ্গা শহরের অদূরের ছোট্ট শহর টিপুকিতে চলে আসেন। আমিও তত দিনে অকল্যান্ড ছেড়ে হ্যামিল্টন শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি।
একদিন স্যারকে হ্যামিল্টন থেকে টিপুকি শহরে দেখতে আসি। স্যার তখন বাঙালিদের থেকে একটু দূরে দূরে থাকেন। আদিবাসী মাউরিদের সঙ্গে এক বাসায় রুম শেয়ার করে থাকেন। স্যার আরো শুকিয়ে গেছেন। গাল-চোখ অরো বসে গেছে। খানিকটা কুঁজো হয়ে গেছেন। অথচ তাঁর বয়স তখন বড়জোর সাতান্ন কি আটান্ন হবে।
সেদিন আজমল স্যারকে দেখে আমার এতই কষ্ট হয়েছিল যে আমি স্যারের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করিনি। বিকেলে একটা কফিশপ থেকে দুই কাপ কফি নিয়ে আমরা টিপুকির একটা পার্ক ধরে হাঁটতে বের হই। পার্কে দেখি কিছু ছেলেমেয়ে খেলা করছে। ওদের মধ্যে আট বছর বয়সীও কেউ কেউ আছে।
স্যার ও আমি পার্কে পাশাপাশি হাঁটছিলাম। হঠাৎ স্যারকে দেখি তিনি পার্কের ছেলেমেয়েদের দেখে খানিকটা দূর দিয়ে ঘুরে যেতে চাচ্ছেন। তিনি কেমন যেন ভয় পাচ্ছেন। ভয় পেয়ে এদিক-ওদিকও তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারি, তিনি হেস্টিংসের সেই ঘটনার পর এই ব্যাপার নিয়ে ভয় পাচ্ছেন।
আমি স্যারের রুমে ফিরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জিজ্ঞেস করি, ‘স্যার, হেস্টিংসে আসলে কী হয়েছিল?’
আজমল স্যার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর কী ভেবে বলেন, ‘হেস্টিংসের উইলোপার্ক। সেই পার্কটা তো তুমি চিনোই। তুমি যখন হেস্টিংসে ছিলে তোমাকে নিয়ে কয়েকবার হাঁটতে গিয়েছি। সেই পার্কে একটা আট বছরের ছেলে বাইক চালাচ্ছিল। আমি তাকে ডেকে চকোলেট দিতে যাই। সে কোনো কারণ ছাড়া চিৎকার দিতে শুরু করে। আমি তাকে তার হাত ধরে বোঝানোর চেষ্টা করি, এটা চকোলেট, অন্য কিছু না। ছেলেটা আরো চিৎকার- চেঁচামেচি করে বাইক নিয়ে চলে যায়। একটু পরে পুলিশ এসে পার্ক থেকে আমাকে ধরে নিয়ে যায়।’
আমি বলি, ‘আমি তো আগেই আপনাকে সতর্ক করেছিলাম। আপনার সরলতা সবাই বুঝবে না। কোনো আট বছরের ছেলেও না।’
আজমল স্যার বেশ কিছুক্ষণ কোনো জবাব দেননি। তারপর নিজের ছেলের প্রসঙ্গ টানেন। আস্তে আস্তে সেদিনের সন্ধ্যাটা আরো ভারী হয়ে ওঠে। তিনি একসময় ছেলে আবরারের আট বছর বয়সের ছবিটা ব্যাগের একটা ডায়েরি থেকে বের করে দেখতে দেখতে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন।
আমার চোখও তখন কেমন ভিজে আসে। আমার মনে হয়েছে স্যারকে কিছু বলি। কোনো সান্ত্বনা। কিন্তু এর কিছুই বলতে পারিনি। আমার বারবার মনে হয়েছিল, এই ছাপ্পান্ন-সাতান্ন বছরের সরল শিশুটাকে কে বোঝাবে যে এই পৃথিবী তাঁর নয়। তাঁর সেই আট বছরের ছেলে আবরার আর আট বছরের নেই।
সেদিন রাতে টিপুকি শহর থেকে হ্যামিল্টনে ফিরতে ফিরতে একটা কথাই মনে হয়েছিল, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই রহমত কাবুলিওয়ালাই শেষ কাবুলিওয়ালা নয়। পিতৃ হৃদয়ের সেই কাবুলিওয়ালাদের আজও প্রতিদিন পৃথিবীর প্রতিটি শহরেই দেখা যায়। শুধু একজন আজমল স্যার নন, শতজন। সহস্রজন বা তারও অধিক।