রাজনৈতিক নেতৃত্বের সংজ্ঞা বা বিশ্লেষণ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্নতর হয় চিন্তাশক্তির প্রখরতা, অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। তবে নেতৃত্ব বিষয়ে ব্রিটিশ টেলিভিশন সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাক্ষাৎকারের বিশ্লেষণটি স্বতঃসিদ্ধ ও অকাট্য বলেই প্রতীয়মান হয়। কারণ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে একজন মানুষের নেতা হওয়ার জন্য অনুসরণযোগ্য সব উপাদান। ১৯৭২ সালের ১৮ জানুয়ারি ফ্রস্টের এক প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু সাতটি বাক্যে নেতৃত্বের বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে—‘সত্যিকারের নেতৃত্ব আসে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।
বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং বিশ্ব মিডিয়া
- অজিত কুমার সরকার
অন্যান্য

আসলে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামে তাঁর নেতৃত্বের যেসব গুণ আমরা দেখতে পাই তাতে শুধু নেতা হওয়া নয়, একজন আদর্শ মানুষ হওয়ার শিক্ষা রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের একেকটি গুণ নিয়ে একেকটি গবেষণাগ্রন্থ রচিত হতে পারে। কিন্তু এই নিবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বিশেষ কিছু গুণের কথা সংক্ষেপে তুলে ধরার জন্য।
ছাত্রাবস্থায়ই বঙ্গবন্ধুর মধ্যে ক্যারিসমেটিক সেনস অব পলিটিকস বা ক্যারিসমেটিক রাজনীতি বোধের প্রকাশ দেখা যায়। এ কারণেই গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়ার সময়ই হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর দৃষ্টিতে আসেন। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর নেতৃত্ব বিকশিত হয় অসাধারণ সব গুণের কারণে। যেমন—তিনি ছিলেন সাহসী, কৌশলী, সৎ, ত্যাগী, ধর্মনিরপেক্ষ, অনলবর্ষী বক্তা ও যোগাযোগকারী, ভিশনারি, মানবিক ইত্যাদি। এসব গুণের কারণেই তিনি হয়ে ওঠেন বিশ্বের ক্যারিসমেটিক নেতাদের একজন। টাইম ম্যাগাজিনের ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সংখ্যায় বলা হয়, ‘ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অর্ধশতাব্দীজুড়ে যাঁরা ক্যারিসমেটিক হিসেবে আলোচিত তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মহাত্মা গান্ধী, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, জওয়াহেরলাল নেহরু। এই তালিকায় সম্ভবত আরেকটি নাম যোগ হতে যাচ্ছে, তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান।’ বিশ্বের খ্যাতনামা এনসাইক্লোপিডিয়াডটকমে বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে, ‘ক্যারিসমেটিক নেতা শেখ মুজিব তৃতীয় বিশ্বে উপনিবেশবিরোধী নেতৃত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।’ কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে সাহস ও ব্যক্তিত্বের বিশালতায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন হিমালয়সম উচ্চতার একজন মানুষ। আর তাই তিনি বঙ্গবন্ধুর মাঝে হিমালয় দেখেছিলেন। ভারতের মণিপুর ও ঝাড়খণ্ডের সাবেক গভর্নর ভেদ মারওয়া, যিনি লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের প্রথম সচিব হিসেবে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে সঙ্গী হন, তিনি বলেছেন, ‘আমার চাকরিজীবনে জওয়াহেরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধীসহ অনেক বিশ্বনেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু আমাকে বলতেই হবে, তাঁদের মধ্যে শেখ মুজিব সবচেয়ে ক্যারিসমেটিক ব্যক্তিত্ব।’ (বাসস পরিবেশিত খবর)।
বঙ্গবন্ধুর সাহসের কথা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার অনেক প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি। লন্ডনের দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের সাংবাদিক সদ্যঃপ্রয়াত সাইমন ড্রিং ‘ট্যাংক ক্র্যাশ রিভল্টস ইন পাকিস্তান’ শিরোনামে (৩০ মার্চ ১৯৭১) প্রকাশিত প্রতিবেদনে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও বঙ্গবন্ধুর দৃঢ়তার সঙ্গে আত্মগোপনে যেতে অস্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন। তিনি লিখেছেন, ‘একজন শুভাকাঙ্ক্ষী শেখ মুজিবুর রহমানকে টেলিফোনে আত্মগোপনে চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি উত্তরে বলেন, আমি যদি আত্মগোপনে চলে যাই ওরা আমাকে খোঁজার জন্য পুরো ঢাকা শহর জ্বালিয়ে দেবে।’ বঙ্গবন্ধু মৃত্যুকে ভয় পেতেন না। ‘হি টেলস ফুল স্টোরি অ্যাবাউট হিজ অ্যারেস্ট অ্যান্ড ডিটেনশন’ শিরোনামে ১৮ জানুয়ারি দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে সাংবাদিক সিডনি শনবার্গ বঙ্গবন্ধুর একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায় নিয়াজির জেলার বন্দিদের দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরিকল্পনার কথা। এ জন্য কারাগারে তাঁর সেলের অদূরেই কবর খোঁড়া হয়। বঙ্গবন্ধু এই হত্যা পরিকল্পনার কথা জেনেছেন পরে। বঙ্গবন্ধু যেটা জানতেন সামরিক ট্রাইব্যুনালের বিচারের রায়ে যেকোনো সময় তাঁর ফাঁসি হতে পারে। তাই কারা তত্ত্বাবধায়ক তাঁকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য টানাটানি শুরু করলে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘তুমি যদি ফাঁসির আদেশ কার্যকর করার জন্য আমাকে নিতে চাও, তাহলে আমাকে প্রার্থনা করার জন্য কয়েক মিনিট সময় দাও।’
বঙ্গবন্ধুর জীবনে সততাই ছিল মূল চালিকাশক্তি। সততার শিক্ষা তিনি পেয়েছেন পরিবার থেকে। বঙ্গবন্ধু তাঁর সারা জীবনে এই সততার অনুশীলন করেছেন। রাজনীতিতে কখনো মিথ্যা, ভণ্ডামির আশ্রয় নেননি। ৯ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে ‘আনডিসপুটেড লিডার অব দ্য বেংগলিস’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়, ‘নো ওয়ান অ্যাকিউসড শেখ মুজিব অব ফলস মডেস্টি।’
বঙ্গবন্ধুর মাঝে মানুষকে আকৃষ্ট করার মোহনীয় শক্তি ছিল। তিনি ছিলেন অনলবর্ষী বক্তা। ১৯৪১ সালে কলকাতায় হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলনে তিনি দুইবারের মধ্যে একবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়ার কারণে। তিনি শুধু ভালো বক্তা নন, ভালো একজন যোগাযোগকারীও। যোগাযোগবিদ্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী তিনি প্রকৃত অর্থে একজন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে সহজ ভাষা ব্যবহার করতেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি শোষণ, বঞ্চনা ও বৈষম্যের কথা তিনি এমনভাবে তুলে ধরতেন যে মানুষ প্রতিবাদী হয়ে উঠত। ভালো বক্তৃতা ও যোগাযোগকারীর গুণ থাকার কারণে তিনি খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য সম্পর্কে ১৯৭০ সালের ৯ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্ক টাইমসের বিশেষ প্রতিবেদনটিতে একজন কূটনীতিকের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, ‘এমনকি আপনি যদি তাঁর (শেখ মুজিব) সঙ্গে একাকী কথা বলেন মনে হবে ইয়াংকি স্টেডিয়ামে তিনি ৬০ হাজার মানুষের উদ্দেশে বক্তৃতা করছেন।’ ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বিশ্ব ইতিহাসের অবিস্মরণীয় উপাদানে পরিণত হয়। ইতিহাসের পর্যবেক্ষক ব্রিটিশ জ্যাকব এফ ফিল্ড বিশ্বের ৪১টি সেরা ভাষণ সংকলিত করে ‘উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস : দ্য স্পিসেস দ্যাট ইনসপায়ারড হিস্টোরি’ নামের একটি গ্রন্থ লিখেছেন। এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। জ্যাকব বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের একটি বাক্যকে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে গ্রন্থিত করেছেন এভাবে—‘রিমেম্বার অনস উই হ্যাভ শেড ব্লাড, ইউ উইল নট হেজিটেট টু শেড মোর। বাট উই উইল ফ্রি দ্য পিপল অব দিস কান্ট্রি, ইনশাআল্লাহ।’
বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী ও কৌশলী। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন। এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ২৩ বছরের আন্দোলন পরিচালনায় ছিলেন অত্যন্ত কৌশলী। তিনি ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে গণতন্ত্র, শোষণ-বৈষম্য, ধর্ম, ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যুক্ত করে তা স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত করেন। তিনি এতটাই কৌশলী ছিলেন যে গণতান্ত্রিক ধারায় আন্দোলন করেছেন এবং ১৯৭১ সালের মার্চের আগ পর্যন্ত আন্দোলনকে সহিংস রূপ নিতে দেননি। ওয়েস্টমিনস্টার টাইপের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়েও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষের জারি করা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের (এলএফও) অধীনে ১৯৭০ সালে নির্বাচনে অংশ নেন। নির্বাচনী প্রচারাভিযানের সময় এক পাকিস্তানি সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবন্ধু বলেন, নির্বাচনের পর ওই এলএফও আমি ছিঁড়ে ফেলব।
বঙ্গবন্ধু ছিলেন মানবিক গুণের অধিকারী। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে পড়াকালীন তাঁর গৃহশিক্ষক কাজী আবদুল হামিদ পরিচালিত সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মুষ্টি চাল তুলে ছাত্রদের বই, পরীক্ষার ফি, জায়গিরের খরচ জোগান দিতেন। ১৯৪৩ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে প্রায় ৫০ লাখ মানুষ না খেয়ে মারা যায়। ওই সময় বঙ্গবন্ধু মুসলিম লীগের কাউন্সিলর। লঙ্গরখানা খুলে মানুষকে খাইয়েছেন। বেকার হোস্টেলে দুপুরে ও রাতে যে খাবার বাঁচে তা বুভুক্ষুদের বসিয়ে ভাগ করে দিয়েছেন। জনগণের প্রতি ভালোবাসা ছিল প্রবল। রাজনীতিতে তিনি জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করতেন। ডেভিড ফ্রস্টের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, ‘আমার সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে, আমি আমার জনগণকে ভালোবাসি। আমার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে, আমি তাদের অত্যধিক ভালোবাসি।’ ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এমনি একজন বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী নেতাকে দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্রে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বাঙালির জাতির কপালে এঁকে দেওয়া হয় কলঙ্কতিলক। আর তাই ভারতীয় সাহিত্যিক ব্রিটিশ নাগরিক বাঙালিদের আখ্যায়িত করে ‘ইনসিডিয়াস বেংগলি’ হিসেবে। আর জার্মানির সাবেক চ্যান্সেলর উইলি ব্রান্ডথ বলেন, ‘শেখ মুজিবকে হত্যার পর কোনো বাঙালিকে বিশ্বাস করা যায় না।’
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক ও বাসসের সাবেক সিটি এডিটর
সম্পর্কিত খবর
আমাদের উৎসব, আমাদের ধর্ম
- অদিতি করিম

অবশেষে বদলে গেল মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম। গত শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানাল, শোভাযাত্রার নতুন নাম হবে ‘বর্ষবরণ আনন্দ শোভাযাত্রা’। নাম বদল নিয়ে কেউ কেউ নানা রকম কথা বলছে, কিন্তু এতে বর্ষবরণ উৎসবের কোনো ছন্দঃপতন হবে না বলেই আমার বিশ্বাস। পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রধান উৎসব।
বাংলাদেশ হাজার বছরের ঐতিহ্য লালিত একটি দেশ। এ দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যেমন মুসলমান, তেমনি বাঙালি। আমরা বাঙালি জাতি ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছি, ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে এ দেশ স্বাধীন করেছি। এ দেশের স্বাধীনতার মূলমন্ত্রের একটি ছিল সব ধর্মের সহাবস্থান। ‘বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার হিন্দু, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার মুসলমান আমরা সবাই বাঙালি’—এই চেতনাই ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূলমন্ত্র। বাঙালিরা কখনোই ধর্মীয় উগ্রবাদকে লালন করে না বা ধর্মের নামে হানাহানি, সহিংসতা পছন্দ করে না। এই অঞ্চলের ঐতিহ্য হলো প্রতিটি ধর্মের মানুষ তাদের নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করে। ঈদ উৎসবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানরা মুসলিম বাড়িতে যায়। সেমাই-পায়েস খায়, উৎসবের আনন্দ মিলেমিশে উদযাপন করে। ঠিক তেমনিভাবে দুর্গাপূজা বা ক্রিসমাসে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিস্টানরাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করে। এটি বাংলাদেশের ঐতিহ্য। এ দেশের মুসলমানরা কখনোই ধর্মান্ধ নয়। তারা অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা, ক্রোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ করার সংস্কৃতিকে লালন করে না। কিন্তু গত ১৫ বছর একটি অসাম্প্রদায়িক চেতনার নামে ধর্মহীনতার একটি সংস্কৃতিকে বিকশিত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ইসলাম ধর্মকে খাটো করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার নামে এক ধরনের প্রতারণা করা হয়েছে জাতির সঙ্গে। এ কারণেই একটি গোষ্ঠী বাঙালির উৎসবকে ধর্মের মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। এটি কখনোই করা উচিত হবে না। অতীতে যে ভুলগুলো হয়েছে, সেই ভুলের যেন পুনরাবৃত্তি আমরা না করি, সেটি আমাদের বুঝতে হবে। বাঙালিদের একটি নিজস্ব সাংস্কৃতিক চেতনা রয়েছে, কিন্তু সেই সাংস্কৃতিক চেতনায় কখনোই ধর্ম উপেক্ষিত নয়, বরং ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির একটি সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী ধর্মকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি কাজ। এই জায়গা থেকে আমাদের সরে আসতে হবে। বাংলাদেশের ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ মুসলমান। কাজেই আমাদের কোনো সংস্কৃতির মধ্যেই ধর্মকে উপেক্ষা করতে পারি না। ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির বিরোধ তৈরি করতে পারি না। সাম্প্রতিক সময়ে আমরা লক্ষ করছি যে পহেলা বৈশাখকে ঘিরে কোনো কোনো মহল বিভিন্ন রকমের বক্তব্য দিচ্ছে। তবে আশার কথা, বাংলাদেশের প্রধান ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো পহেলা বৈশাখ নিয়ে কোনো নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেনি, বরং একটি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় পহেলা বৈশাখ উদযাপনের ক্ষেত্রে একটি অংশগ্রহণমূলক নীতি গ্রহণ করেছে এবং সব গোষ্ঠীকে যুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সেটি সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। প্রতিবছর পহেলা বৈশাখের দুটি উৎসব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, অন্যটি মঙ্গল শোভাযাত্রা। বর্ষবরণ অনুষ্ঠান পাকিস্তান আমলেও হয়েছে। সদ্যঃপ্রয়াত সন্জীদা খাতুনের নেতৃত্বে ছায়ানটের এই বর্ষবরণ বাঙালি সাংস্কৃতিক উৎসবে একটি বড় অনুষঙ্গ। ষাটের দশকে আইয়ুব খানের রবীন্দ্রবিরোধী অবস্থানের বিপরীতে ছায়ানট ছিল সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের প্রেরণা। সেই থেকে এখনো ছায়ানট আমাদের গৌরব। প্রতিবছর ছায়ানটের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা বর্ষবরণ শুরু করি। কিন্তু ২০১০ সাল থেকে আমরা দেখলাম রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যাকে দিয়ে ‘সুরের ধারা’ সৃষ্টি করে ছায়ানটের বিকল্প তৈরির চেষ্টা হলো। বন্যাকে দেওয়া হলো সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। সংস্কৃতি বিভাজনের এই চেষ্টা ছিল নিন্দনীয়। এর বিপরীতে নতুন বাংলাদেশে সংস্কৃতির ঐক্য দরকার। বর্ষবরণের এই ভোরের উৎসবে আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন গোত্রের, বর্ণের মানুষ সেখানে জড়ো হয়। কোনো ধর্মীয় ভেদাভেদ সেখানে থাকে না। বর্ষবরণ যেমন কোনো ধর্মবিরোধী উৎসব নয়, তেমনি কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর উৎসব নয়। এটি সবার আনন্দ উপলক্ষ। সেভাবেই যেন এই উৎসবটি হয়। তাই বর্ষবরণ উৎসবটিকে রাজনীতি এবং সব ধরনের বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখতেই হবে। আমাদের এই উৎসব এবং আমাদের সংস্কৃতিকে আমাদেরই লালন করতে হবে। এটি আমাদের বাঙালি চেতনার একটি বড় অনুষঙ্গ। ছায়ানটের উৎসবের সঙ্গে কখনোই ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। বরং লক্ষ করা যায় যে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরাও এই উৎসবে যোগ দেয়, প্রাণভরে অনুষ্ঠান উপভোগ করে এবং বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নেয়।
দ্বিতীয় যে উৎসবটি নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বিতর্ক হচ্ছে, তা হলো মঙ্গল শোভাযাত্রা। মঙ্গল শোভাযাত্রা জাতিসংঘের ইউনেসকো কর্তৃক বিশ্বসংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এটির মূল উদ্যোক্তা, আয়োজক মূলত চারুকলা বিভাগ। এই শোভাযাত্রার মাধ্যমে নববর্ষের একটি চেতনাকে লালন করা হয়। সেই চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে তরুণ-তরুণীরা বর্ষবরণের উৎসব করে। শোভাযাত্রার উৎসবটি নিয়ে অতীতে কখনোই বিতর্ক লক্ষ করা যায়নি। কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হলো, সাবেক সরকার সব কিছু দলীয় ও নিজেদের কুক্ষিগত করতে গিয়ে মঙ্গল শোভাযাত্রাকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছে। আর এই ব্যবহারের কারণেই মঙ্গল শোভাযাত্রা নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ এবং বিতর্কিত হয়েছে। মঙ্গল শোভাযাত্রার মধ্যে অতীতে কখনো কোনো রাজনৈতিক আবহ আনা হতো না। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর এর মধ্যে রাজনীতি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভিপ্রায় অনুযায়ী মঙ্গল শোভাযাত্রার থিম ঠিক করা হতো। এটি সাবেক সরকারের সমস্যা বা যারা অতি উৎসাহী, চাটুকারদের সমস্যা। এটি মঙ্গল শোভাযাত্রার সমস্যা নয়। এবার যে শোভাযাত্রার মূল বিষয় নির্বাচিত করা হয়েছে, তা অত্যন্ত ভালো। ছায়ানটের উৎসবের সঙ্গে যেমন কোনো ধর্মের বিরোধ নেই, তেমনি আনন্দ শোভাযাত্রার সঙ্গে ধর্মের বিরোধ থাকার কোনো কারণ নেই। কারণ এটি নতুন বর্ষবরণের একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের উৎসব। তবে বিভিন্ন সময়ে এই উৎসব হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের ভাষা। যেমন নব্বইয়ে স্বৈরাচারীর পতনের পর ওই উৎসব ছিল স্বৈরাচারের পতন উদযাপনের উৎসব, ঠিক তেমনি এবার ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পর প্রথম পহেলা বৈশাখ হচ্ছে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনগণের বিজয় উৎসব। কাজেই এই উৎসবকে আমাদের অবগাহন করতেই হবে। আমরা এবার দেখেছি ঈদ উৎসবে এক ধরনের বৈচিত্র্য আনা হয়েছিল। আমাদের পুরনো দিনের সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা ছিল ঈদ আয়োজনে। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ধন্যবাদ পেতেই পারেন। কারণ তরুণদের জন্য তিনি ঈদকে উৎসবমুখর করেছিলেন। এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে কিছু মহল এর সমালোচনা করেছে। কিন্তু আমার মনে হয় যে এই সমালোচনা করা উচিত নয়। প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গে ধর্মকে গুলিয়ে ফেলা উচিত নয়, তেমনি যেকোনো সংস্কৃতির কর্মকাণ্ডকে ধর্মের প্রতিপক্ষ বানানো ঠিক নয়। দুটির পাশাপাশি অবস্থান চলবে। সংস্কৃতি ও ধর্ম রেললাইনে দুটি ধারার মতো। আমাদের সংস্কৃতিতে প্রচুর ধর্মীয় উপাদান আমরা গ্রহণ করেছি। বিশেষ করে এই অঞ্চলে ইসলামের জাগরণের পর আমাদের সংস্কৃতির মধ্যে ইসলামের প্রভাব অনস্বীকার্য।
ধর্ম কখনোই আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে ধর্মকে যারা সংস্কৃতির প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে, তারা আসলে বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এক সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ রাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করে, যেটি বাংলাদেশ কখনোই নয়। এ দেশের মুসলমানরা যেমন পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে, তেমনি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। ধর্ম যার যার—এই চেতনায় এই বাঙালি জাতিই বিকশিত হয়েছে, বেড়ে উঠেছে। কাজেই আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি এই দুটি সত্তা গুলিয়ে ফেললে চলবে না। দুটি সত্তার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রাখতে হবে। অতীতে আমরা দেখেছি যে প্রগতিশীলতা চর্চার নামে ধর্মহীনতার সংস্কৃতিকে উসকে দেওয়া হয়েছে। এটি যেমন অগ্রহণযোগ্য, তেমনি ধর্মকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সংস্কৃতিকে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করাও অগ্রহণযোগ্য। দুটির মধ্যে আমাদের ভারসাম্য বজায় রাখা দরকার। আর এই ভারসাম্যই এ দেশের শক্তি, আমাদের ঐতিহ্য।
লেখক : নাট্যকার ও কলাম লেখক
auditekarim@gmail.com
ভবিষ্যতের সংঘাত ঠেকাতে এখনই ব্যবস্থা নিন
- গাজীউল হাসান খান
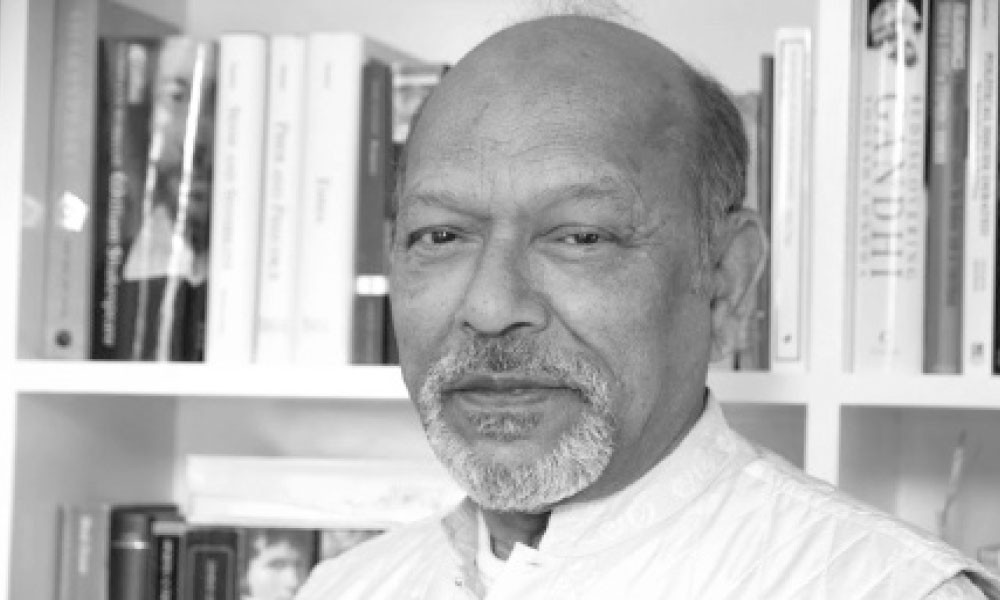
পতিত হাসিনা সরকারের দীর্ঘ শাসনকালের একটা সময়ে, সম্ভবত শুরু থেকে মাঝামাঝি কোনো অবস্থায়, দেশের কোনো একটি গণমাধ্যমে একটি চমৎকার স্লোগান দেখতে পেতাম। সেটি হচ্ছে : ‘আপনি বদলে যান, সমাজ বদলে যাবে।’ চারিত্রিক দিক থেকে আমরা সবাই যদি পরিশুদ্ধ হতে পারি, তাহলে সমাজ, জাতি বা দেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বদলে যাবে। এটি আমাদের ধর্মীয় অনুশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য দিকও।
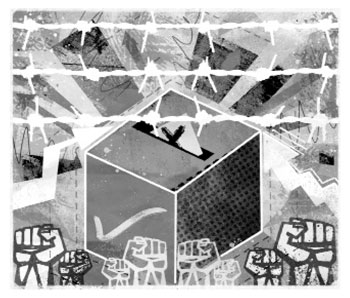 দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই তাদের প্রত্যাশিত নির্বাচনটি সম্পন্ন করতে চায়। সেই লক্ষ্যে তারা নির্বাচনের একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ চেয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে। সে লক্ষ্যে আগামী ১৬ এপ্রিল বিএনপি নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার একটি সাক্ষাৎ বা আলোচনার দিন ধার্য করা হয়েছে। এর আগে প্রধান উপদেষ্টা কয়েকবারই বলেছেন, চলমান সংস্কারের পরিসর সীমিত হলে ডিসেম্বরে নির্বাচন অসম্ভব নয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ অন্য সব ‘স্টেকহোল্ডার’ বা এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াশীল অংশগুলোর সঙ্গে কথা বলে সেটি নির্ধারণ করা হবে। আর কাঙ্ক্ষিত কিংবা অতি আবশ্যকীয়ভাবে সংস্কারের পরিসর কিছুটা বাড়লে আগামী জুনে নির্বাচন হতে পারে। সে আভাস অতীতে বহুবার দেওয়া হয়েছে এবং এখনো সে ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন নিয়ে নানা মহলে একটি ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।’ সে কারণেই তারা (বিএনপি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ চায়। এখানেও আবার একই কথা। ডিম আগে, না মুরগি আগে। কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সংস্কার আগে, না নির্বাচন আগে। তা ছাড়া এখানে আরো একটি প্রত্যাশিত বিষয় কাজ করছে। আর তা হচ্ছে, জরুরি সংস্কারগুলো আলোর মুখ না দেখলে জুলাই-আগস্ট বিপ্লব বা অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ বিফলে যাবে। দ্বিতীয় রিপাবলিক গঠন কিংবা নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় মাঠে মারা যাবে। সম্প্রতি নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাদের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের নেতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে গণবিপ্লব বা অভ্যুত্থান-উত্তর আওয়ামী লীগকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে এই দুটি দল একমত হয়েছে। মোটামুটি চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে তারা। আর তা হচ্ছে, গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগের বিচার নিশ্চিত করা, বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল করা, এ পর্যায়ে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিত রাখা এবং নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগের বিচারের পদক্ষেপ দৃশ্যমান করতে হবে। তা ছাড়া অন্যান্য সংস্কার নিয়েও পারস্পরিক প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করা হয়েছে।
দেশের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই তাদের প্রত্যাশিত নির্বাচনটি সম্পন্ন করতে চায়। সেই লক্ষ্যে তারা নির্বাচনের একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ চেয়েছে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে। সে লক্ষ্যে আগামী ১৬ এপ্রিল বিএনপি নেতাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার একটি সাক্ষাৎ বা আলোচনার দিন ধার্য করা হয়েছে। এর আগে প্রধান উপদেষ্টা কয়েকবারই বলেছেন, চলমান সংস্কারের পরিসর সীমিত হলে ডিসেম্বরে নির্বাচন অসম্ভব নয়। আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ অন্য সব ‘স্টেকহোল্ডার’ বা এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত ক্রিয়াশীল অংশগুলোর সঙ্গে কথা বলে সেটি নির্ধারণ করা হবে। আর কাঙ্ক্ষিত কিংবা অতি আবশ্যকীয়ভাবে সংস্কারের পরিসর কিছুটা বাড়লে আগামী জুনে নির্বাচন হতে পারে। সে আভাস অতীতে বহুবার দেওয়া হয়েছে এবং এখনো সে ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছে। কিন্তু এর মধ্যে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন বলেছেন, ‘আগামী নির্বাচন নিয়ে নানা মহলে একটি ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়েছে।’ সে কারণেই তারা (বিএনপি) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ চায়। এখানেও আবার একই কথা। ডিম আগে, না মুরগি আগে। কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে সংস্কার আগে, না নির্বাচন আগে। তা ছাড়া এখানে আরো একটি প্রত্যাশিত বিষয় কাজ করছে। আর তা হচ্ছে, জরুরি সংস্কারগুলো আলোর মুখ না দেখলে জুলাই-আগস্ট বিপ্লব বা অভ্যুত্থান সম্পূর্ণ বিফলে যাবে। দ্বিতীয় রিপাবলিক গঠন কিংবা নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় মাঠে মারা যাবে। সম্প্রতি নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাদের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের নেতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে গণবিপ্লব বা অভ্যুত্থান-উত্তর আওয়ামী লীগকে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে এই দুটি দল একমত হয়েছে। মোটামুটি চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে তারা। আর তা হচ্ছে, গণহত্যার দায়ে আওয়ামী লীগের বিচার নিশ্চিত করা, বিচার না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নিবন্ধন বাতিল করা, এ পর্যায়ে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম স্থগিত রাখা এবং নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগের বিচারের পদক্ষেপ দৃশ্যমান করতে হবে। তা ছাড়া অন্যান্য সংস্কার নিয়েও পারস্পরিক প্রস্তাবগুলো উত্থাপন করা হয়েছে।
মাঠ পর্যায়ে নির্বাচনী রাজনীতি দ্রুত এগোনো সম্ভব না হলেও জনগণের পর্যায়ে রাজনৈতিক কথোপকথন এগোচ্ছে আশাতীতভাবে। এখানে উল্লেখ্য, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে একটি জাতীয় সরকারের রূপ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে গণ অধিকার পরিষদ। সেই প্রস্তাবিত সরকারের অধীনেই সংস্কার ও সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে গণ অধিকার পরিষদ। তা ছাড়া এ পর্যন্ত ৩০টির বেশি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের ব্যাপারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছে। এগুলো অবশ্যই পর্যালোচনার দাবি রাখে। এগুলো বিভিন্ন অজুহাতে পাশ কাটিয়ে দ্রুত নির্বাচনের দিকে ধাবিত হলে যেমন জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানকে অবহেলা কিংবা অগ্রাহ্য করা হবে, তেমনি বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নগুলোকেও ঝুলিয়ে রাখা সমীচীন হবে না। তাহলে আমরা ক্রমে ক্রমে নিজের অজান্তেই আমাদের মূল লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাব। যদিও অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান অধ্যাপক ইউনূসের জন্য এটি একটি ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’ পরিস্থিতি, তবু তিনি একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিত্ব। তাঁর কাছে মানুষ কোনো নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থোদ্ধারের বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাক, সেটি চায় না; চায় বৃহত্তরভাবে জাতীয় স্বার্থ অর্জনের ক্ষেত্রে আপসহীন ও সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত। এতে তাঁর নীতি-নৈতিকতার দিকটিই অভ্রান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। নতুবা জাতি হিসেবে আমরা আবার আগের অবস্থানেই ফিরে যাব। এতে বর্তমান জটিল বিশ্বপরিস্থিতিতে আমরা একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রেও পরিণত হতে পারি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বর্ধিত কর আরোপের (ট্যারিফ) প্রক্রিয়া যেমন আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি সংকট সৃষ্টি করবে, তেমনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধাদি বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণাও আমাদের জন্য একটি অশনিসংকেত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ভারতের ভূমি ব্যবহার করে আমরা নেপাল ও ভুটানে আমাদের পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করতে পারব না। এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। এখানে জাতীয় নির্বাচন ডিসেম্বরে, না জুনে সম্পন্ন হবে, সেগুলো প্রয়োজনীয় হলেও জরুরি কোনো জাতি বিধ্বংসীমূলক সংকট নয়।
বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অত্যন্ত হুঁশিয়ার ও বিচক্ষণ। অতীতে বিভিন্ন সময় আধিপত্যবাদ কিংবা স্বৈরশাসনের কারণে তারা যথাসময়ে অনেক কাজে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি, কিন্তু সুযোগ পেলে তারা কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে থাকে না। তারা এগিয়ে আসতে পিছপা হয় না। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক নিঃস্বার্থ মানুষ রাজনীতিকদের তুলনায় চিন্তা-ভাবনার জগতে অনেক এগিয়ে থাকে। এর মূল কারণ তারা বেশির ভাগ রাজনীতিকের তুলনায় ব্যক্তি কিংবা কায়েমি স্বার্থে কাজ করে না। তারা সর্বাগ্রে ভাবে দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে। এমন একটি অবস্থার প্রেক্ষাপটে জনগণের বিভিন্ন অংশ থেকে সম্প্রতি একটি কথা চাউর হয়েছে। এখনো সে বক্তব্যটি বেগবান বা তেমনভাবে সমর্থন লাভ না করলেও প্রস্তাব করা হয়েছে, দেশে অদূর ভবিষ্যতে একটি গণভোট অনুষ্ঠান করা যায় কি না? আমাদের সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন কিংবা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করার লক্ষ্যে আমরা অধ্যাপক ইউনূসের নেতৃত্বে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি সরকার চাই কি না? যেভাবে বা যে পদ্ধতিতে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কিংবা পরবর্তী সময়ে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনের বৈধতা দিতে গণভোট সংঘটিত করা হয়েছিল, বর্তমানে অধ্যাপক ইউনূসের শাসনকালকে বৈধভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তেমন একটি জনমত নেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কি না? উল্লিখিত বিষয়াবলির সব কিছুই এখনো মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার বহিঃপ্রকাশের মধ্যে রয়েছে, শক্তপোক্তভাবে রাজনৈতিক মহলে এখনো ঠাঁই পায়নি। দানা বেঁধে ওঠেনি একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব হিসেবে। তবে এই বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষ যে ভাবছে না, তেমন নয়। তা ছাড়া পূর্বনির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব হলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও তথ্যাভিজ্ঞ মহল অধ্যাপক ইউনূসকে দেশ গঠন বা পরিচালনায় সম্পৃক্ত করতে যথেষ্ট আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে। সবার ধারণার ভিত্তি হচ্ছে, অধ্যাপক ইউনূস নিজ দেশ এবং আন্তর্জাতিক দিক থেকে সবার কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। বর্তমানে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে যে সমস্ত সংকট বা চ্যালেঞ্জ ধেয়ে আসছে, সেগুলো মোকাবেলা করতে অধ্যাপক ইউনূসের মতো শক্তপোক্ত অবস্থানে থাকা একজন সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তির প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অধ্যাপক ইউনূস কিংবা তাঁর শুভানুধ্যায়ীমহল থেকে কোনো প্রচারাভিযান চালানো হয়নি, এগুলো সাধারণ মানুষের চিন্তা-চেতনা থেকে উৎসারিত অভিব্যক্তি বলে মনে করা হচ্ছে।
পরিশেষে যে বিষয়টি শুধু আমাকে নয়, দেশের আপামর জনসাধারণকে ভাবিয়ে তুলছে, তা হচ্ছে সংস্কার ও নির্বাচনের প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দলের একটি ঐকমত্যে পৌঁছা। বর্তমানে সংস্কার ও নির্বাচনের প্রশ্নে তাদের মধ্যে বিশাল ফারাক বা ব্যবধান লক্ষ করা যাচ্ছে। বিএনপি ছাড়া জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি কিংবা অন্য অনেকের কাছে সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা ছাড়া রয়েছে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব ও গণহত্যার দায়ে তাদের নেতা-নেত্রীদের বিচারের প্রশ্নগুলো। এগুলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এগুলো এখনই সুরাহা না হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবিরোধকে কেন্দ্র করে রক্ত ঝরতে পারে। বেড়ে যেতে পারে অন্তর্দলীয় রাজনৈতিক সহিংসতা। বিভিন্ন সংস্কার ও দ্রুত নির্বাচন অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিএনপির বিভিন্ন বক্তব্য তাদের প্রতিপক্ষের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক ও আস্থার অভাব সৃষ্টি করেছে। কেউ কাউকে কাঙ্ক্ষিতভাবে আস্থায় নিতে পারছে না। এই অবস্থায় সংস্কার কিংবা নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব নয়। বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার কারো কোনো ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় বসেনি। বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী ছাত্র-জনতা, যারা অন্তর্বর্তী সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে, তাদের কাছে প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করা বর্তমান শাসকদের একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে মানুষ মনে করে। সুতরাং তার প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণের ব্যাপারে সরকারকে হুঁশিয়ার হতে হবে। এ কথা ঠিক যে বর্তমান দ্বিমুখী চাপের মুখে একটি অস্থায়ী সরকার কতটুকু করতে পারে।
অন্তর্বর্তী সরকারের আগের রূপরেখায় অধ্যাপক ইউনূসের সরকার ক্ষমতায় আসেনি। এটি একটি গণবিপ্লব বা অভ্যুত্থান-উত্তর সরকার। এতে শিশু, নারী, ছাত্র-জনতাসহ প্রায় দুই হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এই আত্মত্যাগ নিছক একটি নির্বাচনের মাধ্যমে অন্য কারো ক্ষমতায় আসার জন্য নয়। সুতরাং এই লোমহর্ষক ও অমানবিক ঘটনার ভবিষ্যতে যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং এই হত্যাকাণ্ডের যাতে সুষ্ঠু বিচার হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। সে কারণে প্রয়োজন হলে বিভিন্ন দলকে অন্তর্দলীয়ভাবে আলোচনায় বসতে হবে। নির্বাচনের আগেই তাদের অমীমাংসিত বিষয়াদি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। তাদের মধ্যে বিরাজিত ব্যবধান ঘোচাতে হবে। নতুবা কোনো নির্বাচনই শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে না। নির্বাচনের কয়েক মাসের মধ্যেই রাজপথে নামবে সরকারবিরোধীরা। সেদিনের সেই দ্বন্দ্ব, সংঘাত ও রক্তপাত ঠেকাতে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে এখনই উদ্যোগ নিতে হবে সম্ভাব্য ব্যবধান ঘুচিয়ে একটি ঐকমত্যে পৌঁছতে।
লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
gaziulhkhan@gmail.com
নারী বিশ্বকাপ ক্রিকেটে খেলতে চায় বাংলাদেশ
- ইকরামউজ্জমান

হরহামেশাই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খেলার ইভেন্টে খেলোয়াড় ও ক্রীড়াবিদরা দেশকে প্রতিনিধিত্ব করছেন। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ঘাটতি হলো পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভাব। মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা পুরোপুরি সম্ভব হয় না। সম্ভব হয় না নিজেদের ভাবাবেগ সামাল দেওয়া—এটি আমার পর্যবেক্ষণ।
একাত্মবোধ, অংশগ্রহণ আর দায়বদ্ধতা একটি টিমের প্রধান চাবিকাঠি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই যে আমাদের নারী ক্রিকেটাররা কয়েক বছর ধরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলছেন—তাঁদের রানের ইনিংস কিন্তু বড় করতে পারছেন না। এটি বড় করতে হবে। আর এটি সবাই মিলেই খেলে করতে হবে।
নারী ক্রিকেট বিকেন্দ্রীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। নারী ক্রিকেটকে ঢাকায় কেন্দ্রীভূত না রেখে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আর এটি না করার বিরূপ প্রতিক্রিয়া এখন লক্ষ করা যাচ্ছে। প্রধান বিষয় হলো নতুন নতুন খেলোয়াড় পাওয়া যাচ্ছে না। খেলোয়াড় সৃষ্টির সুযোগ যে সীমিত। এটি বুঝতে হবে এখনকার নারী প্রজন্ম যাঁরা ক্রিকেট খেলছেন, ক্রিকেটে উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তাঁরা যেকোনো সময়ের তুলনায় সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজন্ম। তাঁদের মেধা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো মানেই নারী ক্রিকেটে পরিবর্তন সাধিত হওয়া। হ্যাঁ, রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে যাবে না, বিশ্বাস নিয়ে পরিবর্তনের জন্য কাজের সূচনা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্ববোধের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। নারী ক্রিকেট নিয়ে কাজ করা তো জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট।
 নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাছাইয়ে খেলার জন্য নিগার সুলতানার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নারী দল এখন পাকিস্তানে অবস্থান করছে। নারী দলের লক্ষ্য বাছাই পর্বের বাধা উতরে বিশ্বকাপ খেলা। সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ নারী দল সরাসরি ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দলের বিপক্ষে ২-১-এ সিরিজ হারাতে এখন বাছাই পর্বে খেলতে হচ্ছে। চূড়ান্ত বিশ্বকাপে খেলাটা বাংলাদেশ নারী দলের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের নারী ক্রিকেটের সরাসরি ভবিষ্যৎ ও আগামী দিনের কার্যক্রম। এরই মধ্যে বাংলাদেশ নারী দল স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছে এবং জয়ী হয়েছে। এটি অবশ্যই আত্মবিশ্বাস আরো সুসংহত করার জন্য কার্যকর। তবে এই খেলায় কিছু পর্যবেক্ষণ আছে। আর তা হলো উইকেটে সেট হয়েও ইনিংস বড় করতে পারছেন না নারী দলের ব্যাটাররা। এই বিষয়টি টিম ম্যানেজমেন্ট ও খেলোয়াড়দের ভাবার বিষয়। নারী দলের জন্য ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এরই মধ্যে ছয়টি দল বিশ্বকাপের জন্য কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। আর দুটি দল কোয়ালিফাই করবে পাকিস্তানে বাছাই খেলে। এই দলগুলোর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী, যদিও ক্রিকেটে বড় আর ছোট প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কোনো কিছু নেই। সব প্রতিপক্ষকেই সমীহ করতে হবে। দিনের খেলায় ঝলসে উঠে যেকোনো দল যেকোনো দলকে পরাজিত করতে পারে। পাকিস্তানের উইকেটে রান থাকে সব সময়। এই উইকেটে যদি সবাই মিলে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দলের প্রয়োজনে ব্যাট করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই ভালো কিছু আশা করা সম্ভব। আর বোলিং করতে হবে মাথা খাটিয়ে এবং গুছিয়ে। স্বাগতিক পাকিস্তান নারী দল মরিয়া কোয়ালিফাই করার জন্য। ওদের পুরুষ দল তো ব্যর্থতার মিছিল বড় করেই চলেছে।
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাছাইয়ে খেলার জন্য নিগার সুলতানার নেতৃত্বে বাংলাদেশ নারী দল এখন পাকিস্তানে অবস্থান করছে। নারী দলের লক্ষ্য বাছাই পর্বের বাধা উতরে বিশ্বকাপ খেলা। সুযোগ পেয়েছিল বাংলাদেশ নারী দল সরাসরি ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার। কিন্তু ওয়েস্ট ইন্ডিজ নারী দলের বিপক্ষে ২-১-এ সিরিজ হারাতে এখন বাছাই পর্বে খেলতে হচ্ছে। চূড়ান্ত বিশ্বকাপে খেলাটা বাংলাদেশ নারী দলের জন্য অত্যন্ত জরুরি। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেশের নারী ক্রিকেটের সরাসরি ভবিষ্যৎ ও আগামী দিনের কার্যক্রম। এরই মধ্যে বাংলাদেশ নারী দল স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলেছে এবং জয়ী হয়েছে। এটি অবশ্যই আত্মবিশ্বাস আরো সুসংহত করার জন্য কার্যকর। তবে এই খেলায় কিছু পর্যবেক্ষণ আছে। আর তা হলো উইকেটে সেট হয়েও ইনিংস বড় করতে পারছেন না নারী দলের ব্যাটাররা। এই বিষয়টি টিম ম্যানেজমেন্ট ও খেলোয়াড়দের ভাবার বিষয়। নারী দলের জন্য ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এরই মধ্যে ছয়টি দল বিশ্বকাপের জন্য কোয়ালিফাই করে ফেলেছে। আর দুটি দল কোয়ালিফাই করবে পাকিস্তানে বাছাই খেলে। এই দলগুলোর মধ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তান বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী, যদিও ক্রিকেটে বড় আর ছোট প্রতিদ্বন্দ্বী বলে কোনো কিছু নেই। সব প্রতিপক্ষকেই সমীহ করতে হবে। দিনের খেলায় ঝলসে উঠে যেকোনো দল যেকোনো দলকে পরাজিত করতে পারে। পাকিস্তানের উইকেটে রান থাকে সব সময়। এই উইকেটে যদি সবাই মিলে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে দলের প্রয়োজনে ব্যাট করতে পারেন, তাহলে অবশ্যই ভালো কিছু আশা করা সম্ভব। আর বোলিং করতে হবে মাথা খাটিয়ে এবং গুছিয়ে। স্বাগতিক পাকিস্তান নারী দল মরিয়া কোয়ালিফাই করার জন্য। ওদের পুরুষ দল তো ব্যর্থতার মিছিল বড় করেই চলেছে।
বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচ খেলেছে গত ১০ এপ্রিল থাইল্যান্ডের বিপক্ষে। ১৭৮ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে বাংলাদেশ। এর পরের ম্যাচ ১৩ এপ্রিল আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। এরপর ১৫, ১৭ ও ১৯ এপ্রিল খেলবে যথাক্রমে স্কটল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে এই দুটি খেলা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই দুটি খেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নারী দলের ভাগ্য। প্রতিটি খেলাই বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জ। ছন্দ ধরে রেখে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। প্রতিটি জয় তো অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে। ক্রিকেটের লড়াইয়ে মনঃসংযোগ গুরুত্বপূর্ণ। সব কিছু ছেড়ে শুধু খেলার পৃথিবীতে বিচরণ।
৯ থেকে ১৯ এপ্রিল পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের খেলা ঘিরে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। ওয়ানডেতে বাংলাদেশ সহনীয় দলের কাতারে অবস্থান করছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও পাকিস্তানকে বাংলাদেশ নারী দল আগেও পরাজিত করেছে। অবশ্যই ওয়েস্ট ইন্ডিজ বাংলাদেশের নারী দলের জন্য সবচেয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, যদিও স্কটল্যান্ডের সঙ্গে ১১ রানে হেরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিছুটা পিছিয়ে গেছে। অনেক দিন ধরে নারী দলের সবাই একসঙ্গে খেলছেন। এতে তাঁদের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া আছে। একে অন্যের সামর্থ্য ও যোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন। সবাই মিলে ভালো খেলা অবশ্যই সম্ভব।
নারী ঢাকা প্রিমিয়ার লীগ খেলেই দলটি গেছে বিশ্বকাপের বাছাইয়ে খেলতে। এই লীগ সাহায্য করেছে ক্রিকেটারদের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে। ক্রিকেটাররা খেলার সুযোগ পেয়েছেন। পেয়েছেন সুযোগ তাঁদের সবলতা ও দুর্বলতা নির্ণয়ের। বিসিবি নারী ঢাকা প্রিমিয়ার লীগকে এগিয়ে এনেছে এবার নারী ক্রিকেটারদের প্রস্তুতি পর্বকে কার্যকর করার জন্য। সময়মতো এই টুর্নামেন্টের আয়োজনের জন্য বিসিবিকে ধন্যবাদ। কেননা এরপর প্রচণ্ড গরমে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন কোনোমতেই অর্থবহ হতো না।
লেখক : কলামিস্ট ও বিশ্লেষক। সাবেক সিনিয়র সহসভাপতি, এআইপিএস এশিয়া। আজীবন সদস্য, বাংলাদেশ স্পোর্টস প্রেস অ্যাসোসিয়েশন প্যানেল রাইটার, ফুটবল এশিয়া
ভাষার সৌন্দর্য রক্ষা আমাদের কর্তব্য
- আবদুস সাত্তার মোল্লা
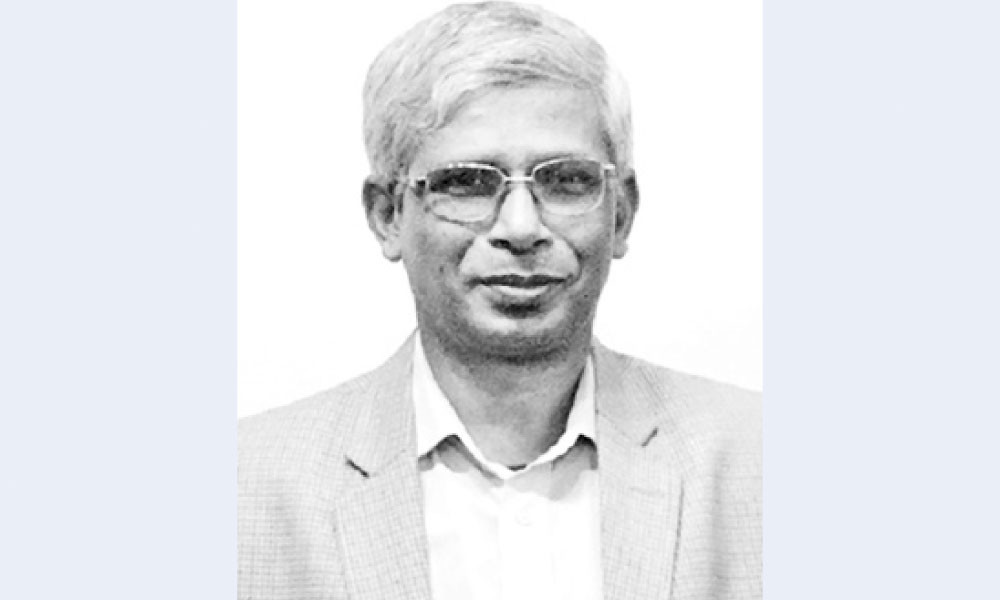
১৯৮৫ সালে স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ তাঁর গদি রক্ষার স্বার্থে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাঁচ মাস বন্ধ রেখেছিলেন। ওই পাঁচ মাস আমরা ক্যাম্পাসের বাইরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম এবং ওই সময়টা ‘এরশাদ ভ্যাকেশন’ নামে বেশ খ্যাতি পেয়েছিল। ওই ভ্যাকেশন শুরু হওয়ার আগে থেকেই সংগীতজ্ঞ সন্জীদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হকের ‘কণ্ঠশীলনে’ ক্লাস শুরু করেছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে হতো ভাষা শুদ্ধ করে উচ্চারণ শেখানোর এই কোর্স।
তরুণ সৃষ্টিশীলদের মুখেও শোনা যায় বাংলা বাক্যে সো, বাট অহরহ আওড়ানো হচ্ছে! ভাষাকে অবশ্যই সতত নতুন শব্দ গ্রহণে রাজি থাকতে হয় ভাষার উৎকর্ষের স্বার্থেই। ধরুন, এই অঞ্চলের মানুষ পিঁড়ি ও মোড়ায় বসত; চেয়ার-টেবিল ছিল না। পশ্চিমাদের কাছে চেয়ারে বসে টেবিলে লেখাপড়া ও খাওয়াদাওয়া করা শিখেছে।
আমাদের নিজ মাতৃভাষায় কয়েক প্রকার ‘কিন্তু’ আছে। অব্যয় কিন্তু এবং বাক্যালংকার কিন্তু তাদের অন্যতম।
আমাদের দেশে টেলিফোন ছিল না। এটি এসেছে ইউরোপ থেকে। আমরা ‘দূরালাপনী’ বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি; ওটি টেকেনি।
বেতার/রেডিওর আবিষ্কারক আমাদের জগদীশ চন্দ্র বসু হলেও এর কৃতিত্ব চলে গেছে ইতালির মার্কনির কাছে (১৯০০)। তাই বলা যায় বেতার/রেডিও আমাদের নয়, ইউরোপ থেকে এসেছে। সুতরাং রেডিও, আমজনতার ‘রেডু’ বেতারের চেয়ে বেশি ব্যবহৃত শব্দ। আমরা যন্ত্রটির সঙ্গে ‘রেডিও’ শব্দটি নিজের করে নিয়েছি।
টেলিভিশন অনেক পরে এসেছে, শুরুটা ১৯২৫ সালে আমেরিকায়। কিন্তু সেটি ছবিসহ দেখতে লেগেছে আরো প্রায় ২০ বছর। আমাদের তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে এলো বোধ হয় ১৯৬০-এর দশকে। জিনিসটি যখন বিদেশ থেকে এসেছে, টেলিভিশন নামটিকেও নিজের করতে আমাদের কোনো দ্বিধা থাকতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গ ‘দূরদর্শন’ টেকাতে পেরেছে। আমরা দিব্যি টেলিভিশন এবং তার সংক্ষিপ্ত রূপ টিভিকে নিজের করে নিয়েছি।
এই টেলিভিশনের অনেক মফস্বল সাংবাদিককে বলতে শুনি বাক্যের এমাথা, ওমাথায় অন্তত দুইবার ‘কিন্তু’ বাক্যালংকার ব্যবহার করছেন। আর কয়েকবার বলছেন ‘আসলে’! আমরা টেলিভিশনে তো সব আসল কথাই শুনতে চাই; কোনো নকল কথা তো শুনতে চাই না। তাহলে বারে বারে ‘আসলে’ বলে সে/তিনি আসল কথা বলছে/বলছেন বলে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কেন?
অনেকে প্রায় এবং অধিক, যেমন প্রায় শতাধিক, প্রায় লক্ষাধিক—শব্দ ব্যবহার করেন। অঙ্কটি যদি নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়, তা লিখতে/বলতে কখনো ‘প্রায়’ ব্যবহার করা যায় না।
বিশ্বে খুব কম জাতি আছে, যাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পেতে রাজপথে মিছিল করতে হয়েছে, রক্ত দিতে হয়েছে। জাতীয় সংসদে প্রতিবাদে ফেটে পড়তে হয়েছে, চিৎকার করতে হয়েছে (ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত) বা রাগে-ক্ষোভে অধিবেশন বর্জন করে রাস্তায় এসে তরুণদের সঙ্গে যোগ দিতে হয়েছে (মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ)। কাউকে কাউকে কলম ধরতে হয়েছে (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ)। নিজ ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে জীবন দিতে হয়েছে বলে শহীদদের জন্য ‘মিনার’ গড়ে তুলতে হয়েছে, মিনার রাষ্ট্রযন্ত্র ভেঙে ফেলেছে; আবার গড়ে তোলা হয়েছে শহীদ মিনার।
এমন জাতির কেউ খামখেয়ালি করে মাতৃভাষার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবে, তা তো হতে পারে না। বাংলা একাডেমি এবং খোদ সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে জেগে উঠে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে জাতীয় সংসদে আইন করে, রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষর নিয়ে মাঠে বাস্তবায়ন করা জরুরি কর্তব্য মনে করি।
লেখক : শিক্ষা গবেষক, নিবন্ধকার এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক (বিসিএস সাধারণ শিক্ষা)
asmolla61@yahoo.com



