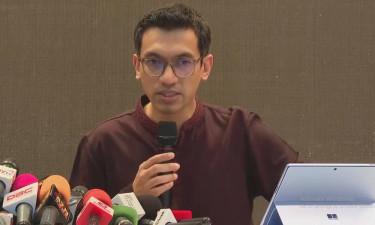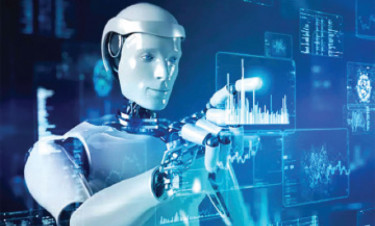বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বৈদেশিক বিনিয়োগ, দেশীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ অথবা প্রবাসীদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে খুবই প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৫ লাখ থেকে ১৮ লাখ পর্যন্ত উচ্চশিক্ষিত অর্থাৎ স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী বেকার রয়েছেন। দেশে প্রতিবছর আট লাখেরও বেশি নতুন গ্র্যাজুয়েট বের হচ্ছেন, কিন্তু উচ্চশিক্ষিত গ্র্যাজুয়েটদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তেমনভাবে সৃষ্টি হচ্ছে না।
বৈদেশিক বিনিয়োগ বাড়াতে সঠিক উদ্যোগ প্রয়োজন
- ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল

 বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে রেডিমেড গার্মেন্টসশিল্পের বিকাশ এবং প্রবাসীদের মাধ্যমে প্রেরিত রেমিট্যান্সের অবদান ছিল। মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে ইলেকট্রনিকস ও ইলেকট্রিক্যাল শিল্পসহ অন্যান্য খাতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশ দুটিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, বেড়েছে রপ্তানি আয় এবং বেড়েছে উৎপাদন। মালয়েশিয়া অত্যন্ত সফলভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে সে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পেছনে রেডিমেড গার্মেন্টসশিল্পের বিকাশ এবং প্রবাসীদের মাধ্যমে প্রেরিত রেমিট্যান্সের অবদান ছিল। মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে ইলেকট্রনিকস ও ইলেকট্রিক্যাল শিল্পসহ অন্যান্য খাতে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগের ফলে দেশ দুটিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, বেড়েছে রপ্তানি আয় এবং বেড়েছে উৎপাদন। মালয়েশিয়া অত্যন্ত সফলভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে সে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।
আমরা বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আগ্রহী করতে পারছি না এবং বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে বিনিয়োগের জন্য আদর্শ স্থান মনে করছেন না। প্রথমত, এটা অনুধাবন করা প্রয়োজন যে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে দেশে বিনিয়োগ করানো সম্ভব না হলে উচ্চশিক্ষিত বেকার সমস্যার সমাধান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয়বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং ১০-১২ বছরের টার্গেট নিয়ে দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মহাপরিকল্পনা করা প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত কম বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট হওয়ার কারণগুলো শনাক্ত করে সেগুলো দূর করে বিনিয়োগবান্ধব নীতি প্রণয়ন ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা), বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং অথরিটি (বেপজা) এবং বিভিন্ন জেলার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করা প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট টার্গেট অর্জনে ফোকাস করা প্রয়োজন। বর্তমানে কিছু কিছু চেম্বার অব কমার্সে হয়তো সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী অথবা কোনো কোনো দেশের প্রতিনিধিরা আসেন এবং শুধু এ পর্যন্তই। পরে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করে বিনিয়োগ করানোর মতো উদ্যোগ দেখা যায় না।
বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার মতো প্রবল ইচ্ছা, কার্যকর নেটওয়ার্ক ও যোগ্যতাসম্পন্ন জনবলের অভাব রয়েছে। সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের আগ্রহী করে তোলার জন্য প্রয়োজন ওয়ান স্টপ সার্ভিস চালু, বিদ্যুৎ ও গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ, স্পেশাল ইকোনমিক জোনসহ দেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি করা প্রয়োজন। এ জন্য সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব কর কাঠামো প্রয়োজন। এ ছাড়া সবার আন্তরিকতা, দেশের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞাপন, সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ গড়ে তোলা দরকার। এলাকাভিত্তিক সম্ভাব্য বিনিয়োগের খাতগুলোকে শনাক্ত করে এবং কারখানা স্থাপনের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আমন্ত্রণ জানানো প্রয়োজন। শিক্ষিত ও মেধাবী, সৎ, আন্তরিক, টেকনিক্যালি ও যোগাযোগ রক্ষা করায় দক্ষতাসম্পন্ন, লক্ষ্য অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এমন একটি নেটওয়ার্ক টিম প্রয়োজন। নেটওয়ার্ক টিমটি সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে দেশের সম্ভাব্য খাতগুলোতে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানাবে। দেশে বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধাগুলো তুলে ধরবে এবং দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা এলে তাদের সর্বাত্মক বৈধ সুবিধা প্রদানসহ খাত ও স্থানভিত্তিক নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের আমন্ত্রণ জানাবে। প্রয়োজনে এ টিমকে সহায়তা করার জন্য বিদেশ থেকে টার্গেট অর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনবল নিয়ে আসা প্রয়োজন। এই নেটওয়ার্ক টিমটি সফল হলে আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা প্রদান করতে হবে।
মালয়েশিয়ার একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক দল বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিল। বাংলাদেশের কৃষি, তথ্য-প্রযুক্তি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ খাত, ইলেকট্রনিকস ও ইলেকট্রিক্যাল খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার সম্ভাবনা রয়েছে। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীরা, বিডা এবং বেপজার গতিশীল, যোগ্যতাসম্পন্ন ও লক্ষ্য অর্জনে একনিষ্ঠ, সৎ কর্মকর্তাবৃন্দ, যোগ্যতাসম্পন্ন বিভিন্ন চেম্বারের নেতৃবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সরকারি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত নেটওয়ার্ক টিমটি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাবে। মালয়েশিয়া ২০২২ সালে বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্ট করার জন্য প্রায় পাঁচ হাজার ৪০০ কোটি টাকার কৌশলগত অর্থ বরাদ্দ করেছিল। মালয়েশিয়া বেকারত্ব নিরসন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদিতে বৈদেশিক বিনিয়োগের বিরাট ভূমিকার বিষয়টি অনুধাবন করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করতে পেরেছিল। মালয়েশিয়ার শক্তিশালী ও টেকসই অর্থনৈতিক ভিত্তি, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ, দূরদর্শী ফোকাস ও গতিশীল কর্মশক্তি বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বেকারত্ব নিরসন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পেরেছে।
আমাদের ভারসাম্যপূর্ণ রাজস্বনীতি, বিনিয়োগবান্ধব মুদ্রানীতি, শিল্পনীতি ইত্যাদির মাধ্যমে বৈদেশিক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকৃষ্ট করার জন্য দূরদর্শী ফোকাসের অভাব রয়েছে। সর্ব বিষয়ে অতিমাত্রায় রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বেকারত্ব হ্রাস, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার দূরদর্শী ফোকাসের অন্তরায়। বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার প্রাথমিক ধাপে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি, অস্থিতিশীল বিনিময় হার বিরাজ করছে এবং প্রয়োজনের তুলনায় রিজার্ভ কম রয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি, সুদের হার, বিনিময় হার ইত্যাদির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। মানি লন্ডারিং, অবৈধ অর্থ, সিন্ডিকেট বাণিজ্য, দুর্নীতি, রাজনৈতিক প্রভাব প্রভৃতি কারণে দেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি বিরাজ করছে। রাজস্বনীতি, মুদ্রানীতি, শিল্পনীতি, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে এবং বিনিময় হার নির্ধারণ করাসহ বিভিন্ন উপায়ে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়ন অত্যন্ত জরুরি।
বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণ অত্যন্ত সহযোগিতামূলক হওয়া প্রয়োজন। একজন সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী যাতে প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও সহায়তা সহজেই পেতে পারেন এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন। বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করার মনোভাবের অভাব রয়েছে। আমাদের দেশের নিজের স্বার্থেই বিনিয়োগ, আয়, কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করা প্রয়োজন। কর ব্যবস্থাকে আরো বিনিয়োগবান্ধব করা সম্ভব হলে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও রাজস্ব বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটিতে গবেষণার জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন।
মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম কিভাবে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করেছে এবং বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে কী ধরনের কৌশলগত পদক্ষেপ নিয়েছে—এ বিষয়গুলো মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে বিডা, বেপজা এবং প্রস্তাবিত নেটওয়ার্ক টিমটিতে প্রদর্শন করানো প্রয়োজন এবং বাংলাদেশের কৌশলের সঙ্গে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূরীকরণ ও স্থিতিশীল নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন। অদক্ষতা ও জটিল শুল্ক ব্যবস্থার কারণে বন্দরে পণ্য খালাসের গতি কমে যায়। এ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও দক্ষতা অর্জন জরুরি। সর্বক্ষেত্রে নৈতিকতা ও সুশাসন প্রয়োজন। যেসব বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছেন তাঁদের কাজের অগ্রগতির দিকে নজর দিতে হবে। যেসব বৈদেশিক বিনিয়োগকারী বাংলাদেশে এরই মধ্যে বিনিয়োগ করেছেন তাঁদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন। সুতরাং দেশের বেকার সমস্যা এবং ক্রমবর্ধমান উচ্চশিক্ষিত বেকার সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে এবং দেশের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির বিকল্প নেই। বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিষয়টিকে দেশের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে দূরদর্শী ফোকাস এবং লক্ষ্য অর্জনে একনিষ্ঠ ও সমন্বিত প্রচেষ্টা একান্তভাবেই কাম্য।
লেখক : অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ শাহজালাল বিজ্ঞান ও
প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট
সম্পর্কিত খবর
ট্রাম্পের নীতি ও বিশ্বব্যবস্থার নতুন দ্বন্দ্ব
- ড. সুজিত কুমার দত্ত

কংগ্রেসের যৌথ কক্ষে সম্প্রতি এক ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে আমেরিকা ‘পৃথিবীর বুকে বিদ্যমান সবচেয়ে প্রভাবশালী সভ্যতা’ হয়ে উঠবে। ট্রাম্পের এই দাবিটি বিশাল এবং প্রশাসনের বৃহত্তর কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরে, যা আমেরিকান ব্যতিক্রমবাদ, শূন্য-সমষ্টি চিন্তা-ভাবনা এবং ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্রমবর্ধমান ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় নিমজ্জিত। এই দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি একক, প্রধান প্রতিপক্ষ চীন। ট্রাম্পের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ তাঁর ২০২০ সালের বই ‘আমেরিকান ক্রুসেড’-এ এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, যেখানে চীন কেবল ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং একটি ‘আধ্যাত্মিক প্রতিপক্ষ’।
বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক বিলি গ্রাহামের পুত্র এবং ট্রাম্পের একনিষ্ঠ সমর্থক ফ্র্যাংকলিন গ্রাহাম চীনের হুমকি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্পের MAGA আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্টিভ ব্যানন, কিছু ইভানজেলিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রতিধ্বনিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার গতিশীলতা এবং চীনের মতো দেশগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষের বিষয়ে।
ট্রাম্পকে নিয়ে ইউরোপ ও এশিয়ার ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশগুলোর দুশ্চিন্তাও রয়েছে। কারণ এত দিন তারা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব ও প্রভাবকে ব্যবহার করে নিজেদের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হলো বহুমুখী চরিত্রের সংকট। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গড়ে ওঠা আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা তথা বিশ্বব্যবস্থার ভবিষ্যেক সংকটে ফেলে দিয়েছেন।
ট্রাম্পের চীন ও রাশিয়ার প্রতি মনোভাবও উদ্বেগজনক। তিনি চীনের সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু করেন, কিন্তু একই সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতিও তাঁর সহানুভূতি দেখা যায়। এসব পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহ্যবাহী মিত্রদের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি করে। ট্রাম্পের অধীনে যুক্তরাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক চুক্তি থেকে সরে আসে এবং বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ কমিয়ে দেয়, তবে বিশ্বজুড়ে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা তৈরি হতে পারে। এর ফলে সৃষ্ট শূন্যতা চীন ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো পূরণ করতে পারে। এতে বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা ও সংঘাত বাড়তে পারে। ট্রাম্পের নীতি বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যব্যবস্থাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। তাঁর বাণিজ্যযুদ্ধ এবং সংরক্ষণবাদী নীতি বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা ডেকে আনতে পারে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি চীন ও রাশিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর জন্য প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে ইউরোপ ও এশিয়ায় এই দেশগুলো তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে। চীন তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ব্যবহার করে বিশ্বজুড়ে তার প্রভাব বাড়াচ্ছে। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের মাধ্যমে চীন এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে। এর মাধ্যমে তারা এই দেশগুলোর ওপর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করছে। অন্যদিকে রাশিয়া ইউরোপে তার সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে। ইউক্রেন সংকট ইউরোপের নিরাপত্তাব্যবস্থাকে দুর্বল করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। রাশিয়া ইউক্রেন সংকট ও অন্যান্য ভূ-রাজনৈতিক ইস্যুতে তার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে, যা পশ্চিমা দেশগুলোর জন্য উদ্বেগের কারণ। যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি বিশ্বশৃঙ্খলায় গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে, যা ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অস্থিরতা ও সংঘর্ষের আশঙ্কা বাড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যে এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বর্তমানে হুমকির সম্মুখীন।
বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলো মোকাবেলায় সহযোগিতা অপরিহার্য। জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি, সন্ত্রাসবাদ, খাদ্য নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক সংকটের মতো ইস্যুগুলো কোনো একক দেশের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি এই সমস্যাগুলোর সমাধানে বাধা সৃষ্টি করে এবং বৈশ্বিক স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে। ট্রাম্পের নীতির কারণে কেবল আন্তর্জাতিক অঙ্গনেই সংকট তৈরি হয়নি, বরং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও গভীর বিভাজন সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর অভিবাসনবিরোধী মনোভাব যুক্তরাষ্ট্রের সমাজে বর্ণবাদ এবং বিভাজনকে উসকে দিয়েছে। অতএব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত সম্মিলিতভাবে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত তার বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতি থেকে সরে এসে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ফিরে আসা। অন্যথায় বিশ্বব্যবস্থা আরো অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে এবং সংঘাতের ঝুঁকি বাড়বে।
লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
প্রধান উপদেষ্টার চীন সফর দুই দেশের সম্পর্ককে দৃঢ়তর করবে
- এ কে এম আতিকুর রহমান

চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংয়ের আমন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৬ মার্চ ২০২৫ চার দিনের এক সরকারি সফরে চীন যান। সফরকালে তিনি ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংয়ের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। তিনি চীনের হাইনান প্রদেশে আয়োজিত বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়া (বিএফএ) সম্মেলনে যোগ দেওয়া ছাড়াও চীনের ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন। গত বছরের আগস্ট মাসে সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই তাঁর প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফর।
দুই.
প্রধান উপদেষ্টা ২৭ মার্চ দক্ষিণ চীনের হাইনান প্রদেশের বোয়াওয়ে অনুষ্ঠিত বোয়াও ফোরাম ফর এশিয়ার (বিএফএ) বার্ষিক সম্মেলনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন এবং বক্তব্য দেন। তিনি বলেন যে এশিয়ার দেশগুলোর গন্তব্য হচ্ছে পরস্পরগ্রন্থিত।
তিন.
ড. মুহাম্মদ ইউনূস ২৭ মার্চ রাতে বোয়াও থেকে রাজধানী বেইজিংয়ে পৌঁছেন। ২৮ মার্চ সকালে বেইজিংয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে চীনা প্রেসিডেন্ট শি চিনপিংয়ের সঙ্গে তাঁর দ্বিপক্ষীয় বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উপদেষ্টা তাঁর প্রতিনিধিদলসহ হলে প্রবেশ করলে প্রেসিডেন্ট শি তাঁদের স্বাগত জানান। অত্যন্ত আন্তরিক এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রধান উপদেষ্টা গত বছর বাংলাদেশে সংঘটিত গণ-অভ্যুত্থানের ঘটনা চীনা প্রেসিডেন্টকে অবহিত করার সময় তাঁর অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেন। তিনি পারস্পরিক স্বার্থেই দ্বিপক্ষীয়, বিশেষ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রগুলোতে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি চীনের কাছে বাংলাদেশি তরুণদের স্বপ্নপূরণে সহায়তা চেয়ে একটি চীন সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপনের অনুরোধ জানান। তিনি চীনা প্রকল্প ঋণের সুদের হার কমানো এবং প্রতিশ্রুত অর্থের জন্য আরোপিত প্রতিশ্রুতি ফি মওকুফের অনুরোধ করেন। ড. ইউনূস বলেন, মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবর্তনে চীনের শক্তিশালী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ব্যাপারে তিনি চীনের কার্যকর সহযোগিতা কামনা করেন। এ ছাড়া তিনি শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় চীনকে আরো জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান। প্রধান উপদেষ্টা চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করেন।
 প্রেসিডেন্ট শি প্রধান উপদেষ্টার প্রতি চীনের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কর্মসূচির প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশকে চীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসেবে বর্ণনা করে বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য চীনের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি বাংলাদেশি পণ্যের জন্য চীনের দেওয়া শূন্য শুল্ক সুবিধা ২০২৮ সালের শেষ পর্যন্ত বহাল রাখার কথা জানান। বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগের পথকে সুগম করার জন্য তিনি বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও বিনিয়োগ চুক্তির জন্য আলোচনার প্রস্তাব দেন। প্রধান উপদেষ্টার অনুরোধে চীনা প্রেসিডেন্ট তাঁর দেশের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগ ও উৎপাদনকেন্দ্র স্থানান্তরের বিষয়ে উৎসাহিত করবেন বলে অবহিত করেন। তিনি বাংলাদেশে একটি বিশেষ চীনা শিল্পাঞ্চল ও শিল্প পার্ক নির্মাণে চীনের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট শি বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি বাড়ানো, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) প্রকল্পে বাংলাদেশকে উন্নতমানের সহযোগিতা প্রদান এবং ডিজিটাল ও সামুদ্রিক অর্থনীতিতে সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি স্বাস্থ্য ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিকদের চীনের ইউনান ও অন্য প্রদেশগুলোতে চিকিৎসার জন্য স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশে একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দেন। তিনি বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মায়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য তাঁর দেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।
প্রেসিডেন্ট শি প্রধান উপদেষ্টার প্রতি চীনের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কার কর্মসূচির প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশকে চীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী হিসেবে বর্ণনা করে বাংলাদেশের দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য চীনের উন্নয়ন অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব দেন। তিনি বাংলাদেশি পণ্যের জন্য চীনের দেওয়া শূন্য শুল্ক সুবিধা ২০২৮ সালের শেষ পর্যন্ত বহাল রাখার কথা জানান। বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগের পথকে সুগম করার জন্য তিনি বাংলাদেশ-চীন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) ও বিনিয়োগ চুক্তির জন্য আলোচনার প্রস্তাব দেন। প্রধান উপদেষ্টার অনুরোধে চীনা প্রেসিডেন্ট তাঁর দেশের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগ ও উৎপাদনকেন্দ্র স্থানান্তরের বিষয়ে উৎসাহিত করবেন বলে অবহিত করেন। তিনি বাংলাদেশে একটি বিশেষ চীনা শিল্পাঞ্চল ও শিল্প পার্ক নির্মাণে চীনের সমর্থনের কথা ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট শি বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানি বাড়ানো, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই) প্রকল্পে বাংলাদেশকে উন্নতমানের সহযোগিতা প্রদান এবং ডিজিটাল ও সামুদ্রিক অর্থনীতিতে সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি স্বাস্থ্য ও মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নাগরিকদের চীনের ইউনান ও অন্য প্রদেশগুলোতে চিকিৎসার জন্য স্বাগত জানান এবং বাংলাদেশে একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণা দেন। তিনি বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া মায়ানমারের নাগরিক রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের জন্য তাঁর দেশের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেন।
দুই পক্ষের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক শেষে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতার বিষয়ে একটি চুক্তি এবং আটটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকগুলোর মধ্যে রয়েছে দুই দেশের কালজয়ী সাহিত্য ও শিল্পকর্মের অনুবাদ ও সৃজন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও খবর আদান-প্রদান, গণমাধ্যম, ক্রীড়া এবং স্বাস্থ্য খাতে বিনিময় সহযোগিতা। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে যে পাঁচটি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তা হলো—বিনিয়োগ আলোচনা শুরু, বাংলাদেশে চীনের বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু, মোংলা বন্দরের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ, বাংলাদেশে একটি রোবট ফিজিওথেরাপি ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং চীনা অনুদান হিসেবে বাংলাদেশকে একটি হৃদরোগ সার্জারি যানবাহন প্রদান।
তথ্য মতে, মোংলা বন্দর আধুনিকীকরণ প্রকল্পে প্রায় ৪০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দেবে চীন। এ ছাড়া চীনা শিল্প অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়নে ৩৫০ মিলিয়ন ডলার এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা হিসেবে আরো ১৫০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। সর্বোপরি রয়েছে অনুদান ও অন্যান্য ঋণ সহায়তা।
প্রধান উপদেষ্টা চীনের পানিসম্পদমন্ত্রী লি গোইয়িংয়ের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশের নদী ও পানি ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে তিস্তা নদী প্রকল্প নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং এ বিষয়ে চীনের কাছ থেকে ৫০ বছরের একটি মাস্টারপ্ল্যান পাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
চার.
দ্বিপক্ষীয় বৈঠক শেষ হওয়ার পর সেদিনই তিনি বেইজিংয়ের দ্য প্রেসিডেনশিয়ালে অনুষ্ঠিত চীনা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একটি বিনিয়োগ সংলাপে অংশ নেন। মূলত প্রধান উপদেষ্টার সফরকে কেন্দ্র করেই ওই সংলাপ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সংলাপের মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে চীনা বিনিয়োগকারীদের অবহিত করা। প্রধান উপদেষ্টা একই ভেন্যুতে তিনটি গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন, যার বিষয়বস্তু ছিল টেকসই অবকাঠামো ও জ্বালানি বিনিয়োগ, বাংলাদেশ : উৎপাদন ও বাজারের সুযোগ এবং সামাজিক ব্যবসা, যুব উদ্যোক্তা ও থ্রি-জিরো বিশ্বের ভবিষ্যৎ। ওই সব আলোচনা প্রধান উপদেষ্টাকে বিভিন্ন কম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সামাজিক ব্যবসা ক্ষেত্রের অভিজ্ঞ ব্যক্তি ও চীনের স্বনামধন্য কম্পানির কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ এনে দেয়।
ড. ইউনূস চীনা বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে ব্যবসাবান্ধব ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। চীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী দেশ বাংলাদেশ উল্লেখ করে তিনি বাণিজ্য ও ব্যবসা সম্প্রসারণে সমুদ্র যোগাযোগের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। তিনি নেপাল ও ভুটান ছাড়াও ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্ব রাজ্য স্থলবেষ্টিত উল্লেখ করে এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ওপর জোর দেন, যা বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
প্রধান উপদেষ্টা বাংলাদেশের মানবসম্পদের সম্ভাবনা সম্পর্কে বলেন, বাংলাদেশে প্রায় ১৭ কোটি মানুষ বাস করে, যাদের বেশির ভাগই যুবক, যারা উদ্যম, সৃজনশীলতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পরিপূর্ণ। তিনি এই তরুণ জনগোষ্ঠীর অব্যবহৃত সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। গত বছর ঘটে যাওয়া বাংলাদেশের রূপান্তর প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে দেশে নতুন প্রজন্ম উঠে আসছে, যা ব্যবসা ও বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।
চীন সরকার ও চীনা কম্পানিগুলোর কাছ থেকে ২১০ কোটি মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ, ঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে। দেশটির প্রায় ৩০টি কম্পানি বাংলাদেশের বিশেষ চীনা শিল্প অর্থনৈতিক অঞ্চলে এক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের অঙ্গীকার করেছে।
পাঁচ.
২৯ মার্চ সকালে চীনের পিকিং বিশ্ববিদ্যালয় ড. ইউনূসকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। এই উপলক্ষে সেখানে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘বিশ্বকে বদলে দিতে বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখতে হবে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শুধু শেখার জায়গা নয়, এটি স্বপ্ন দেখারও জায়গা। আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন, তবে তা ঘটবেই। আপনি যদি স্বপ্ন না দেখেন, তবে তা কখনো ঘটবে না। এখন পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, কেউ না কেউ আগে তা কল্পনা করেছিল।’
প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ‘তিন শূন্য তত্ত্ব’—শূন্য কার্বন নির্গমন, শূন্য দারিদ্র্য এবং শূন্য বেকারত্বের ওপরও আলোকপাত করেন। তিনি তাঁর ‘সামাজিক ব্যবসা’ তত্ত্বটিও তুলে ধরে বলেন যে এটি এমন একটি ব্যবসা, যা সামাজিক সমস্যার সমাধান করে। শিক্ষার্থীদের কার্বন নির্গমনে অংশ না নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সবার উচিত নিজেদের ‘তিন শূন্য’ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলা।
ছয়.
চীন সফরটি প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফর। দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দিন দিন দৃঢ়তর ও গভীর হচ্ছে। এই সফর বিদ্যমান সম্পর্কে আরো নতুন শক্তি জোগাবে বলেই বিশ্বাস। আমরা এর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, যখন প্রধান উপদেষ্টা ও চীনা প্রেসিডেন্টের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বাড়াতে উভয় পক্ষ ঐকমত্য পোষণ করে।
চীন যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেসব বাস্তবায়ন করা গেলে তা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকাকে আরো সচল এবং গতিময় করবে। দেশে যখন বিনিয়োগপ্রবাহ নেতিবাচক ধারার দিকে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে চীনের নতুন বিনিয়োগ দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবেশ, বিশেষ করে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
যেকোনো দেশের জন্যই চীন একটি বড় বাজার, কিন্তু বাংলাদেশ সেই বাজারটি ধরতে পারেনি। দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে রপ্তানির চেয়ে আমদানি প্রতিবছরই বেড়ে চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে চীন থেকে দুই হাজার ১১২ কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে বাংলাদেশ। অথচ একই সময়ে দেশটিতে বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে মাত্র ৬৮ কোটি ডলারের পণ্য। রপ্তানি বাড়াতে হলে চীনের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের পণ্য উৎপাদন করতে হবে। এ ছাড়া যেসব পণ্য চীনের চেয়ে বাংলাদেশে উৎপাদন খরচ কম হবে, সেসব উৎপাদনের জন্য চীনা বিনিয়োগকারীদের এখানে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে। বাংলাদেশে উৎপাদিত ওই সব পণ্য চীন ছাড়াও অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা যাবে।
বাংলাদেশ থেকে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক রোগী প্রতিবেশী ভারত ছাড়াও থাইল্যান্ড বা সিঙ্গাপুরে গিয়ে থাকে। বাংলাদেশের কাছাকাছি চীনের কুনমিংয়ে বাংলাদেশিদের চিকিৎসাসেবার জন্য চারটি হাসপাতাল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধির আভাসও দেওয়া হয়েছে। যাতায়াতসহ অন্যান্য খরচ ও চিকিৎসা ব্যয় যদি তুলনামূলকভাবে কম হয় এবং চিকিৎসার মান উন্নত হয়, তাহলে এই প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয় হবে। এ ছাড়া নতুন করে যেসব চুক্তি বা স্মারক স্বাক্ষরিত হলো, তা বাস্তবায়িত হলে সেসবের মাঝে এই সফরের সাফল্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে চীন সব সময়ই বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে আসছে। আমাদের বিশ্বাস, চীন মায়ানমারকে চাপ দিলে প্রত্যাবাসন সহজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। কিন্তু চীন যে ভূমিকা নিলে প্রত্যাবাসন সম্ভব হবে, তা নেবে কি না সেই প্রশ্নটি রয়েই যায়।
আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে চীন বাংলাদেশের সঙ্গে যে সমীকরণ রক্ষা করে চলছে, সেভাবেই চলবে বলে মনে হয়। এ ক্ষেত্রে তেমন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। কারণ বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট ও দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতির সমীকরণ বেশ জটিল হয়ে আছে।
যা হোক, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান উপদেষ্টার চীন সফর দুই দেশের সম্পর্ককে শক্তিশালী করতে নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
লেখক : সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব
নতুন নতুন শহরে ডেঙ্গুর বিস্তার : নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জ
- অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার

ডেঙ্গু বাংলাদেশের জন্য একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জনসচেতনতার অভাবের ফলে এডিস মশাবাহিত এই রোগের প্রকোপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। আগাম ব্যবস্থা না নিলে এ বছরও ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।
বাংলাদেশে ডেঙ্গুর সংক্রমণ প্রথম ধরা পড়ে ২০০০ সালে, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর প্রকোপ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ২০১৯ ও ২০২৩ সালে ডেঙ্গু ভয়াবহ রূপ নেয় এবং মৃত্যুহারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। বর্তমানে ডেঙ্গু শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ নেই, বরং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর সংক্রমণ অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।
ডেঙ্গুর জন্য দায়ী মূলত এডিস এজিপ্টি এবং এডিস এলবোপিক্টাস প্রজাতির মশা। এগুলো সাধারণত দিনের বেলায়, বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যায় মানুষকে কামড়ায়। তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশারের গবেষণায় দেখা গেছে, এটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাতের বেলায়ও কামড়ায়।
 এডিস মশা সাধারণত পরিষ্কার ও জমে থাকা পানিতে ডিম পাড়ে। যেমন—ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের পাত্র, ফ্রিজের ট্রে, এসির পানি জমানো স্থান ইত্যাদি। অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং ছোট শহরে অধিক জনসংখ্যার কারণে প্রচুর পরিমাণে ছোট-বড় পাত্র তৈরি হয়, যার মধ্যে পানি জমা হয়ে মশার বংশবৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করছে। প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহারের ফলে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের প্লাস্টিকের পাত্র। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্লাস্টিকের বোতল, কাপ, ব্যাগ ইত্যাদি।
এডিস মশা সাধারণত পরিষ্কার ও জমে থাকা পানিতে ডিম পাড়ে। যেমন—ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের পাত্র, ফ্রিজের ট্রে, এসির পানি জমানো স্থান ইত্যাদি। অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং ছোট শহরে অধিক জনসংখ্যার কারণে প্রচুর পরিমাণে ছোট-বড় পাত্র তৈরি হয়, যার মধ্যে পানি জমা হয়ে মশার বংশবৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করছে। প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহারের ফলে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের প্লাস্টিকের পাত্র। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্লাস্টিকের বোতল, কাপ, ব্যাগ ইত্যাদি।
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ডেঙ্গু সংক্রমণের জন্য অত্যন্ত সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উষ্ণ আবহাওয়ায় মশার ডিম থেকে পূর্ণবয়স্ক মশা হয়ে উঠতে কম সময় লাগে। ফলে মশার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আগে শুধু বর্ষাকালে ডেঙ্গু দেখা যেত, এখন গ্রীষ্মকালেও ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অনিয়মিত ও অতিবর্ষণের ফলে বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকে, যা মশার জন্মের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।
ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি প্রধান ধরন বা সেরোটাইপ (DENV-1, DENV-2, DENV-3 ও DENV-4) রয়েছে। একবার একটি সেরোটাইপ দিয়ে কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে শরীরে সেই সেরোটাইপের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি গড়ে ওঠে। ওই একই সেরোটাইপ দিয়ে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত না হলেও অন্য সেরোটাইপের ডেঙ্গু ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।
ভাইরাস খুব দ্রুত মিউটেডেট বা পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ডেঙ্গুর ধরন পরিবর্তিত হলে সংক্রমণ আরো মারাত্মক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, DENV-2 ও DENV-3 ধরনের সংক্রমণ সাধারণত বেশি মারাত্মক রূপ নেয় এবং এগুলো ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের ঝুঁকি বাড়ায়। একবার একটি ধরন বা সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হওয়ার পর যদি অন্য ধরন দ্বারা সংক্রমিত হয়, তাহলে অ্যান্টিবডি-ডিপেনডেন্ট এনহান্সমেন্ট (ADE) নামক একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রমণ আরো গুরুতর হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় ইমিউন সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রোগী রোগ প্রতিরোধক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পরিবর্তিত পরিবেশে ভাইরাস খুব দ্রুত অভিযোচিত হয়। ভাইরাসের জিনগত পরিবর্তনের ফলে এটি আরো সংক্রামক হতে পারে এবং ভ্যাকসিন বা চিকিৎসাপদ্ধতিও কম কার্যকর হয়ে যেতে পারে। তাই এন্টোমলজিক্যাল সার্ভিলেন্সের পাশাপাশি সেরো সার্ভিলেন্স বা ভাইরাসের জিনগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে নিয়মিত জেনেটিক সার্ভেইল্যান্স করা প্রয়োজন। ডেঙ্গুর প্রতিটি সেরোটাইপ ও তার সংক্রমণের ধরন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা উচিত। সাধারণ জনগণ, চিকিৎসক ও নার্সদের ডেঙ্গুর নতুন ধরন ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করা জরুরি।
বর্তমানে ঢাকার বাইরে অনেক শহরে মশা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং হাসপাতালের প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয়। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশালসহ অন্যান্য শহরে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ডেঙ্গুর বিস্তার সহজ হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলাবদ্ধতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব নতুন শহরগুলোতে মশার বংশবৃদ্ধি বাড়িয়ে দিচ্ছে। শহরের বাইরে মানুষ বেশি ঘরের বাইরে কাজ করে। ফলে মশার কামড়ের ঝুঁকিও বেশি। এ বছর ঢাকার বাইরে বেশ কিছু জেলায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেলা শহরগুলোতে মশা নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষিত জনবল ও বাজেট না থাকায় নিয়ন্ত্রণ কষ্টসাধ্য। প্রতিটি জেলা ও শহরে মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু করা দরকার। ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের আবর্জনায় বৃষ্টির পানি জমা হয়ে যেহেতু মশা প্রজনন হয়, তাই পানির জমাট বাঁধা রোধে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা প্রয়োজন। নতুন এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ কমাতে নিয়মিত সংক্রমণ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। বিগত বছরগুলোতে ডেঙ্গু রোগে মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রোগী উপজেলা বা জেলা শহরগুলো থেকে ঢাকায় স্থানান্তরে সময়ক্ষেপণের কারণে বেশি মারা গেছে। ডেঙ্গুর মৃত্যু কমাতে প্রতিটি জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।
ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কোনো অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ নেই, শুধু সাপোর্টিভ কেয়ার দেওয়া হয়। কিন্তু রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেলে হাসপাতালগুলোর ওপর মারাত্মক চাপ পড়ে। প্রতিবছর বর্ষা-পরবর্তী সময়ে হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়, যা স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। স্যালাইন, প্যারাসিটামল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধের সংকট তৈরি হয়। এ বছরের ডেঙ্গু মোকাবেলায় তাই পূর্বপ্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।
লেখক : কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
professorkabirul@gmail.com
দেশ কারো একার নয়, দেশ সবার
- গাজীউল হাসান খান
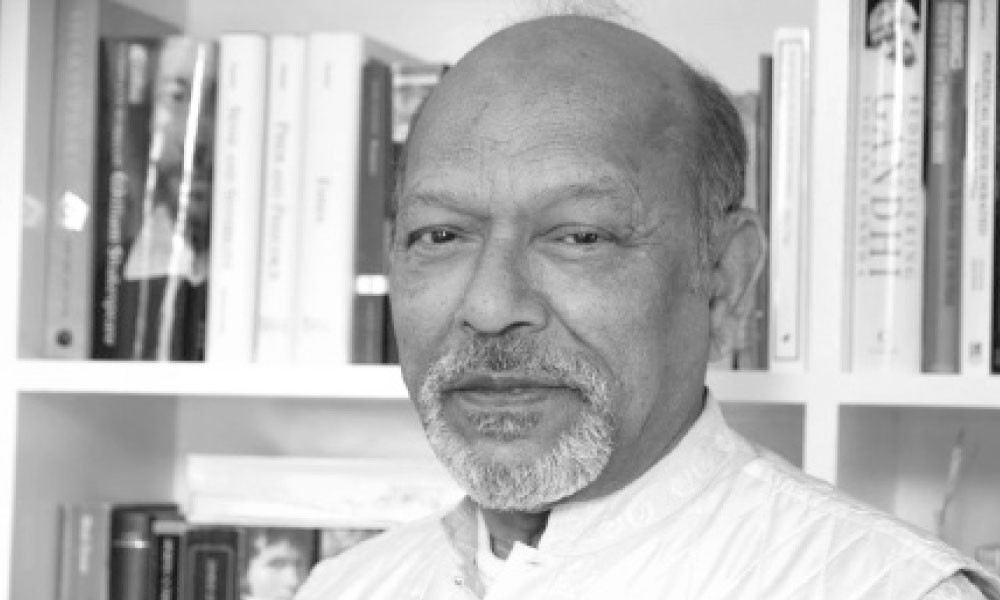
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্থাৎ এই অঞ্চলের মানুষের হাজার বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে অবিভক্ত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম হিসেবে আবির্ভূত হলেও এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে একটি কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত মেলমন্ধন গড়ে উঠেছিল, যা তাদের এই উপমহাদেশের অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় একটি ভিন্নতর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং জীবনাচরণ, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসরতা এনে দিয়েছিল। নদীমাতৃক বাংলার ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থান, কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ এই অঞ্চলের মানুষের মন-মানসিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং জীবন দর্শনের ক্ষেত্রেও নিজেদের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মতো একটি প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণের ছোট কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে বাংলাদেশ একটি সুবিস্তীর্ণ ও বিশাল সমতল ভূমি।
বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার দরুন উত্তর ভারতীয় শাসকদের অনেকেই নানাভাবে চেষ্টা করেও বাংলাদেশের ওপর তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কখনো কখনো কোনো কোনো সম্রাট বা শাসক যদিও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করতেন, তবু তাঁদের কর্তৃত্ব এখানে বেশিদিন স্থায়ী হতো না। বাংলার শাসকরা বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।
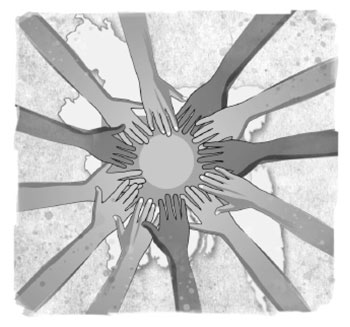 ওপরে উল্লেখিত বিভাজন কিংবা বিভক্তির রাজনীতি চালু করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত লাভবান হয়নি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি। শেষ পর্যন্ত ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তারা। তবে পেছনে ফেলে গেছে এক বহুধাবিভক্ত কূটকৌশলগত বিশাল জনপদ, যেখানে পদে পদে আজও অসামান্য খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতাকামী মানুষকে। বাংলার সংগ্রামী জনগণের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, সেদিন তাঁদের বেশির ভাগই প্রস্তাবিত বিভক্ত উপমহাদেশের না ভারত, না পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত অংশে যেতে প্রস্তুত ছিল। তারা চেয়েছিল একটি অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গভূমি, যা তাদের পূর্বপুরুষরাও অতীতে চেয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে। কিন্তু বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থ ও ষড়যন্ত্রের কারণে সেদিন তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। সেদিন শুধু ব্রিটিশশাসিত এই উপমহাদেশই নয়, বিভক্ত হয়েছিল অখণ্ড বঙ্গভূমিও। সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতিগত স্বার্থের কাছে হেরে গিয়েছিল বাংলার অগ্রসর মানুষের অতীতের চিন্তা-ভাবনা।
ওপরে উল্লেখিত বিভাজন কিংবা বিভক্তির রাজনীতি চালু করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত লাভবান হয়নি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি। শেষ পর্যন্ত ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তারা। তবে পেছনে ফেলে গেছে এক বহুধাবিভক্ত কূটকৌশলগত বিশাল জনপদ, যেখানে পদে পদে আজও অসামান্য খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতাকামী মানুষকে। বাংলার সংগ্রামী জনগণের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, সেদিন তাঁদের বেশির ভাগই প্রস্তাবিত বিভক্ত উপমহাদেশের না ভারত, না পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত অংশে যেতে প্রস্তুত ছিল। তারা চেয়েছিল একটি অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গভূমি, যা তাদের পূর্বপুরুষরাও অতীতে চেয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে। কিন্তু বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থ ও ষড়যন্ত্রের কারণে সেদিন তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। সেদিন শুধু ব্রিটিশশাসিত এই উপমহাদেশই নয়, বিভক্ত হয়েছিল অখণ্ড বঙ্গভূমিও। সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতিগত স্বার্থের কাছে হেরে গিয়েছিল বাংলার অগ্রসর মানুষের অতীতের চিন্তা-ভাবনা।
নতুন পর্যায়ে ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে যোগ দিয়েও শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না সেদিনের খণ্ডিত পূর্ব বাংলা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিরোধ, ব্যবধান ও বৈষম্যের কারণে নবগঠিত পাকিস্তান নামক সেই রাষ্ট্রটি ভেঙে গেল। ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ তার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রাজনীতি এবং আর্থ-সামাজিক স্বার্থ, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার জন্য লড়েছিল ৯ মাসের এক সশস্ত্র সংগ্রাম। অনেক রক্ত বিসর্জন ও চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে একাত্তরে অর্জিত হয়েছিল এ দেশের মানুষের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, যার নাম বাংলাদেশ। সাতচল্লিশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান নামক মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে এই অঞ্চলের বাঙালিরা যেমন পায়নি তাদের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও গৌরব, তেমনি একাত্তরের রক্তাক্ত সংগ্রামের পরও নিজেদের তথাকথিত স্বজাতির কাছ থেকে তারা পায়নি তাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। ফ্যাসিবাদ বা আধিপত্যবাদ, রাজনৈতিক নির্যাতন কিংবা অর্থনৈতিক লুটপাট ও শোষণ-বঞ্চনার কাছে পদদলিত হয়েছে তাদের অধিকার ও মুক্তির স্বপ্ন দেড় দশকেরও অধিক সময় ধরে। বাংলাদেশটিকে বিদায়ি শাসকগোষ্ঠী তাদের পারিবারিক সম্পত্তি কিংবা জমিদারি বলে মনে করেছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিসচেতন মানুষ যেমন ধর্মের নামে পাকিস্তানি শাসকদের ২৪ বছরের অগণতান্ত্রিক ও সামরিক স্বৈরশাসন মেনে নেয়নি, তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে যারা বিগত দেড় দশকের বেশি সময় এ দেশের মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণ-বঞ্চনা চালিয়েছে, তাদেরও মেনে নেয়নি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আপসহীন সংগ্রামের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেত্রী ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তথাকথিত ধর্ম কিংবা বাঙালি জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে অন্যায়, অবিচার, শোষণ-শাসন ও নৈরাজ্য চালিয়ে এ দেশে কেউ রেহাই পায়নি। এ দেশের মানুষ অধিকারসচেতন এবং আপসহীনভাবে সংগ্রামী। সে কারণেই প্রাচীন কাল থেকেই এ দেশকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘বিদ্রোহের দেশ’ হিসেবে।
সাতচল্লিশপূর্ব ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন-বিদ্রোহ কম হয়নি। ১৭৬০ সালে এবং তা ১৮০০ সাল পর্যন্ত এ দেশে ইংরেজ প্রশাসন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে ফকির ও সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে সংগ্রাম করেছে। তারপর শুরু হয় নীল বিদ্রোহ। ১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে বাংলায় নীল চাষ বিলুপ্ত হয়। বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিল এই বাংলায়ই। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তিতুমীর। বাংলার অধঃপতিত সমাজকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এক ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবর্তক হাজি শরীয়তুল্লাহ। পলাশী যুদ্ধের পর পরাধীনতার যুগে বাংলার মানুষের অবস্থার চরম অবনতির কথা উপলব্ধি করেই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মাঠে নামেন। তার পর থেকে এ দেশের জনগণের অধিকার আদায় ও মুক্তির প্রশ্নে বহু আন্দোলন-সংগ্রাম ও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু সে আন্দোলন-সংগ্রাম বা বিদ্রোহ চূড়ান্ত পর্যায়ে কোনো বিশেষ সাফল্যের মুখ দেখেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আন্দোলনকারী কিংবা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব। সে আন্দোলন, অভ্যুত্থান কিংবা বিদ্রোহের সঙ্গে যদি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার মহান অভ্যুত্থানের তুলনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যুগের অগ্রগতি ও উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির কারণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা অনেক সাফল্য পেয়েছে। মূলত রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক সে অভ্যুত্থানে তারা একটি শক্তিশালী ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটিয়েছে, যা অতীতের আন্দোলনকারী কিংবা বিদ্রোহীরা পারেনি।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী নন। তবু তাঁদেরই লাগাতার জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের নেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা তখন তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নিতে পারেনি। তাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ দেশের কিছু প্রতিষ্ঠিত অরাজনৈতিক মানুষের। একটি অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য। সে কারণেই ছাত্র-জনতার সেই গণ-অভ্যুত্থানকে জনগণের বিপ্লব বলা যায় না। কারণ বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল থাকতে হয়, যারা বিপ্লবোত্তরকালে দেশ পরিচালনা করবে। যত প্রয়োজনীয় সংস্কার কিংবা পরিবর্তন, সেটি সেই বিপ্লবী দলই করবে। গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকা ছাত্র-জনতা সেই দায়িত্বটি পালন করতে পারেনি। ফলে রাষ্ট্র মেরামত কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের প্রশ্নে এখন বিএনপিসহ দেশের বিভিন্ন দল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীদের নিয়ে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা যখন বলছেন রাষ্ট্র মেরামতের সুযোগ হারানো ঠিক হবে না, তখন বিএনপিসহ অনেকে বলছে, নির্বাচনসংশ্লিষ্টতার বাইরে আপাতত কোনো সংস্কারের প্রয়োজন নেই। এর পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতারা বলছেন, আগে প্রয়োজনীয় সংস্কার, তারপর নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে অনেকে বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের আগেই এসব বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত ছিল। তাদের নির্দিষ্ট করে বলা উচিত ছিল, তারা কত দিন ক্ষমতায় থাকবে এবং সে সময়ে তাদের কোন কোন দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। সে অন্তর্বর্তী সময়ে অর্থাৎ একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকবে কি না।
জুলাই-আগস্টের আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বা অর্জনকে আখ্যায়িত করছে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বা নতুন বাংলাদেশ হিসেবে। তারা এটিকে ‘সেকেন্ড রিপাবলিক’ (দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র) হিসেবে ঘোষণা করতে চায়। এ ব্যাপারে আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বিমতও রয়েছে। নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা নাহিদ ইসলাম সম্প্রতি বলেছেন, একাত্তর ও চব্বিশ আলাদা কিছু নয়, বরং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই একাত্তরের স্পিরিট পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।
এ কথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীন বাংলাদেশ বাঙালি জাতির জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। একাত্তরে বাঙালি জাতি ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে যে স্বাধীন রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেছে, তাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, তার পরবর্তী সময়ে ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থান কিংবা জুলাই-আগস্টে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে একটি মহান গণ-অভ্যুত্থান। একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে পরবর্তী পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হতো না। সে কারণেই ২০২৪-এ সংঘটিত জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান একাত্তরের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এ ক্ষেত্রে যারা একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধকে কম গুরুত্ব দিতে চায়, তারা আসলে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিভিন্ন বিতর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন করে আমাদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করতে চায়। একাত্তরে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা একটি বহুতল সুউচ্চ ভবনের মতো। আমাদের জাতির ইতিহাসে যতই দিন যাচ্ছে, ততই সেই ভবনটি আরো উচ্চতর হচ্ছে, তার ভিত্তি আরো মজবুত হচ্ছে। প্রাচীন কাল থেকেই এই উপমহাদেশের বাংলাভাষী জাতিগোষ্ঠীর স্বপ্ন ছিল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার।
এ কথা ঠিক যে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে অতীতে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, অনেক জাতীয় স্বার্থবিরোধী মানুষও দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিল, কিন্তু দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে তাদের সব অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং একাত্তর কিংবা চব্বিশ নিয়ে মনগড়া বিতর্ক সৃষ্টির ফল হবে জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থ বিনষ্ট করা। নিজেদের মধ্যে অহেতুক মতবিরোধ কিংবা বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা। এতে আমাদের দেশপ্রেম এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দল বা মতের মানুষের মধ্যে আলোচনা হতে পারে। আমাদের জাতীয় জীবনে সেটি একটি অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয়। এ দেশ আমাদের সবার। এ দেশ আমাদের পূর্বপুরুষেরও। কারণ প্রাচীন কাল থেকে তাঁরাও স্বাধীন বাংলাদেশ নামে একটি ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই আমাদের সব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে হবে। জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নগুলোকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে। তাহলেই আমাদের দেশ প্রকৃত অর্থেই হবে এক ‘মহান বাংলাদেশ’।
লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
gaziulhkhan@gmail.com