এ কথা অনস্বীকার্য যে রাজনীতি রাজনীতিকদেরই সাজে। এই গণসম্পৃক্ত কাজটি তাঁদেরই সার্বিক দায়দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। রাজনীতি অবশ্যই আমাদের জাতীয় জীবনের একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে তার সার্বিক অগ্রগতি কিংবা সাফল্য নির্ভর করে মূলত কিছু নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ ও সঠিক কর্মপদ্ধতির ওপর।
এ লড়াই জিততে হবে
- গাজীউল হাসান খান
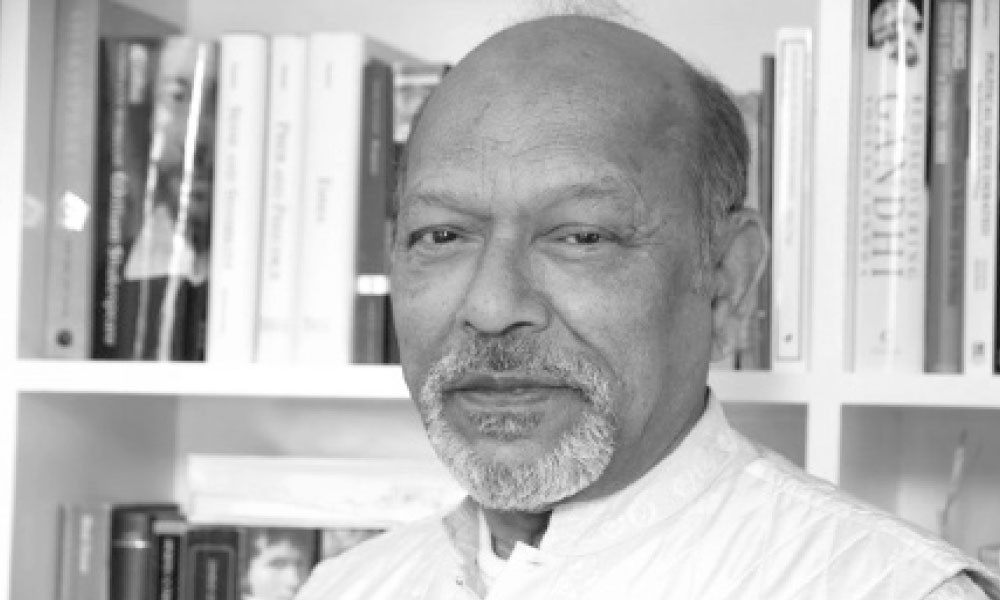
কোনো কোনো নির্দিষ্ট সময় ছাড়া এই বিষয়টি আমাদের স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫২ বছরের রাজনৈতিকজীবনে বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেছে।
 রাজনীতি রাজনীতিকদের কাজ হলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় সব পেশাজীবী ও চিন্তাশীল মানুষের অংশগ্রহণ একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। রাষ্ট্র সবার। তাই রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ নিয়ে ভাবার অধিকার সবার, মানুষেরই সমাজ। এটি রাজনীতিকদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষেত্র নয়। শুধু রাজনীতিকরাই সব কিছু বুঝেন আর কেউ নয়, যদি সত্যি এমনটি হতো, তাহলে বিগত ৫২ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতির এই হাল হতো না। দেশের সর্বত্র এবং সব মহলে এখন সময়োচিত সংস্কার ও রাষ্ট্র মেরামতের দাবি উঠেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শুধু একা রাজনীতিকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া কাঙ্ক্ষিত কিংবা মোটেও বাঞ্ছিত নয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এই মহান দায়িত্বটি সম্মিলিতভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, ‘এমন সুযোগ একটি জাতির জীবনে খুব কমই আসে। সুতরাং তাকে হাতছাড়া করা যাবে না, ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।’ এই মহান দায়িত্বটি পালন করার বা সমন্বয় করার ভার যাঁদের ওপর ছাত্র-জনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অর্পণ করেছে, তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। নতুবা সম্মিলিতভাবে এই মহান কর্তব্য বা দায়িত্বটি পালন করতে অসমর্থ হলে দেশে আবার রাজনৈতিক অসন্তোষ, নৈরাজ্য, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও দুঃশাসন অচিরেই ফিরে আসবে। ব্যর্থ হবে গণতান্ত্রিক সব প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন হবে বিফল মনোরথ। বর্তমানে ছাত্র-জনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রদত্ত এই সংস্কারের উদ্যোগ কোনো অসাধু মহলের চক্রান্তে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রটি একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে কিংবা কারো করদরাজ্যে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। যারা এই মহান কাজে এখন বিঘ্ন ঘটাবে, একদিন এর ব্যর্থতার দায়ভার সবটুকুই তাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। সুতরাং রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ভূমিকা নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতিগতভাবে আরো অধঃপতিত ও বিপদগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ আমাদের খুবই কম। সম্মিলিত কিংবা জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংস্কারের চলমান প্রক্রিয়াকে এখন যেকোনো মূল্যের বিনিময়ে অব্যাহত রাখতে হবে। নতুবা লাগামহীন রাজনৈতিক তাণ্ডবে নিঃস্ব হবে দেশ, চরমভাবে বিপর্যস্ত হবে সমগ্র জাতি।
রাজনীতি রাজনীতিকদের কাজ হলেও রাষ্ট্র পরিচালনায় সব পেশাজীবী ও চিন্তাশীল মানুষের অংশগ্রহণ একটি অবিচ্ছেদ্য বিষয়। রাষ্ট্র সবার। তাই রাষ্ট্রের সার্বিক কল্যাণ নিয়ে ভাবার অধিকার সবার, মানুষেরই সমাজ। এটি রাজনীতিকদের একচ্ছত্র আধিপত্যের ক্ষেত্র নয়। শুধু রাজনীতিকরাই সব কিছু বুঝেন আর কেউ নয়, যদি সত্যি এমনটি হতো, তাহলে বিগত ৫২ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতির এই হাল হতো না। দেশের সর্বত্র এবং সব মহলে এখন সময়োচিত সংস্কার ও রাষ্ট্র মেরামতের দাবি উঠেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি শুধু একা রাজনীতিকদের ওপর ছেড়ে দেওয়া কাঙ্ক্ষিত কিংবা মোটেও বাঞ্ছিত নয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এই মহান দায়িত্বটি সম্মিলিতভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে। তিনি আরো বলেছেন, ‘এমন সুযোগ একটি জাতির জীবনে খুব কমই আসে। সুতরাং তাকে হাতছাড়া করা যাবে না, ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না।’ এই মহান দায়িত্বটি পালন করার বা সমন্বয় করার ভার যাঁদের ওপর ছাত্র-জনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অর্পণ করেছে, তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। নতুবা সম্মিলিতভাবে এই মহান কর্তব্য বা দায়িত্বটি পালন করতে অসমর্থ হলে দেশে আবার রাজনৈতিক অসন্তোষ, নৈরাজ্য, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও দুঃশাসন অচিরেই ফিরে আসবে। ব্যর্থ হবে গণতান্ত্রিক সব প্রক্রিয়া এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন হবে বিফল মনোরথ। বর্তমানে ছাত্র-জনতা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রদত্ত এই সংস্কারের উদ্যোগ কোনো অসাধু মহলের চক্রান্তে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশ নামক এই রাষ্ট্রটি একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে কিংবা কারো করদরাজ্যে পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। যারা এই মহান কাজে এখন বিঘ্ন ঘটাবে, একদিন এর ব্যর্থতার দায়ভার সবটুকুই তাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে। সুতরাং রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ভূমিকা নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করে জাতিগতভাবে আরো অধঃপতিত ও বিপদগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ আমাদের খুবই কম। সম্মিলিত কিংবা জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংস্কারের চলমান প্রক্রিয়াকে এখন যেকোনো মূল্যের বিনিময়ে অব্যাহত রাখতে হবে। নতুবা লাগামহীন রাজনৈতিক তাণ্ডবে নিঃস্ব হবে দেশ, চরমভাবে বিপর্যস্ত হবে সমগ্র জাতি।
ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধবিগ্রহের কারণে আন্তর্জাতিকভাবে শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক ব্যাপক মন্দার দীর্ঘসূত্রতার পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে। এতে বিশ্বব্যাপী নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তদুপরি বিশ্বব্যাপী খারাপ আবহাওয়া ও প্রলয়ংকরী বন্যার কারণে ফসলহানি কিংবা শাক-সবজির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশ তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে-নগরে তার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। তদুপরি রয়েছে সিন্ডিকেট, মজুদদার ও অসাধু ব্যবসায়ীদের তৎপরতা। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও বাজার ব্যবস্থায় আরো অনেক কঠোর হতে হবে। প্রয়োজন হলে আইনসংগতভাবে ভেঙে দিতে হবে অসাধু চক্রের সব কর্মকাণ্ড এবং নিশ্চিত করতে হবে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের অবাধ সরবরাহ। নজরদারি জোরদার করতে হবে, যাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। নতুবা বাজার নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থায় আরো বাস্তবভিত্তিক পরিবর্তন আনতে হবে। টিসিবির মতো বিপণনব্যবস্থা আরো ব্যাপকভিত্তিক ও প্রসারিত করতে হবে। এর পাশাপাশি আর যে বিষয়টি সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত পীড়া দিচ্ছে, তা হলো আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের প্রশ্ন হচ্ছে, সামরিক বাহিনীর হাতে ‘ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা’ (যত সাময়িকই হোক) দেওয়ার পরও রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহর-নগরীতে যে ধরনের চুরি, ডাকাতি ও রাহাজানি হচ্ছে, তা অত্যন্ত অনাকাঙ্ক্ষিত। এতে মনে হয়, এ দেশে চোর-ডাকাতরাও অত্যন্ত সংগঠিত ও তথ্য-প্রযুক্তি সমৃদ্ধ। সুতরাং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকেও ততটাই সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে হবে। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অর্থাৎ ৫ আগস্ট-পরবর্তী বিপর্যস্ত পুলিশ বাহিনী এখন তাদের নিজ নিজ দায়িত্বে আবার বেশির ভাগই যোগ দিয়েছে। সংগঠিত কিংবা পরিকল্পিতভাবে কাজও শুরু করেছে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের আশার সঞ্চার হচ্ছে যে সার্বিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রণে আসবে।
ছাত্র-জনতার জুলাই-আগস্টের মৃত্তিকা-কাঁপানো গণ-অভ্যুত্থানের মতো এত বড় একটি বিস্ময়কর ঘটনা দেশের কিছু মানুষ বোধ হয় এরই মধ্যে ভুলতে বসেছে। দেশের সব কিছু যে রাতারাতি ওলটপালট হয়ে গেছে, বদলে গেছে সব কিছু, তা যেন তাদের নজরেই পড়েনি। সে ব্যাপক পরিবর্তন কিংবা ‘গণেশ ওল্টানোর’ কারণে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে গণপ্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনসহ সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংকট ও শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তিত, পরিকল্পিত, উন্নত ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যা ক্রমে ক্রমেই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন রাষ্ট্রে এ ধরনের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মানুষ উন্নত জীবন ব্যবস্থার জন্য নতুন করে আশায় বুক বাধে, ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে। এতটা অসহিষ্ণু ও অধৈর্য হয়ে পড়ে না। আমাদের দেশে এক ধরনের রাজনীতিক রয়েছেন, যাঁরা দেশের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও যথাযথ রাষ্ট্রীয় মেরামত চান অথচ তার জন্য দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সময়টুকু দিতে আগ্রহী নন। এই দেশটি সবার, শুধু রাজনীতিকদের নয়। সুতরাং একজন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞদের নিজ নিজ মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। নতুবা তাঁরা সংস্কারের প্রশ্নে রাজনীতিকদের ভূমিকা নিয়ে খেপে যেতে পারেন। রাজনীতিকদের ওপর আস্থা হারাতে পারেন। এ কথাও ঠিক যে আমাদের বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং সেনাবাহিনী বিভিন্ন বিষয়ে অত্যন্ত চাপের মুখে রয়েছে। এর মধ্যে দেশীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু ছাড়াও রয়েছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। টেকনাফের কাছে মায়ানমার নৌবাহিনীর অবস্থান, বাংলাদেশি জেলেদের ওপর আক্রমণ, হত্যা ও তাঁদের ধরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি দেশের সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে। সরকারকে অসময়ে করেছে যথেষ্ট বিব্রত। মায়ানমার নৌবাহিনী বা নৌবহর বাংলাদেশের জলসীমায় আনাগোনা শুরু করেছে। এই বিষয়টির উৎপত্তি কোথায়, তা নিয়ে সরকার এবং আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী যথেষ্ট তৎপর হয়ে উঠেছে।
মায়ানমার নৌবাহিনীর সাম্প্রতিক তৎপরতাকে চীনের উসকানি বলে অনেকে মনে করছে। তা ছাড়া চীন গত কিছুদিনের মধ্যে মায়ানমারকে প্রতিশ্রুত ১৬টির মধ্যে ছয়টি জঙ্গিবিমান সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিশেষ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান এই বিষয়গুলো নিয়ে ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা বলেছেন। বোঝা যাচ্ছে, চীন বাংলাদেশের ওয়াশিংটনমুখী কার্যকলাপকে খুব ভালোভাবে নেয়নি। তারা চায় রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা সমাধানসহ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা প্রশ্নে ও ইন্দো-প্যাসিফিক জলপথকে ঝঞ্ঝামুক্ত রাখার ব্যাপারে ঢাকা বেইজিংয়ের সঙ্গে একটি সমঝোতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখুক। তারা এ অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী কিংবা আগ্রাসনবাদী পরিকল্পনাকে বেশি দূর বাড়তে দেওয়ার বিপক্ষে। সে কারণে বাংলাদেশের সব অবস্থার একটি নির্ভরযোগ্য বন্ধু ও উন্নয়ন সহযোগী হিসেবে পাশে থাকতে চায় চীন। বর্তমান ইউনূস প্রশাসন ও সেনাবাহিনী এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। এর বিপক্ষে যাওয়া বাংলাদেশের পক্ষে কল্যাণকর হবে না। ফলে চীনের দুটি রণতরি চট্টগ্রামে এসেছে সম্প্রতি। সেখানে চীনের রাষ্ট্রদূতের উপস্থিতিতে চীন ও বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ নৌ কর্মকর্তারা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বৈঠক করেছেন। এতে বাংলাদেশ নিয়ে বেইজিংয়ে জমে ওঠা শীতল বরফ কিছুটা গলতে শুরু করে, চীন থেকে অস্ত্র আমদানিও শুরু হচ্ছে। দেশে দ্রব্যমূল্য ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের বিষয় দুটি বাদ দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি, বাণিজ্য ও অন্যান্য সেক্টরে অগ্রগতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এতে মানুষের মনে ক্রমেই ইতিবাচক ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে ইউনূস সরকারের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ভবিষ্যৎ ও সংস্কার কর্মকাণ্ডের সম্ভাবনা নিয়ে। এখন আমাদের প্রয়োজন ধৈর্যসহকারে সর্বক্ষেত্রে কর্মমুখর হওয়া। এই গণ-অভ্যুত্থান, সংস্কারপ্রক্রিয়া এবং নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে কোনোভাবেই ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না। দেশ-বিদেশের চক্রান্তকারীদের এখন একযোগে রুখতে হবে। কারণ সম্ভাবনাময় জোনাকির আঁধারমানিকগুলো ক্রমে ক্রমে এখন জ্বলে উঠতে শুরু করেছে। একে অস্থিরতা কিংবা হতাশার আচ্ছাদনে ঢেকে দেওয়া যাবে না। আমাদের এ লড়াই আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, সামনে এগিয়ে যাওয়ার লড়াই।
লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
gaziulhkhan@gmail.com
সম্পর্কিত খবর
নতুন নতুন শহরে ডেঙ্গুর বিস্তার : নিয়ন্ত্রণের চ্যালেঞ্জ
- অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশার

ডেঙ্গু বাংলাদেশের জন্য একটি অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং জনসচেতনতার অভাবের ফলে এডিস মশাবাহিত এই রোগের প্রকোপ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গুর সংক্রমণ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে। আগাম ব্যবস্থা না নিলে এ বছরও ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।
বাংলাদেশে ডেঙ্গুর সংক্রমণ প্রথম ধরা পড়ে ২০০০ সালে, তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এর প্রকোপ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে ২০১৯ ও ২০২৩ সালে ডেঙ্গু ভয়াবহ রূপ নেয় এবং মৃত্যুহারও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। বর্তমানে ডেঙ্গু শুধু ঢাকায় সীমাবদ্ধ নেই, বরং সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে বাংলাদেশে ডেঙ্গুর সংক্রমণ অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে।
ডেঙ্গুর জন্য দায়ী মূলত এডিস এজিপ্টি এবং এডিস এলবোপিক্টাস প্রজাতির মশা। এগুলো সাধারণত দিনের বেলায়, বিশেষ করে সকাল ও সন্ধ্যায় মানুষকে কামড়ায়। তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কবিরুল বাশারের গবেষণায় দেখা গেছে, এটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাতের বেলায়ও কামড়ায়।
 এডিস মশা সাধারণত পরিষ্কার ও জমে থাকা পানিতে ডিম পাড়ে। যেমন—ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের পাত্র, ফ্রিজের ট্রে, এসির পানি জমানো স্থান ইত্যাদি। অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং ছোট শহরে অধিক জনসংখ্যার কারণে প্রচুর পরিমাণে ছোট-বড় পাত্র তৈরি হয়, যার মধ্যে পানি জমা হয়ে মশার বংশবৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করছে। প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহারের ফলে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের প্লাস্টিকের পাত্র। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্লাস্টিকের বোতল, কাপ, ব্যাগ ইত্যাদি।
এডিস মশা সাধারণত পরিষ্কার ও জমে থাকা পানিতে ডিম পাড়ে। যেমন—ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের পাত্র, ফ্রিজের ট্রে, এসির পানি জমানো স্থান ইত্যাদি। অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং ছোট শহরে অধিক জনসংখ্যার কারণে প্রচুর পরিমাণে ছোট-বড় পাত্র তৈরি হয়, যার মধ্যে পানি জমা হয়ে মশার বংশবৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করছে। প্লাস্টিকের বহুল ব্যবহারের ফলে তৈরি হচ্ছে নানা ধরনের প্লাস্টিকের পাত্র। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্লাস্টিকের বোতল, কাপ, ব্যাগ ইত্যাদি।
জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ডেঙ্গু সংক্রমণের জন্য অত্যন্ত সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উষ্ণ আবহাওয়ায় মশার ডিম থেকে পূর্ণবয়স্ক মশা হয়ে উঠতে কম সময় লাগে। ফলে মশার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আগে শুধু বর্ষাকালে ডেঙ্গু দেখা যেত, এখন গ্রীষ্মকালেও ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অনিয়মিত ও অতিবর্ষণের ফলে বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকে, যা মশার জন্মের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে।
ডেঙ্গু ভাইরাসের চারটি প্রধান ধরন বা সেরোটাইপ (DENV-1, DENV-2, DENV-3 ও DENV-4) রয়েছে। একবার একটি সেরোটাইপ দিয়ে কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত হলে শরীরে সেই সেরোটাইপের বিরুদ্ধে ইমিউনিটি গড়ে ওঠে। ওই একই সেরোটাইপ দিয়ে দ্বিতীয়বার আক্রান্ত না হলেও অন্য সেরোটাইপের ডেঙ্গু ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থেকে যায়।
ভাইরাস খুব দ্রুত মিউটেডেট বা পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ডেঙ্গুর ধরন পরিবর্তিত হলে সংক্রমণ আরো মারাত্মক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, DENV-2 ও DENV-3 ধরনের সংক্রমণ সাধারণত বেশি মারাত্মক রূপ নেয় এবং এগুলো ডেঙ্গু হেমোরেজিক ফিভারের ঝুঁকি বাড়ায়। একবার একটি ধরন বা সেরোটাইপ দিয়ে আক্রান্ত হওয়ার পর যদি অন্য ধরন দ্বারা সংক্রমিত হয়, তাহলে অ্যান্টিবডি-ডিপেনডেন্ট এনহান্সমেন্ট (ADE) নামক একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংক্রমণ আরো গুরুতর হতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় ইমিউন সিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রোগী রোগ প্রতিরোধক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। পরিবর্তিত পরিবেশে ভাইরাস খুব দ্রুত অভিযোচিত হয়। ভাইরাসের জিনগত পরিবর্তনের ফলে এটি আরো সংক্রামক হতে পারে এবং ভ্যাকসিন বা চিকিৎসাপদ্ধতিও কম কার্যকর হয়ে যেতে পারে। তাই এন্টোমলজিক্যাল সার্ভিলেন্সের পাশাপাশি সেরো সার্ভিলেন্স বা ভাইরাসের জিনগত পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করতে নিয়মিত জেনেটিক সার্ভেইল্যান্স করা প্রয়োজন। ডেঙ্গুর প্রতিটি সেরোটাইপ ও তার সংক্রমণের ধরন নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা করা উচিত। সাধারণ জনগণ, চিকিৎসক ও নার্সদের ডেঙ্গুর নতুন ধরন ও ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন করা জরুরি।
বর্তমানে ঢাকার বাইরে অনেক শহরে মশা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং হাসপাতালের প্রস্তুতি পর্যাপ্ত নয়। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশালসহ অন্যান্য শহরে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ার ফলে ডেঙ্গুর বিস্তার সহজ হচ্ছে। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, জলাবদ্ধতা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব নতুন শহরগুলোতে মশার বংশবৃদ্ধি বাড়িয়ে দিচ্ছে। শহরের বাইরে মানুষ বেশি ঘরের বাইরে কাজ করে। ফলে মশার কামড়ের ঝুঁকিও বেশি। এ বছর ঢাকার বাইরে বেশ কিছু জেলায় ডেঙ্গু পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেলা শহরগুলোতে মশা নিয়ন্ত্রণে প্রশিক্ষিত জনবল ও বাজেট না থাকায় নিয়ন্ত্রণ কষ্টসাধ্য। প্রতিটি জেলা ও শহরে মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি চালু করা দরকার। ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের আবর্জনায় বৃষ্টির পানি জমা হয়ে যেহেতু মশা প্রজনন হয়, তাই পানির জমাট বাঁধা রোধে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা প্রয়োজন। নতুন এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ কমাতে নিয়মিত সংক্রমণ পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। বিগত বছরগুলোতে ডেঙ্গু রোগে মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, রোগী উপজেলা বা জেলা শহরগুলো থেকে ঢাকায় স্থানান্তরে সময়ক্ষেপণের কারণে বেশি মারা গেছে। ডেঙ্গুর মৃত্যু কমাতে প্রতিটি জেলা হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডেঙ্গু চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে।
ডেঙ্গু চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট কোনো অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ নেই, শুধু সাপোর্টিভ কেয়ার দেওয়া হয়। কিন্তু রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেলে হাসপাতালগুলোর ওপর মারাত্মক চাপ পড়ে। প্রতিবছর বর্ষা-পরবর্তী সময়ে হাসপাতালগুলোতে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়, যা স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। স্যালাইন, প্যারাসিটামল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ওষুধের সংকট তৈরি হয়। এ বছরের ডেঙ্গু মোকাবেলায় তাই পূর্বপ্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন।
লেখক : কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
professorkabirul@gmail.com
দেশ কারো একার নয়, দেশ সবার
- গাজীউল হাসান খান
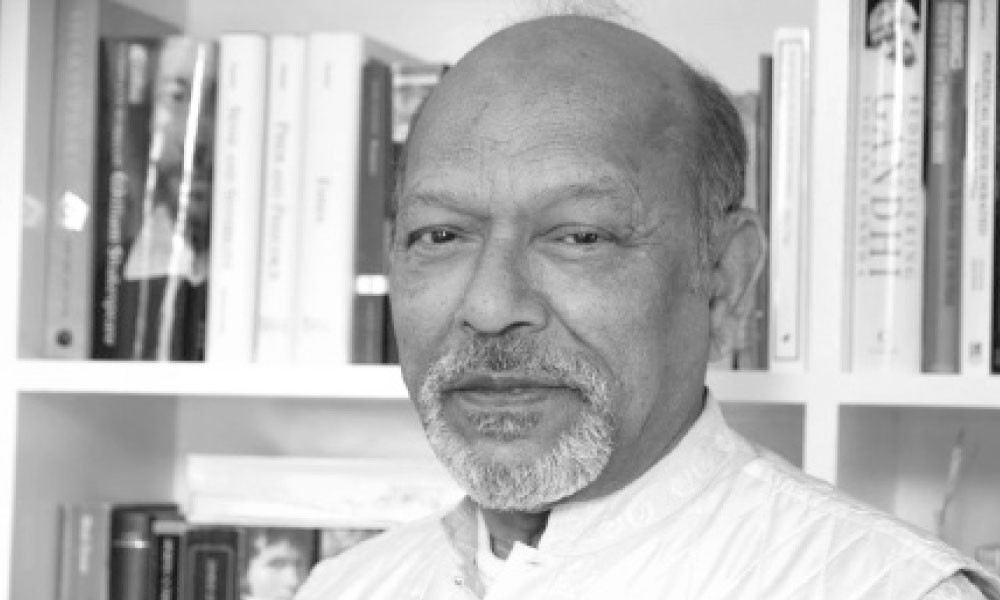
বাংলাদেশের স্বাধীনতা আমাদের পূর্বপুরুষদের অর্থাৎ এই অঞ্চলের মানুষের হাজার বছরের আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় পর্যায়ক্রমে অবিভক্ত বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম হিসেবে আবির্ভূত হলেও এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে একটি কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত মেলমন্ধন গড়ে উঠেছিল, যা তাদের এই উপমহাদেশের অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় একটি ভিন্নতর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং জীবনাচরণ, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রসরতা এনে দিয়েছিল। নদীমাতৃক বাংলার ভূ-প্রকৃতিগত অবস্থান, কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশ এই অঞ্চলের মানুষের মন-মানসিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং জীবন দর্শনের ক্ষেত্রেও নিজেদের সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার মতো একটি প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল। পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণের ছোট কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল বাদ দিলে বাংলাদেশ একটি সুবিস্তীর্ণ ও বিশাল সমতল ভূমি।
বাংলাদেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার দরুন উত্তর ভারতীয় শাসকদের অনেকেই নানাভাবে চেষ্টা করেও বাংলাদেশের ওপর তাঁদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। কখনো কখনো কোনো কোনো সম্রাট বা শাসক যদিও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করতেন, তবু তাঁদের কর্তৃত্ব এখানে বেশিদিন স্থায়ী হতো না। বাংলার শাসকরা বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।
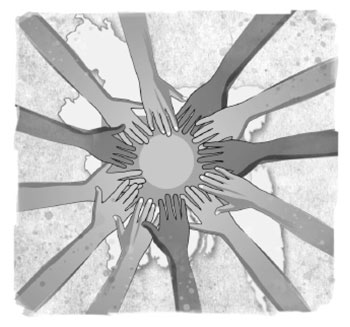 ওপরে উল্লেখিত বিভাজন কিংবা বিভক্তির রাজনীতি চালু করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত লাভবান হয়নি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি। শেষ পর্যন্ত ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তারা। তবে পেছনে ফেলে গেছে এক বহুধাবিভক্ত কূটকৌশলগত বিশাল জনপদ, যেখানে পদে পদে আজও অসামান্য খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতাকামী মানুষকে। বাংলার সংগ্রামী জনগণের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, সেদিন তাঁদের বেশির ভাগই প্রস্তাবিত বিভক্ত উপমহাদেশের না ভারত, না পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত অংশে যেতে প্রস্তুত ছিল। তারা চেয়েছিল একটি অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গভূমি, যা তাদের পূর্বপুরুষরাও অতীতে চেয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে। কিন্তু বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থ ও ষড়যন্ত্রের কারণে সেদিন তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। সেদিন শুধু ব্রিটিশশাসিত এই উপমহাদেশই নয়, বিভক্ত হয়েছিল অখণ্ড বঙ্গভূমিও। সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতিগত স্বার্থের কাছে হেরে গিয়েছিল বাংলার অগ্রসর মানুষের অতীতের চিন্তা-ভাবনা।
ওপরে উল্লেখিত বিভাজন কিংবা বিভক্তির রাজনীতি চালু করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত লাভবান হয়নি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তি। শেষ পর্যন্ত ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তারা। তবে পেছনে ফেলে গেছে এক বহুধাবিভক্ত কূটকৌশলগত বিশাল জনপদ, যেখানে পদে পদে আজও অসামান্য খেসারত দিতে হচ্ছে বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতাকামী মানুষকে। বাংলার সংগ্রামী জনগণের নেতৃত্বে যাঁরা ছিলেন, সেদিন তাঁদের বেশির ভাগই প্রস্তাবিত বিভক্ত উপমহাদেশের না ভারত, না পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত অংশে যেতে প্রস্তুত ছিল। তারা চেয়েছিল একটি অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গভূমি, যা তাদের পূর্বপুরুষরাও অতীতে চেয়েছিলেন যুগ যুগ ধরে। কিন্তু বিভিন্ন কায়েমি স্বার্থ ও ষড়যন্ত্রের কারণে সেদিন তাদের সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। সেদিন শুধু ব্রিটিশশাসিত এই উপমহাদেশই নয়, বিভক্ত হয়েছিল অখণ্ড বঙ্গভূমিও। সাম্প্রদায়িকতা এবং জাতিগত স্বার্থের কাছে হেরে গিয়েছিল বাংলার অগ্রসর মানুষের অতীতের চিন্তা-ভাবনা।
নতুন পর্যায়ে ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসার লক্ষ্যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে যোগ দিয়েও শেষ পর্যন্ত টিকতে পারল না সেদিনের খণ্ডিত পূর্ব বাংলা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন বিরোধ, ব্যবধান ও বৈষম্যের কারণে নবগঠিত পাকিস্তান নামক সেই রাষ্ট্রটি ভেঙে গেল। ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন বাংলাদেশ তার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর রাজনীতি এবং আর্থ-সামাজিক স্বার্থ, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখার জন্য লড়েছিল ৯ মাসের এক সশস্ত্র সংগ্রাম। অনেক রক্ত বিসর্জন ও চরম আত্মত্যাগের বিনিময়ে একাত্তরে অর্জিত হয়েছিল এ দেশের মানুষের জন্য একটি স্বাধীন ভূখণ্ড, যার নাম বাংলাদেশ। সাতচল্লিশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর পাকিস্তান নামক মুসলিম অধ্যুষিত রাষ্ট্রে এই অঞ্চলের বাঙালিরা যেমন পায়নি তাদের ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা ও গৌরব, তেমনি একাত্তরের রক্তাক্ত সংগ্রামের পরও নিজেদের তথাকথিত স্বজাতির কাছ থেকে তারা পায়নি তাদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি। ফ্যাসিবাদ বা আধিপত্যবাদ, রাজনৈতিক নির্যাতন কিংবা অর্থনৈতিক লুটপাট ও শোষণ-বঞ্চনার কাছে পদদলিত হয়েছে তাদের অধিকার ও মুক্তির স্বপ্ন দেড় দশকেরও অধিক সময় ধরে। বাংলাদেশটিকে বিদায়ি শাসকগোষ্ঠী তাদের পারিবারিক সম্পত্তি কিংবা জমিদারি বলে মনে করেছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিসচেতন মানুষ যেমন ধর্মের নামে পাকিস্তানি শাসকদের ২৪ বছরের অগণতান্ত্রিক ও সামরিক স্বৈরশাসন মেনে নেয়নি, তেমনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে যারা বিগত দেড় দশকের বেশি সময় এ দেশের মানুষের ওপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণ-বঞ্চনা চালিয়েছে, তাদেরও মেনে নেয়নি। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আপসহীন সংগ্রামের মুখে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেত্রী ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তথাকথিত ধর্ম কিংবা বাঙালি জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে অন্যায়, অবিচার, শোষণ-শাসন ও নৈরাজ্য চালিয়ে এ দেশে কেউ রেহাই পায়নি। এ দেশের মানুষ অধিকারসচেতন এবং আপসহীনভাবে সংগ্রামী। সে কারণেই প্রাচীন কাল থেকেই এ দেশকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘বিদ্রোহের দেশ’ হিসেবে।
সাতচল্লিশপূর্ব ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন-বিদ্রোহ কম হয়নি। ১৭৬০ সালে এবং তা ১৮০০ সাল পর্যন্ত এ দেশে ইংরেজ প্রশাসন ও জমিদারদের বিরুদ্ধে ফকির ও সন্ন্যাসীরা একসঙ্গে সংগ্রাম করেছে। তারপর শুরু হয় নীল বিদ্রোহ। ১৮৫৯-৬০ সালের নীল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আঘাতে বাংলায় নীল চাষ বিলুপ্ত হয়। বাংলার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের সূত্রপাত হয়েছিল এই বাংলায়ই। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন তিতুমীর। বাংলার অধঃপতিত সমাজকে আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে এক ব্যাপকভিত্তিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবর্তক হাজি শরীয়তুল্লাহ। পলাশী যুদ্ধের পর পরাধীনতার যুগে বাংলার মানুষের অবস্থার চরম অবনতির কথা উপলব্ধি করেই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে মাঠে নামেন। তার পর থেকে এ দেশের জনগণের অধিকার আদায় ও মুক্তির প্রশ্নে বহু আন্দোলন-সংগ্রাম ও বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু সে আন্দোলন-সংগ্রাম বা বিদ্রোহ চূড়ান্ত পর্যায়ে কোনো বিশেষ সাফল্যের মুখ দেখেনি। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল আন্দোলনকারী কিংবা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব। সে আন্দোলন, অভ্যুত্থান কিংবা বিদ্রোহের সঙ্গে যদি ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টে সংঘটিত ছাত্র-জনতার মহান অভ্যুত্থানের তুলনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যুগের অগ্রগতি ও উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির কারণে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা অনেক সাফল্য পেয়েছে। মূলত রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক সে অভ্যুত্থানে তারা একটি শক্তিশালী ফ্যাসিবাদী সরকারের পতন ঘটিয়েছে, যা অতীতের আন্দোলনকারী কিংবা বিদ্রোহীরা পারেনি।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা কোনো প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী নন। তবু তাঁদেরই লাগাতার জুলাই-আগস্টের আন্দোলনের ফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের নেত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। আন্দোলনরত ছাত্র-জনতা তখন তাৎক্ষণিকভাবে নিজেদের হাতে ক্ষমতা তুলে নিতে পারেনি। তাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ দেশের কিছু প্রতিষ্ঠিত অরাজনৈতিক মানুষের। একটি অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে তুলে নেওয়ার জন্য। সে কারণেই ছাত্র-জনতার সেই গণ-অভ্যুত্থানকে জনগণের বিপ্লব বলা যায় না। কারণ বিপ্লব সংগঠিত করতে হলে একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক দল থাকতে হয়, যারা বিপ্লবোত্তরকালে দেশ পরিচালনা করবে। যত প্রয়োজনীয় সংস্কার কিংবা পরিবর্তন, সেটি সেই বিপ্লবী দলই করবে। গণ-অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকা ছাত্র-জনতা সেই দায়িত্বটি পালন করতে পারেনি। ফলে রাষ্ট্র মেরামত কিংবা গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের প্রশ্নে এখন বিএনপিসহ দেশের বিভিন্ন দল, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীদের নিয়ে গঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টি এবং অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টারা যখন বলছেন রাষ্ট্র মেরামতের সুযোগ হারানো ঠিক হবে না, তখন বিএনপিসহ অনেকে বলছে, নির্বাচনসংশ্লিষ্টতার বাইরে আপাতত কোনো সংস্কারের প্রয়োজন নেই। এর পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের নেতারা বলছেন, আগে প্রয়োজনীয় সংস্কার, তারপর নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে অনেকে বলছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের আগেই এসব বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত ছিল। তাদের নির্দিষ্ট করে বলা উচিত ছিল, তারা কত দিন ক্ষমতায় থাকবে এবং সে সময়ে তাদের কোন কোন দায়িত্ব সম্পাদন করতে হবে। সে অন্তর্বর্তী সময়ে অর্থাৎ একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগ পর্যন্ত দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকবে কি না।
জুলাই-আগস্টের আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বা অর্জনকে আখ্যায়িত করছে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বা নতুন বাংলাদেশ হিসেবে। তারা এটিকে ‘সেকেন্ড রিপাবলিক’ (দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র) হিসেবে ঘোষণা করতে চায়। এ ব্যাপারে আবার কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের দ্বিমতও রয়েছে। নবগঠিত জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা নাহিদ ইসলাম সম্প্রতি বলেছেন, একাত্তর ও চব্বিশ আলাদা কিছু নয়, বরং চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই একাত্তরের স্পিরিট পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।
এ কথা অনস্বীকার্য যে স্বাধীন বাংলাদেশ বাঙালি জাতির জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন। একাত্তরে বাঙালি জাতি ৯ মাসের সশস্ত্র যুদ্ধে যে স্বাধীন রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেছে, তাকে কেন্দ্র করেই ঘটেছে পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, তার পরবর্তী সময়ে ৭ নভেম্বর সিপাহি-জনতার অভ্যুত্থান কিংবা জুলাই-আগস্টে সংঘটিত বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে একটি মহান গণ-অভ্যুত্থান। একাত্তরে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে পরবর্তী পরিবর্তনগুলো সংঘটিত হতো না। সে কারণেই ২০২৪-এ সংঘটিত জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান একাত্তরের রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এ ক্ষেত্রে যারা একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধকে কম গুরুত্ব দিতে চায়, তারা আসলে নিজেদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিভিন্ন বিতর্কিত প্রশ্নের সম্মুখীন করে আমাদের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করতে চায়। একাত্তরে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা একটি বহুতল সুউচ্চ ভবনের মতো। আমাদের জাতির ইতিহাসে যতই দিন যাচ্ছে, ততই সেই ভবনটি আরো উচ্চতর হচ্ছে, তার ভিত্তি আরো মজবুত হচ্ছে। প্রাচীন কাল থেকেই এই উপমহাদেশের বাংলাভাষী জাতিগোষ্ঠীর স্বপ্ন ছিল একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার।
এ কথা ঠিক যে আমাদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে অতীতে অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, অনেক জাতীয় স্বার্থবিরোধী মানুষও দেশ বা রাষ্ট্র পরিচালনায় ছিল, কিন্তু দেশপ্রেমিক জনগণের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে তাদের সব অপচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং একাত্তর কিংবা চব্বিশ নিয়ে মনগড়া বিতর্ক সৃষ্টির ফল হবে জাতীয় ঐক্য ও স্বার্থ বিনষ্ট করা। নিজেদের মধ্যে অহেতুক মতবিরোধ কিংবা বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা। এতে আমাদের দেশপ্রেম এক অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে। জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিষয় নিয়ে বিভিন্ন দল বা মতের মানুষের মধ্যে আলোচনা হতে পারে। আমাদের জাতীয় জীবনে সেটি একটি অত্যন্ত কাঙ্ক্ষিত বিষয়। এ দেশ আমাদের সবার। এ দেশ আমাদের পূর্বপুরুষেরও। কারণ প্রাচীন কাল থেকে তাঁরাও স্বাধীন বাংলাদেশ নামে একটি ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাই বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থেই আমাদের সব বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে হবে। জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নগুলোকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হবে। তাহলেই আমাদের দেশ প্রকৃত অর্থেই হবে এক ‘মহান বাংলাদেশ’।
লেখক : বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক
gaziulhkhan@gmail.com
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের শাটল ডিপ্লোমেসি
- ড. ফরিদুল আলম

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ‘শাটল ডিপ্লোমেসি’ বলে একটি ধারণা প্রচলিত আছে। দুই পক্ষের মধ্যে যখন সংঘাত চলে এবং নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে এই সংঘাত নিরসনের কোনো সম্ভাবনা থাকে না কিংবা দুই পক্ষের কেউ কাউকে একবিন্দু ছাড় দিতে রাজি নয়, এমন অবস্থায় তৃতীয় এবং শক্তিশালী একটি রাষ্ট্রের প্রচেষ্টায় এই সংঘাত বন্ধের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, সংক্ষেপে একেই শাটল ডিপ্লোমেসি বলা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারকে শাটল ডিপ্লোমেসির উদ্যোক্তা বলা হয়। ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরায়েলের মধ্যকার সংঘাত এবং পরবর্তী সময়ে একে কেন্দ্র করে আরব রাষ্ট্রগুলোর তেল রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞাকে নিয়ে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়।
 ওপরের এই ভূমিকাটি দেওয়ার কারণ হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় দুটি সংকটের মধ্যে একটি হচ্ছে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ এবং অপরটি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এর মধ্যে তিন বছরাধিক কাল ধরে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ১০ লক্ষাধিক মানুষ শরণার্থী হিসেবে অন্যত্র চলে গেছে এবং অসংখ্য মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত হয়েছে। এরই মধ্যে শক্তিশালী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইউক্রেন তার ২০ শতাংশ ভূমির দখল হারিয়েছে এবং যেকোনো সময় রাশিয়ার পক্ষ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে। পশ্চিমাদের সুস্পষ্ট সমর্থন থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর এ নিয়ে খোদ পশ্চিমাদের মধ্যেই বিভাজিত অবস্থা তৈরি হয়েছে।
ওপরের এই ভূমিকাটি দেওয়ার কারণ হচ্ছে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় দুটি সংকটের মধ্যে একটি হচ্ছে ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধ এবং অপরটি রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। এর মধ্যে তিন বছরাধিক কাল ধরে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে, ১০ লক্ষাধিক মানুষ শরণার্থী হিসেবে অন্যত্র চলে গেছে এবং অসংখ্য মানুষ অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত হয়েছে। এরই মধ্যে শক্তিশালী রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইউক্রেন তার ২০ শতাংশ ভূমির দখল হারিয়েছে এবং যেকোনো সময় রাশিয়ার পক্ষ থেকে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁকি রয়েছে। পশ্চিমাদের সুস্পষ্ট সমর্থন থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর এ নিয়ে খোদ পশ্চিমাদের মধ্যেই বিভাজিত অবস্থা তৈরি হয়েছে।
গত ২৫ মার্চ রাশিয়ার ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে এক মাসের জন্য (ট্রাম্প-পুতিন আলোচনার পর গত ১৮ মার্চ থেকে) ইউক্রেনের কিছু নির্দিষ্ট স্থানে যুদ্ধবিরতির কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে পারমাণবিক স্থাপনার বাইরেও রয়েছে তেল ও গ্যাস ক্ষেত্র, বৈদ্যুতিক স্থাপনা এবং খাদ্য মজুদ ব্যবস্থায় হামলা না করা। মোটাদাগে দুই পক্ষই একে অপরের এনার্জি ব্যবস্থাপনা ও খাদ্য মজুদ ব্যবস্থার ওপর হামলা থেকে বিরত থাকবে এবং কোনো এক পক্ষ এটি ভঙ্গ করলে অপর পক্ষও আর এটি মেনে চলতে বাধ্য নয়। এখানে উল্লেখ্য, রাশিয়ার তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে যে তারা এটি মেনে চললেও ইউক্রেন এরই মধ্যে রাশিয়ার সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে বেশ কিছু ক্যামিকাজ ড্রোন নিক্ষেপ করেছে, যা রাশিয়া ভূপাতিত করেছে। তারা বলছে, ইউক্রেনের তরফ থেকে ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে চলা হচ্ছে না। এর ফলে রাশিয়ার পক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন পাল্টা হামলায় নতুন করে ইউক্রেনের কিছু বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে আশার কথা যে মার্কিন মধ্যস্থতায় দুই পক্ষের মধ্যে রিয়াদ আলোচনা এখনো চলমান এবং একটি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরের পথে অনেকটাই ইতিবাচক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
রাশিয়ার এ ক্ষেত্রে দাবি স্পষ্ট। ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য হওয়ার স্বপ্ন পরিত্যাগ করতে হবে, রুশ বাহিনী কর্তৃক দখলকৃত ইউক্রেনের ভূমি রাশিয়ার বলে স্বীকার করে নিতে হবে, ইউরোপীয় দেশগুলো কর্তৃক ইউক্রেনে শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে হবে এবং ২০২২ সালের বসন্তে ইস্তাম্বুল-রাশিয়া-ইউক্রেন চুক্তির বাস্তবায়ন করতে হবে। কী ছিল ইস্তাম্বুল-রাশিয়া-ইউক্রেন চুক্তিতে? ইউক্রেনের সামরিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, সেনাবাহিনীর আকার সীমিত করা এবং ইউক্রেনে বসবাসরত রুশ ভাষাভাষীদের সুরক্ষা দেওয়া। এসব বিষয়ও আলোচনা হয়েছে ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যে। এত কিছুর পর ট্রাম্পের পক্ষ থেকে আশাবাদ ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে এটিই স্পষ্ট যে ট্রাম্প যেকোনো শর্তেই এই যুদ্ধ বন্ধ করতে চান এবং এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী ইউক্রেনের বিরল খনিজ পদার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ নিশ্চিত করতে চান। এ ক্ষেত্রেও অবশ্য নিরপেক্ষতার একটি বড় ধরনের ব্যত্যয় থেকে যায়।
আপাতদৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র দুই পক্ষের মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধের মধ্য দিয়ে নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হলেও কূটনৈতিক বিবেচনায় কিন্তু রাশিয়াই শতভাগ এই যুদ্ধের ফলাফল নিজেদের করে নিতে যাচ্ছে। ২০০৮ সালের বুখারেস্ট সম্মেলনে ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্য করে নিতে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইউরোপীয় নেতাদের চাপ দেন। আজ ১৭ বছর পর এসে আনুষ্ঠানিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের দেওয়া চাপ থেকে সরে আসতে হচ্ছে। এটি এক বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে রাশিয়ার এক বড় ধরনের বিজয় অর্জন।
ট্রাম্প ও পুতিনের মধ্যকার আলোচনায় পুতিনের পক্ষ থেকে উপরোক্ত দাবিগুলো মেনে না নিলে যুদ্ধবিরতির প্রশ্নে অনীহা প্রকাশ করা হয়েছিল। দুই নেতার মধ্যে ফোনালাপের আগে এবং পরে রিয়াদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়া-ইউক্রেনের প্রতিনিধিদের কয়েক দফা আলোচনার মাঝেও দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল, যেখানে রাশিয়া একের পর এক ইউক্রেনের ওপর তাদের আক্রমণ অব্যাহত রাখছিল। এর বিপরীতে মার্কিন সমর্থন হারিয়ে ইউক্রেন ধুঁকছিল।
সর্বশেষ অগ্রগতি সম্পর্কে জানানো হয়েছে যে রাশিয়া ট্রাম্পের প্রস্তাব অনুসারে কেবল ইউক্রেনের জ্বালানি স্থাপনাগুলোতে ৩০ দিনের জন্য যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে এবং এই সময়ের মধ্যে আলোচনার ফলাফল তাদের অনুকূলে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধবিরতিতে তারা সম্মত হবে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে মনে হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে রাশিয়ার হয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র নিজ থেকেই। আর এর কারণ একটিই, দীর্ঘ মেয়াদে ইউক্রেনের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব ধরে রাখা। তবে এর বিনিময়ে রাশিয়াকে ভবিষ্যতে ইউক্রেনের নিরাপত্তার জন্য শঙ্কা হওয়া থেকে বিরত রাখতে হলে তাদের দাবিগুলো মেনে নিতেই হবে। একই সঙ্গে এটিও ধারণা করা হচ্ছে যে দুই নেতার মধ্যে ফোনালাপে রাশিয়ার ওপর থেকে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা পুরোপুরি প্রত্যাহার করা না হলেও যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে এটি প্রত্যাহারের বিষয়ে ট্রাম্পের সম্মতি থাকতে পারে। আর এমনটি হলে এটি ইউরোপের জন্যও একটি বাড়তি চাপ সৃষ্টি করবে।
আপাতত যুদ্ধ বন্ধ এবং একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা সৃষ্টি হলেও দীর্ঘ মেয়াদে এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি কেবল ইউরোপ নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও স্বার্থের প্রতিকূলে যেতে পারে। একদা ১৯৯০-এর দশকে রাশিয়ার গণতান্ত্রিক উত্থানকে গ্রহণ না করে পশ্চিমা দেশগুলো নিজেদের শক্তি দিয়ে তা মোকাবেলা করার চেষ্টা করেছে, যা থেকে রাশিয়া ক্রমেই নিজেদের নিরাপত্তা উদ্বেগ থেকে আগ্রাসী হয়েছে। সময়ের ধারাবাহিকতায় পুতিনের একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্বে রাশিয়া কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশ্বের শক্তির প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করেছে।
লেখক : অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
mfulka@yahoo.com
সেলাই করা খোলা মুখ
সবার আগে জাতীয় ঐক্য
- মোফাজ্জল করিম

জাতীয় পর্যায়ে ছোট-বড় যেকোনো আন্দোলন বা কর্মসূচির সাফল্যের জন্য সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন, তা হচ্ছে জাতীয় ঐক্য। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ একাত্তরের আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। তখন আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি, তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ওই সময় মুষ্টিমেয় দু-একটি জনসমর্থনশূন্য রাজনৈতিক দল ব্যতীত বাকি সবাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক। তবে হ্যাঁ, যে ভয়াবহ পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে তখন সারা দেশ যাচ্ছিল, তাতে হয়তো মুখ ফুটে বেশির ভাগ মানুষই স্বাধীনতার সপক্ষে কথা বলতে পারত না।
 স্বাধীন বাংলাদেশের গত দেড় দশকের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে পাক আমলের সঙ্গে কোথায় যেন কিছুটা হলেও মিল পাওয়া যায়। এখানেও মানুষের মনে যতই কষ্ট, যতই প্রতিবাদ জমা হোক না কেন, তা প্রকাশ করতে গেলেই ছিল বিপদ। গুম খুন ক্রসফায়ার মামলা হামলা ইত্যাদির ডেমোক্লিসের তরবারি সব সময় মাথার ওপর ঝুলত। স্বৈরাচারী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হলেও সাহস করে কেউ প্রতিবাদ করতে পারত না।
স্বাধীন বাংলাদেশের গত দেড় দশকের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে পাক আমলের সঙ্গে কোথায় যেন কিছুটা হলেও মিল পাওয়া যায়। এখানেও মানুষের মনে যতই কষ্ট, যতই প্রতিবাদ জমা হোক না কেন, তা প্রকাশ করতে গেলেই ছিল বিপদ। গুম খুন ক্রসফায়ার মামলা হামলা ইত্যাদির ডেমোক্লিসের তরবারি সব সময় মাথার ওপর ঝুলত। স্বৈরাচারী শাসনের জাঁতাকলে পিষ্ট হলেও সাহস করে কেউ প্রতিবাদ করতে পারত না।
অবশেষে এলো জুলাই চব্বিশের তারুণ্যনির্ভর আন্দোলন। সরকারি চাকরিতে নিয়োগের কিছু অন্যায্য নীতিমালার বিরুদ্ধে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা গড়ে তুলল ব্যাপকভাবে জনসমর্থিত একটি আন্দোলন, যাকে বলা হলো কোটাবিরোধী আন্দোলন। এর পাশাপাশি সাধারণ মানুষ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রকাশ্য সমর্থন ছাড়াই রাজপথে নামল বিপুল জনসমর্থন নিয়ে। শিক্ষার্থীরা যখন একাত্মতা ঘোষণা করে ওই নাম-গোত্রহীন মানুষের সঙ্গে এককাতারে দাঁড়াল, তখন ছাত্র-জনতার এই অভূতপূর্ব সম্মিলন শাসকগোষ্ঠীর ভিত দিল কাঁপিয়ে।
নিবন্ধের গোড়াতেই আমরা বলেছি, এই ভূখণ্ডে ঐক্যের সবচেয়ে বড় উদাহরণ একাত্তরে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ। শুরুতে যা ছিল রাজনৈতিক আন্দোলন, দাবিদাওয়া আদায়ের কৌশল, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিসংগ্রামে সারা দেশের আপামর জনগণকে সম্পৃক্ত করে তা-ই রূপ নেয় ‘এক জাতি এক দেশ বাংলাদেশ’-এর স্লোগানে, তথা মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৪৭ থেকে ২৪ বছরের লাঞ্ছনা-বঞ্চনার ইতিহাস বাঙালিকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল, পাকিদের সঙ্গে আর এক দিনও থাকা চলবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও আমরা ছিলাম সুবিধাবঞ্চিত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। পাকিরা মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধাভোগীকে সঙ্গে নিয়ে রীতিমতো শাসন-শোষণ করছিল পূর্ব বাংলাকে। অনেক জেল-জুলুম, হত্যা-নির্যাতন-নিপীড়নের পর একাত্তরে যখন একটি অসম যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয় বাংলার মানুষের ওপর, তখন হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান, বাঙালি-পাহাড়ি, ধনী-গরিব সবাই উপলব্ধি করল, এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। এবং তা হতে হবে ঐক্যবদ্ধভাবে। একাত্তরে প্রকাশ্যে হয়তো সবাই মুক্তির কথা, স্বাধীনতার কথা বলতে সাহস পেত না, কিন্তু এ দেশের সব মানুষের অন্তরে স্বাধীনতার দীপশিখাটি প্রজ্বলিত ছিল। ফলে রণক্ষেত্রে অস্ত্রহাতে হয়তো যুদ্ধ করেছে দুই লক্ষ তরুণ মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতার জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে গেছে তারা, আর সারা দেশের ঘরে ঘরে কোটি কোটি মানুষ ছিল তাদের সপক্ষে। এমন জাতীয় ঐক্য বিদ্যমান ছিল বলেই একটি সম্পূর্ণ অসম যুদ্ধে একটি দানবীয় শক্তিকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছিল বাংলাদেশের মানুষ। সেই ঐক্য ছিল ইস্পাতকঠিন। কোনো লোভ-লালসা, কোনো প্রাপ্তির হাতছানি ফাটল ধরাতে পারেনি সেই ঐক্যে।
কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বিজয় অর্জনের পর যে কলুষিত অধ্যায় সূচিত হলো এ দেশের ইতিহাসে, তা-ই গ্রাস করতে লাগল সব স্বর্ণোজ্জ্বল অর্জনকে। কোথায় রইল জাতীয় ঐক্য, কোথায় উবে গেল একটি নির্যাতন-নিষ্পেষণমুক্ত সাম্য-সম্প্রীতির বাংলাদেশের স্বপ্ন। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো এক শ্রেণির ক্ষমতাশালী মানুষ ‘এক সাগর রক্তের বিনিময়ে’ পাওয়া দেশটাকে খামচে-খুবলে-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে ছাড়ল। এই অন্যায় অবিচার নির্যাতনের মাশুল জাতিকে দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী যাবৎ শোধ করতে হলো।
এর পরেই এলো ২০২৪-এর জুলাই-আগস্টের ঘুরে দাঁড়ানোর সফল আন্দোলন। স্বল্পমেয়াদি সেই আন্দোলন সাফল্যের মুখ দেখল ছাত্র-জনতার ঐক্যের কারণে। দীর্ঘদিনের অত্যাচারী স্বৈরশাসক ‘য পলায়তি স জীবতি’—এই আপ্তবাক্য জপতে জপতে হেলিকপ্টারে চড়ে পালালেন। এই দেশেরই এক রাজা একদা খিড়কি দুয়ার দিয়ে প্রাণ নিয়ে যেভাবে পালিয়েছিলেন সেভাবে। আর দীর্ঘদিন চেপে থাকা এই সিন্দবাদের ভূতকে নামানো সম্ভব হয়েছে ওই জাতীয় ঐক্যের কারণে। জেল-জুলুম, খুন-গুম ও আয়নাঘরের ভয়ে মুখে না বললেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু জাতি ঐক্যবদ্ধ ছিল এমন একটি পরিণতি দেখার জন্য।
এখন সবার একটাই প্রত্যাশা, সিন্দবাদের ভূতকে তো নামানো গেল, এরপর কী? নিশ্চয়ই স্বপ্নের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ফিরে পাওয়া, যার জন্য জাতি গত দেড় যুগ অনেক মূল্য দিয়েছে। আর সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য নানাজনের নানা মত ও পথের ঠিকানা থাকতে পারে। তবে এক জায়গায় তো সংশ্লিষ্ট সবাইকে একমত হতে হবে : যে করে হোক একটি সুন্দর সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন। এবং তা যত দ্রুত সম্ভব, ততই মঙ্গল। নইলে আবার সুযোগসন্ধানীরা জল ঘোলা করে ফেলবে। এত দিনের দুঃখ-কষ্টে, ত্যাগ-তিতিক্ষায় যা কিছু অর্জন, তা যাবে হারিয়ে। শেষ কথা তাই, জাতীয় স্বার্থে চাই জাতীয় ঐক্য, যার কোনো বিকল্প নেই।
লেখক : সাবেক সচিব, কবি
mkarim06@yahoo.com



